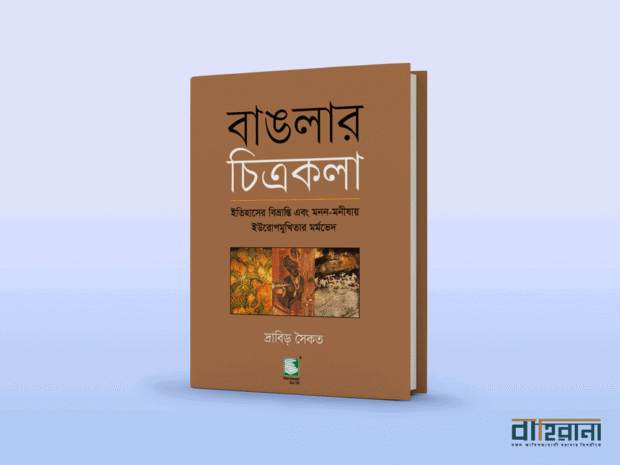দ্রাবিড় সৈকত একজন কবি এবং সেইসাথে তিনি চিত্রকলা নিয়ে পড়েছেন। চিত্রকলায় রঙ-রেখায় অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে হয়, এটা এই মাধ্যমটির মূল ক্রিয়া, যেমন কবিতায় শব্দ। কিন্তু একদেশের চিত্রকর্মের সাথে অন্যদেশের চিত্রকর্মের পার্থক্য কীভাবে গড়ে ওঠে? পার্থক্য গড়ে উঠে দেশটির ইতিহাসের পর্যায়ের রূপান্তরের বা এক শব্দে ইতিহাসের মাধ্যমে। ইউরোপের চিত্রকলায় পুঁজিবাদী ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার কারণে বিমূর্ত চিত্রকলা গড়ে উঠেছিল, সেটা ওই ইতিহাসের রূপান্তরের কারণেই। গীর্জার প্রভাবও ভালোভাবে আছে সেখানে। দ্রাবিড় সৈকতের বাঙলার চিত্রকলা: ইতিহাসের বিভ্রান্তি এবং মনন-মনীষায় ইউরোপমুখিতার মর্মভেদ বইটিতে বাংলাদেশের চিত্রকলার ইতিহাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, তিনি বলছেন আমাদের চিত্রকলার মর্মমূল এখনও ঠিকমতো রচিত হয়নি, বরং হয়েছে ভুলভাবে লোকশিল্প নাম দিয়ে। এটা ভাববার মতো নতুন কথা নি:সন্দেহে।
এই বিষয়ে আমাদের দুইজন মহৎ শিল্পীর দিকে তাকাতে পারি আমরা, বাংলাদেশের চিত্রকলায় বাংলার কৃষিকর্মেরত পেশিবহুল আদি কৃষকদের এস এম সুলতান তার চিত্রকলায় নিয়ে এসেছিলেন, সুলতানের কাছে আমরা ই্উরোপীয় চিত্রকলার বলয় থেকে বেরুনোর কথাই শুধু নয় তার চিত্রকলায়ও তার প্রতিফলন দেখেছি। অন্যদিকে স্বেচ্ছানির্বাসিত ভাস্কর্যশিল্পী নভেরা আহমেদ যিনি আমাদের শহীদ মিনারের নকশা করেছিলেন, তার বিভিন্ন কাজের মধ্যে ইউরোপের বাংলাদেশিরূপও দেখেছি। প্রশ্ন হলো ঠিক কী কারণ ও বিবেচনায় এই দুই শিল্পীকে বাংলাদেশের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্পের মূল ধারায় গ্রহণ করা হয়েছিল? এস এম সুলতান-এর মূলধারায় প্রবেশ একটি বিপর্যয়কর ঘটনা ধরে নিলেও, তার কাজও একদমই ইউরোপের উত্তরাধিকার বঞ্চিত নয়, নভেরা আহমেদ-এর কথা তো বললামই। এখানেই উত্তর রয়েছে, তাদের কাজে কোনো না কোনোভাবে ইউরোপমুখীতার নিদর্শন ছিল। তবে বাংলাদেশের চিত্রকলা থেকে বাংলার প্রকৃত রূপ-রঙ-রসের চিত্রকলাকে মূলধারায় স্থান দেওয়া হয়নি। ফোক আর্ট বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এতে যা ক্ষতি হচ্ছে তার মূল্য নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। দ্রাবিড় সৈকত বাঙলার চিত্রকলা বইটিতে কেন এমন হলো তারই অনুসন্ধান করেছেন।
দ্রাবিড় সৈকতের বাঙলার চিত্রকলা ইতিহাসের বিভ্রান্তি এবং মনন মনীষায় ইউরোপমুখিতার মর্মভেদ বইটিতে ভূমিকাসহ প্রবন্ধ আছে চারটি, অধ্যায় দিয়ে ভাগ করা প্রবন্ধগুলোকে একটি গবেষণার চারটি ভাগ বলা যেতে পারে। “বাঙলার চিত্রকলার প্রাসঙ্গিক আলোচনা” এরপর একে একে “ঐতিহাসিক মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে বাঙলার চিত্রচর্চার ধারা” “বাঙলার চিত্রকলা: ইউরোপমুখিতার মর্মভেদ” ও “মনস্তাত্ত্বিক বলয়ে বাঙলার চিত্রকলা: প্রস্তাবনা ও সম্ভাবনা” এই হচ্ছে অধ্যায়গুলো। বইয়ের শিরোনামেই স্পষ্ট, তিনি বাংলার ভৌগোলিক অঞ্চল ধরে চিত্রকলার ইতিহাসের ফাঁক-ফোকর আর বিভ্রান্তির নিশানা খুঁজতে চাইছেন। দিতে চাইছেন সম্ভাবনার ইঙ্গিত, কিন্তু সমস্যাকে চিহ্নিত করেই।
প্রথম সমস্যাটি হলো সমস্যাটি ‘বাঙলা’ শব্দটিতেই, তাই তিনি পরিষ্কার অবস্থান নিতে শব্দটি দ্বারা অঞ্চল বুঝিয়েছেন, তিনি বলছেন, “‘বাঙলা’ শব্দটি দিয়ে কী বোঝানো হবে এ বিষয়ে বিবিধ ঐতিহাসিক কারণে কিছুটা ধোঁয়াশাচ্ছন্নতা রয়েছে।” এই ধোঁয়াশাচ্ছন্নতার কারণে বিশাল অঞ্চলজুড়ে এই ভূভাগটির সবকিছুরই সঠিক মূল্যপ্রক্রিয়া নির্ণয়ে সমস্যা রয়ে গেছে। এর মধ্যে চিত্রশিল্প সবচেয়ে বেশি গোলমেলে অবস্থায় রয়েছে। কারণ লোকশিল্পকে বাঙলার চিত্রকলা বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যা আদৌ সত্য নয়। তিনি একে প্রশ্নের আওতায় এনেছেন, এর মাঝেই এসে পড়েছে পাশ্চাত্যের চিত্রশিল্পের সমান্তরালে এখানকার চিত্রকর্মের ইতিহাস, একেও প্রশ্নের পরিধিতে এনেছেন তিনি।
এরজন্য তিনি ইতিহাসের পেছনদিক থেকে তার মতনির্মাণের প্রক্রিয়াটি শুরু করেছেন, যা বইটিকে নতুন কথা বলাতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বলে ধারণা করি। এর জন্য তিনি বাঙলা অঞ্চলটির ধর্ম, দর্শন বিশ্লেষণ করেছেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের সাথে এর বৈপরীত্য ও শক্তির জায়গাটিও নির্দিষ্ট করেছেন, শুধু তাই নয় বৈশ্বিক যোগাযোগের বিষয়টিও বাদ দেননি। আবার শিল্পটির বৈশ্বিক অনুকরণের বিষয়ে বাজার-অর্থনীতির প্রভাবও উল্লেখিত হয়েছে বইটিতে। বলা যায় বাঙলার চিত্রকলা কেমন এর মূল সন্ধানে গিয়ে সেটি কী কী বিষয়ে সচেতন থাকতে পারে সেসব বিষয়ও তুলে এনেছেন তিনি। ফলে লোকশিল্প আর পাশ্চাত্য সবই বিশ্লেষণের মধ্যে এসে পড়েছে।
বইটি এদেশের চিত্রকলা বিষয়ে আগ্রহীদের জন্য নতুন ভাবনা দেবে এটা বলা যায় আর সেইসাথে নতুন চিন্তা ও ইতিহাসে আগ্রহীদেরও নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে।
বাঙলার চিত্রকলা : ইতিহাসের বিভ্রান্তি এবং মনন-মনীষায় ইউরোপমুখিতার মর্মভেদ
লেখক: দ্রাবিড় সৈকত
প্রকাশকাল: ২০২৪
প্রকাশনী: পাঠক সমাবেশ
দাম: ৪৯৫ টাকা।
বইটি কিনতে চাইলে:
বাঙলার চিত্রকলা (Banglar Chitrakola) – বাহিরানা