ফয়েজ আলমের সাক্ষাৎকার
স্বতন্ত্রধারার লেখক, গবেষক, কবি ও অনুবাদক ফয়েজ আলম সাহিত্য-তত্ত্বচর্চায় তাঁর চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সমৃদ্ধ গবেষণাশৈলী, যুক্তিনির্ভর নৈপুণ্য তাঁকে কেবল একজন সাহিত্যিক নয়, বরং একজন সচেতন তাত্ত্বিক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বহুমাত্রিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সাহিত্যতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, দর্শন এবং আধুনিক সমাজভাবনার আলোকে তিনি এক নতুন ব্যাখ্যা-ভাষা নির্মাণ করেছেন। সমকালীন সাহিত্যধারায় তাঁর বিশেষত্ব হলো—তত্ত্ব ও সাহিত্যচর্চার সমন্বিত প্রয়োগ। তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, লোকায়ত অভিজ্ঞতা এবং আধুনিকতার টানাপোড়েন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর গবেষণা বাংলা সাহিত্যের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক সেতুবন্ধন রচনা করেছে। তত্ত্ববিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রচনা ‘অরিয়েন্টালিজম’ ভাষান্তরের মাধ্যমে তিনি ভাষার স্বচ্ছতা ও মর্মার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, গ্রন্থটি বাংলায় উত্তর-উপেনিবেশবাদ ও সাঈদ চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন, অনুবাদ কেবল ভাষান্তর নয়, বরং এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা-বিনিময়ের সেতু। তিনি সাহিত্যকে দেখেন—সামাজিক দায়বদ্ধতা, সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও নন্দনতত্ত্বের আলোকে। সাহিত্যকে কেবল নান্দনিক অভিব্যক্তি নয়, বরং সমাজ-ইতিহাসের এক নিরন্তর অনুসন্ধান হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থান একদিকে বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে বিশ্বসাহিত্য ও সমকালীন সমালোচনার সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ।
ফয়েজ আলমের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ : ব্যক্তির মৃত্যু ও খাপ-খাওয়া মানুষ (কবিতা, ১৯৯৯); প্রাচীন বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি (গবেষণা, ২০০৪); বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা (গবেষণা, ২০২৪); এডওয়ার্ড সাঈদের অরিয়েন্টালিজম (অনুবাদ, ২০০৫); উত্তর-উপনিবেশী মন (প্রবন্ধ, ২০০৬); কাভারিং ইসলাম (অনুবাদ, ২০০৬); ভাষা, ক্ষমতা ও আমাদের লড়াই প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ, ২০০৮); বুদ্ধিজীবী, তার দায় ও বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব (প্রবন্ধ, ২০১২); জলছাপে লেখা (কবিতা, ২০২১); ভাষার উপনিবেশ: বাংলা ভাষার রূপান্তরের ইতিহাস (প্রবন্ধ, ২০২২); রাইতের আগে একটা গান (কবিতা, ২০২২)।
ফয়েজ আলমের সাক্ষাৎকার-এ উঠে এসেছে—ভাষার রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদের দৌরাত্ম, দেশিয় রাজনীতি, সংস্কৃতির বিকাশহীনতা, ইতিহাসের ঘোঁট এবং শিল্প-সাহিত্যের তত্ত্বীয় নানান বিশ্লেষণ, এর প্রতিফলন তার কবিতায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তার কবিতা নিজস্ব ভাষাগুন, চিত্রকল্প ও উপমার অভিনবত্বে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস পরম্পরায় ইতোমধ্যেই স্বতন্ত্র স্থান অর্জন করেছে।
বাহিরানায় প্রকাশিত ফয়েজ আলমের সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পাঠ বলে পাঠকের নিকট বিবেচিত হবে।
বাহিরানা Talk-এ প্রকাশিত সব লেখক, কবি ও চিন্তকদের সাক্ষাৎকার পড়ুন।
এহসান হায়দার: আপনার ছেলেবেলার দিনগুলো সম্পর্কে বলবেন?
ফয়েজ আলম: ছেলেবেলাটা জীবনের সবচেয়ে মধুর, সৃজনশীলতার পেছনে সবচেয়ে প্রভাবক সময় বলে মনে হয় আমার কাছে। আমার ছোটবেলার একটা পর্ব কেটেছে মফস্বলে, নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া থানার গোপালপুর গ্রামে। আমাদের আদত বাড়ি পাশের যোগীরনগুয়ায়। শৈশব পার করেছি ঘোড়াশালে। আব্বা প্রথমে শিক্ষকতা, পরে সরকারের রাজস্ব বিভাগে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে আসেন। আর ফেরত যাননি। স্বাধীনতার পর ঘোড়াশালে ন্যাশনাল জুটমিলের পারচেজ অফিসার পদে যোগ দেন।ফলে একঅর্থে আমার জীবন অবিরাম সফরের। জন্ম বাবার তৎকালীন কর্মস্থল নেত্রকোনার মদন থানা হেডকোয়ার্টারে। অতিশৈশব কাটে ঠাকুরাকোনায়। এরপর ঘোড়াশাল।
ঘোড়াশালের পরিবেশটা ছিলো অনেকটা নিয়মতান্ত্রিক। সকালে তৈরি হয়ে নাস্তা খেয়ে স্কুল। ছুটি হওয়ার পর স্কুলেই একটু খেলাধুলা। দুপুরে বাসায় এসে খেয়েদেয়ে খানিকটা ঘুম। বিকালে আবার খেলতে বের হতাম। পাশেই ছিল শ্রমিক কলোনী। মাঝেমধ্যে নিয়ম ভেঙ্গে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের সাথে বেরিয়ে পড়তাম। কোন কোন ছুটির দিনে দলবেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তাম শীতলক্ষার পানিতে। শীতলক্ষাতেই আমার সাঁতার শেখা।
আমরা চার ভাই দুই বোন। আব্বা জীবনযাপনে সোজাসাপটা পথের মানুষ ছিলেন। বাংলা ইংরেজি দুটোই ভালো জানতেন। মা কড়া মেজাজের বুদ্ধিমতি মহিলা। হাইস্কুল পার হননি। তবু ভালো বাংলা লিখতে পারতেন। খুব সুন্দর ছিল হাতের লেখা। প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে মা-ই ছিলেন আমাদের ঘরের শিক্ষক। পড়াশোনা আর সামাজিক সম্পর্ক যোজন অর্থাৎ মানুষের সাথে আচারআচরণের ব্যাপারে কড়া নজর রাখতেন। ঝগড়া ফ্যাসাদ এড়িয়ে চলা, বড়দের সম্মান করা এইগুলা ছিল বাধ্যতামূলক। কেউ এসে আমাদের নামে অভিযোগ করলে সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের ধার ধারতেন না। সোজা পিটান। তার বক্তব্য ছিল, এক হাতে তালি বাজে না। তো, মার ভয়ে আমরা সবাই হাতের তালু লুকিয়েই চলাফেরার চেষ্টা করেছি যাতে তালিও না বাজে, পিটানও খেতে না হয়।
আব্বা ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। প্রায়ই বলতেন চাকরি মানে গোলামী। একদিন কাউকে কিছু না বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সবাইকে নিয়ে সোজা গ্রামের বাড়ি হাজির হন। যোগীরনগুয়ায় জ্ঞাতীগোষ্ঠী বেড়ে যাওয়ায় জায়গার টানাটানি। তাই বাড়ি করেছিলেন লাগোয়া গোপালপুর গ্রামে। ওখানে আমার ছেলেবেলার দ্বিতীয় পর্ব। বাড়ি বললে অই জায়গাটাকেই মনে পড়ে।
এই ঘটনায় একরকম আর্থিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সঙ্কটে পড়ে আমার গোটা পরিবার। তবে, আমি এখন ভাবি সেটি ছিল আমার জীবনে খুবই গুরুত্বপুর্ণ এক বাঁক ফেরার মত। ঘোড়াশালের শিল্প এলাকার নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক জীবন থেকে গোপালপুরের জায়জঙ্গল খালবিলে ভরা বিপুল বিস্তারের মধ্যে আসল স্বাধীন এক জীবন। বাড়িটাও ছিলো তিনচার পুরুষের নিজস্ব সম্পত্তি। তেরচৌদ্ধ বিঘা জমির উপরে মূল বাড়িটাই পাঁচ বিঘা প্রায়। চারদিকে গহীন জঙ্গলের সামনের দিকের এককোনায় খানিকটা জায়গা পরিস্কার করে দুইতিনটা ঘর। মাঝখানে বড় উঠান। এরপর কাছারি ঘর, ওখানে বলে ‘আলগঘর’। কাছারি ঘরের সামনেও অনেকটা খোলা জায়গা। এরপর তরকারী ক্ষেত। শেষে বিল।
ঘোড়াশালের বাসার পাশের ফিটফাট ইস্কুল জীবন শেষ। গোপালপুরে স্কুলে যেতাম প্রায় পৌনে এক মাইল হেঁটে, পুব দিকে সূর্য মুখে করে। আবার ছুটির পর ফিরতাম পশ্চিম দিকে। আবার সেই রোদমুখে। তবু ভালো লাগত। কাঁচা সড়কের দুইপাশে নানা জাতের ফসলের ক্ষেত। বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো। নানা আকারের আর রঙের গরুছাগল চড়ে বেড়াত। অনেকে মিলে গায়ে বাতাস লাগিয়ে, বকবক করতে করতে, অযথা ধাক্কাধাক্কি হাসাহাসি করতে করতে স্কুলে যাওয়ার মজাই আলাদা।
বর্ষায় কানায় কানায় ভরে উঠে সামনের বড়বিল। বাড়ির নামায় এসে ছলাৎ ছলাৎ ছন্দোময় আওয়াজ তোলে। শুকনার সময়টা বিলের পাড়ে খেলার জায়গা। বছরের শুকনার আটমাস আমাদের দুনিয়াটা ছিল অসীম। যেদিকে চোখ যায় প্রকৃতির সবুজে ঢাকা। যেদিকে মন চায় হাঁটতাম, নিত্য নতুন জায়গা আবিস্কার করতাম। একেকটার সুরত, রঙ, গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন। সন্ধ্যায় বিলের পাড়ে খেলার শেষে দুর্বার কার্পেটে শুয়ে দেখতাম আসমানজুড়ে সরালির উড়াল। হাজার হাজার সরালির ডাকের রিনরিনে কলতানে ভরে উঠা গোপালপুরের আসমান। চাঁদনী রাতে পড়া শেষ করে ঘুরতে বের হতাম গ্রামে। নিরিবিলি পথে আম কাঁঠাল কিংবা বরুণ গাছের নিচে ঝালর কাটা জোছনা, চারদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করা ছোট ছোট গাছ মিলে গা চমচম করা রহস্যময় অবয়বের আবছায়া।
কোন কোন বর্ষার রাতে নৌকা করে চলে যেতাম বিলের মাঝাখানে। গলুইয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখতাম। চারপাশের অপার্থিব নিরবতার মধ্যে পানির ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ। কাটাকাটা মেঘের ফাঁক গলে নেমে আসা চাঁদের আলো। মনে হত আমাদের চেনা দুনিয়ার বাইরের এক জগত যেন। শীতের মওসুমে কখনো মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতাম চাঁদের রহস্যময় আলোয় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। কোন দূর থেকে ভেসে আসছে সবিনার মধুর কোরআন তেলাওয়াত। কিংবা পশ্চিমপাড়ার কোন বাড়িতে জমে উঠা কীর্তনের ঢোল জুরির শব্দ। সারা দুনিয়া যখন নিরব তখন ছন্দোময় এই আওয়াজ অপার্থিব হয়ে ধরা দিত। শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম!
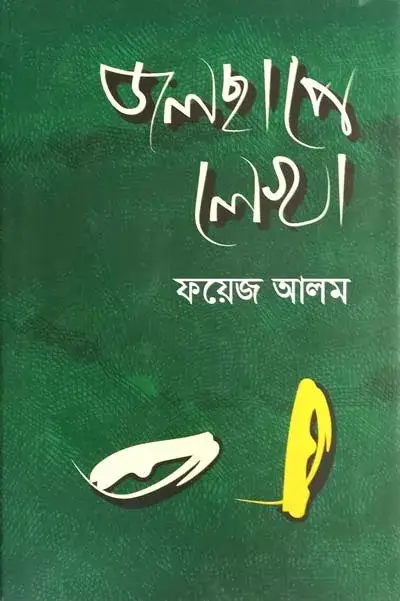
অই পরিবেশে যারা জন্মেছে তাদের জন্য সেটি এক রকম। আমার কাছে তা আরেক হয়ে ধরা দিয়েছিল। শিল্পএলাকার একটা কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশ থেকে ছুটি পেয়ে অই বিশাল দুনিয়ায় গিয়ে দেখি সবই নতুন, সবই বিস্ময়, কেবল আমার আবিষ্কার আর আস্বাদনের অপেক্ষায়। প্রতিদিন অবিরাম সৃষ্টিশীল প্রকৃতি, তার নতুন নতুন রহস্য, আন্তরিক উম খুঁজে নিয়ে তার সাথে সম্পর্ক যোজনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠা আমার। সে জীবনের চারপাশ মনের সৃজনশীল হয়ে উঠার আঁতুড়ঘর। সৃষ্টির সেই আঁতুড়ঘরে কাটিয়েছি আমার ছেলেবেলা। খুব কম বয়সেই লিখতে শুরু করি, খুব সম্ভবত পঞ্চম শ্রেণি থেকে। অস্টম শ্রেণীতে হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা বের করি আমি আর এক বন্ধু মিলে। সেটি আমার জীবনের সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে রহস্যময়, সবচেয়ে উদ্দীপক সময়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পুরাদস্তর লেখক হয়ে উঠার উস্কানি অইখান থেকে এসেছে।
এহসান হায়দার: আপনি কবিতা লিখতে ভালোবাসেন, কিন্তু চিন্তাচর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতেও আপনি নিরন্তর প্রচেষ্টা রেখেছেন, ভিন্নভাবে দেখা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে, আপনার প্রবন্ধ রচনা ও গবেষণাগুলোর গূঢ় লক্ষ্য জানাবেন?
ফয়েজ আলম: কবিতা দিয়েই আমার লেখালেখি শুরু। প্রথম প্রকাশনা কবিতার বই, ১৯৯৯ সালে বের হয়। কবিতা ভালবাসি কেবল তা নয়, নিজেকে কবিই মনে করি আমি। কবিতার আবেগ থেকে ভালোবাসা থেকে কবিতা লেখি। লিখে চলেছি নিয়মিত।
কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালেখি শুরু করি অত্যন্ত সচেতনভাবে, একটা দায়িত্ববোধ থেকে, উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথাগত ধারণা ও জনপ্রিয় জ্ঞানভাষ্যগুলোকে ভালোভাবে যাচাই না করে গ্রহণ না করার একটা অভ্যাস কম বয়সেই গড়ে উঠেছিল আমার। কবিতা চর্চার প্রয়োজনীয় পাঠ নিতে গিয়ে দেখি বাঙালির জ্ঞানজগতের বহু চলমান ধারণা, জনপ্রিয় বলশালী ডিসকোর্স আমাদের জনমানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সিলসিলা ও চলমান জীবনযাপনের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক। এমন বহু বয়ান বাঙালি তথা বাংলাদেশের জনমানুষের ঐতিহ্যিক সঞ্চয় হিসাবে প্রচার করা হয়েছে যেগুলো আসলে সার্বজনীন ইতিহাস বা সংস্কৃতির অংশ নয়, সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতার ফসল, যেগুলো বহু পরের বিশেষ করে উনিশ বিশ শতকের নির্মাণ। উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞানভাষ্য ও বয়ানের ধরণ, নির্মাণের কারণ ও ইতিহাস খুঁজতে শুরু করি আমি। এবং এই খোঁজার সফরেই পরিচিতি হই ওয়াল্টার বেনজামিন, রেমন্ড উইলিয়ামস, মিশেল ফুকো, এডওয়ার্ড সাঈদ, জ্যাক দেরিদা, গিয়োর্গিও আগামবেন, এইমে সিজেয়ার, ফ্রাঞ্জ ফানো, এইসব লেখকের চিন্তার ধরণ ও প্রথাগত জ্ঞান বিশ্লেষণের কৌশলগুলোর সাথে।
আমি দেখি এইসব নির্মিত জ্ঞানভাষ্যের আন্তসম্পর্ক আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি করছে। ইতিহাসের কোন একটি উদ্দেশ্যমূলক বয়ান জনপ্রিয় হয়ে উঠার পর তা প্রভাবিত করছে সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি বা সাহিত্যের ধারাণাগুলোকে। তেমনি, উল্টোটাও সত্যি। এগুলো আমাকে আমার মতো করে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে। কেবল তাই না, এই জাতীয় জ্ঞানভাষ্যগুলো নির্দিষ্ট কিছু সাংস্কৃতিক ছাঁচ, ট্যাবু তৈরির মধ্য দিয়ে সৃজনশীল মানুষদেরকে কেবল নির্দিষ্ট একটা দিকে চালিত করে। মুক্তিবুদ্ধির চর্চা সম্ভব হয় না। এইসব জ্ঞানভাষ্য, বিকৃত বয়ান, অপরিশোধিত ধারণাগুচ্ছের জন্মের কারণ ও ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারি এ সমস্ত কিছুর সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে উপনিবেশি শাসন ও উপনিবেশি জ্ঞানচর্চার। বিশেষত গোটা উনিশ শতকে উপনিবেশি শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় বাঙালির রেঁনেসার নামে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ ও ধর্মচর্চার ধারাবাহিক বিকাশের চিহ্ন তছনছ করে প্রচার করা হয় মনগড়া, সাম্প্রদায়িক আকাঙ্ক্ষায় রাঙানো নানা রকম জ্ঞানভাষ্য। এইসব নির্মিত জ্ঞানভাষ্য ও বয়ান প্রধানত কলিকাতাকেন্দ্রিক উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষায় রঞ্জিত, যার সাথে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বিশেষ কোন সংযোগ নেই। যুগের পর যুগ ধরে এগুলো পনুরুৎপাদন করা হয় পাঠ্যপুস্তক, পত্রপত্রিকা, অন্যান্য রচনায়। হাজির করা হয় অসম্ভব সব তাফসির। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনমানুষের বিকাশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক চর্চা যেমন বিকৃত করা হয়, তেমনি পরিকল্পিত ইতিহাস নির্মাণ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এমন ইতিহাসের বয়ান ও সংস্কৃতি প্রস্তাব করা হয় যাতে বাংলাদেশের মানুষের মনে স্থায়ী হীনমন্যতা বোধের সৃষ্টি হয়।
আমার সকল বৃদ্ধিবৃত্তিক শ্রম-ঘামের বেশিরভাগটাই ব্যয় করেছি এইসব উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞানভাষ্য ও বানোয়াট বয়ান নির্মাণের ইতিহাস ও লক্ষ্য তুলে ধরা, এ জাল ভেদ করে সত্যের কাছে পৌঁছানোর কাজে। এ জন্য আমি হাতবদলি তথ্য ও মনগড়া তাফসিরের জাল ছিঁড়ে প্রাথমিক উৎসের সন্ধান করেছি আমার সব রচনায়। জনমানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের আসল ইতিহাস উদ্ধার এবং তার নিরিখে ভবিষ্যতের পথ সাজিয়ে নেয়া আমার লেখালেখির একটা উদ্দেশ্য।
অন্যদিকে, এখানে চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসে ব্যক্তি ভয়াববহভাবে নিষ্পেষিত। সে কেবলই ছোট, নিজস্ব স্বরহীন, প্রতিরোধহীন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গুটিতে পরিণত হচ্ছে। আমাদের সামাজিক বিন্যাসটাই এমন এখানে দলছুট ব্যক্তির অস্তিত্বরক্ষা কঠিন। দল বলতে আমি কেবল রাজনৈতিক দল বুঝাচ্ছি না। সরকারী-বেসরকারী চাকরি, সামাজিক তৎপরতা, শিল্প চর্চা, সাহিত্যচর্চা সবক্ষেত্রেই তুমি দেখবে কিছু অযোগ্য অমেধাবী মানুষ বিশেষ সুবিধা নেয়ার জন্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির তাবেদারীর দল সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি এইসব দাসদলের বাইরে থাকবে সে অধিকার বঞ্চিত ও নির্যাতিত হবে। এই দেশে দলহীন ব্যক্তি সবধরণের ক্ষমতার শিকার, নির্যাতনের লক্ষ্য। ব্যক্তি এখানে ভাষাহীন একটা অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। সে কাজে লাগে মাথা গোনার সময়, ভোটের দরকারে। এই নিষ্পেষিত ব্যক্তির অধিকারের জন্য, তার কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে দেয়ার জন্যও আমি লিখি।
এহসান হায়দার: বাংলাদেশে অনুবাদসাহিত্যে চিন্তাশীল পাঠকের নিকট আপনি পরিচিত মুখ। এদেশে অনুবাদের জগতে চিন্তাশীল গ্রন্থ কম জনপ্রিয়তা পেয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার অনুবাদগ্রন্থ খুব দ্রুত পাঠক গ্রহণ করেছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন?
ফয়েজ আলম: একটা সময় ছিল সিরিয়াস রচনার অনুবাদ খুব একটা হত না, পাঠকদের সাড়াও পাওয়া যেত না। অরিয়েন্টালিজমের অনুবাদ যখন বের হয় তখনো সিরিয়াস অনুবাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠক তৈরি হয়নি। সময়টাও গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ হয়েছে। এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার চাপে সচেতন মানুষের মধ্যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, গণবুদ্ধিজীবী হিসাবে ফুকো, চমস্কি, এডওয়ার্ড সাঈদ এদের নাম সারা দুনিয়ায় খুব আলোচিত হচ্ছিল। গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসাবে অরিয়েন্টালিজম-এর কথা অনেকে শুনেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তথাকথিত ‘বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ব’ মার্কা সমালোচনা-আলোচনা পাঠে জর্জরিত তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও পিপাসা তৈরি হচ্ছিল জ্ঞানচর্চার বিষয়গুলোকে ক্রিটিক্যালি দেখার ও বুঝার। এ পরিস্থিতিতে, সিরিয়াস রচনার জন্য উন্মুখ পাঠকদের সামনে অরিয়েন্টালিজম হাজির করার পর তারা দ্রুত সেটি গ্রহণ করেন। শুধু তাই না, অরিয়েন্টালিজম-এর অনুবাদ এখানকার পাঠকদেরকে উস্কানি দেয় সিরিয়াস লেখাজোকা খুঁজে নেয়ার ব্যাপারে। অন্যদিকে, অনুবাদটির জনপ্রিয়তা দেখে এখানকার অনুবাদকরাও বুঝতে পারেন কি ধরণের কাজ বেছে নেয়া দরকার। এখন কিন্তু চিন্তা উস্কানো রচনার অনুবাদ সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ বেড়েছে। আমি তো অতদূর বলতে চাই যে, বাংলাদেশে ক্রিট্যিাক্যাল বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার যে বিকাশমান ধারাটা আমরা এখন দেখছি তার সূচনা পর্বে অরিয়েন্টালিজম-এর অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে।
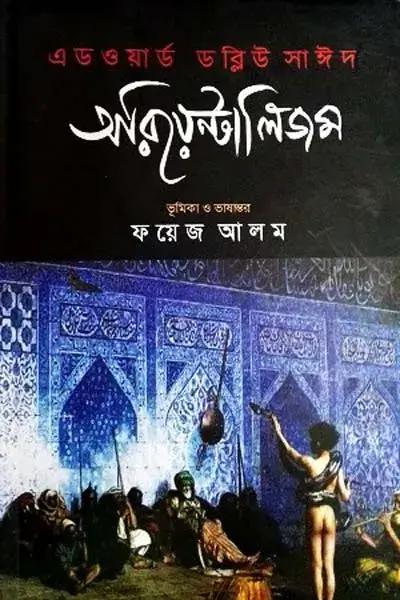
এহসান হায়দার: এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদের লেখা ১৯৭৮ সালের একটি গ্রন্থ অরিয়েন্টালিজম (Orientalism), যেখানে লেখক প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আপনি এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেছিলেন, তখন কী কারণে এই গ্রন্থটি অনুবাদের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল আপনার?
ফয়েজ আলম: একটু আগে যেটি বলছিলাম, বাংলাদেশের জনমানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস নিয়ে প্রচলিত বিকৃত জ্ঞানভাষ্য, বয়ান, অপরিশোধিত ধারণাগুচ্ছের জন্মের কারণ ও ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আমি এক পর্যায়ে দেখি এগুলো উপনিবেশি শাসন ও উপনিবেশি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র থেকেই উঠে এসেছে। সাঈদ তার বইয়ে দেখিয়েছেন পশ্চিমের রাষ্ট্রনায়ক-চিন্তক-লেখক-সংস্কৃতি কর্মী পুবের দেশ ও সমাজগুলোকে হীন চোখে দেখেছেন। পুবকে তারা অসভ্য, বর্বর, বিশৃঙ্খল হিসাবে প্রচার করেছেন। যার ফলে পুবকে দখল করা এবং সেখানকার সমাজকে সভ্যভব্য করার উদ্দেশ্যে সেখানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে শাসন করা জায়েজ হয়ে যায়। আর এর প্রতি সম্মতি উৎপাদনের জন্য উপনিবেশিত মানুষের ইতিহাস, জ্ঞান, সাংস্কৃতিক চর্চাকে হীন প্রমাণ করে মুছে ফেলা এবং তার বদলে উপনিবেশক শক্তির ইতিহাস ও জ্ঞানভাষ্য প্রতিষ্ঠা করার দরকার হয় যা জন্ম দেয় হেজেমনিক সম্পর্কের। কেন এবং কিভাবে এটি ঘটে তার দুর্দান্ত বিশ্লেষণ এডওয়ার্ড ডিব্লিউ. সাঈদের ‘অরিয়েন্টালিজম’ বইটি। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে, বইটি পড়ার পর দেখি যে, সাঈদ উপনিবেশের যে বৈশ্বিক বিন্যাস দেখিয়েছেন তার স্থানিক নমুনা হলো বাংলাদেশে বৃটিশ উপনিবেশ। আমার উপর উপনিবেশের ক্ষয়ক্ষতির ধরন ও মাত্রা পদ্ধতিগতভাবে বুঝার ক্ষেত্রে ‘অরিয়েন্টালিজম’ গাইডবুকের মত কাজ করে। তখনই আমি বইটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিই।
এহসান হায়দার: প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়টিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেন?
ফয়েজ আলম: প্রাচ্যতত্ত্ব এমন এক তত্ত্ব যা একক কোন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়নি। তেমনি যারা প্রাচ্যতত্ত্বের স্রষ্টা তারা একে তত্ত্বহিসাবে প্রচারও করেননি বা করতে চান না। কারন প্রাচ্যতত্ত্বমূলত একদল মানুষের দ্বারা আরেকদল মানুষকে শোষণ-শাসন-নির্যাতন করার বিষয়টিকে বৈধ দাবী করার জ্ঞানতত্ত্ব। সাঈদ দেখিয়েছেন পশ্চিমের রাষ্ট্রনায়ক-চিন্তক-লেখক-সংস্কৃতি কর্মী পুবের দেশ ও সমাজগুলোকে হীন চোখে দেখেছেন, সেই দুই আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই। পুবকে তারা অসভ্য, বর্বর, বিশৃঙ্খল হিসাবে প্রচার করেছেন। যার ফলে পুবকে দখল করা এবং সেখানকার সমাজকে সভ্যভব্য করার উদ্দেশ্যে সেখানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে শাসন করার উস্কানি তৈরি হয় পশ্চিমের জ্ঞানচর্চায়। পুবের দেশগুলোয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করার কাজটি তাদের সমাজে জায়েজ রূপ পায়। আর এর প্রতি উপনিবেশিত মানুষদের সম্মতি উৎপাদনের জন্য তাদের ইতিহাস, জ্ঞান, সাংস্কৃতিক চর্চাকে হীন ট্যাগ দিয়ে মুছে ফেলা এবং তার বদলে উপনিবেশি শক্তির ইতিহাস ও জ্ঞানভাষ্য প্রতিষ্ঠা করার দরকার হয় যা জন্ম দেয় হেজেমনিক সম্পর্কের। পরিণামে দীর্ঘায়িত হয় উপনিবেশি শাসন। এটিই প্রাচ্যতত্ত্বের মূল কথা। কিন্তু এই জ্ঞানভাষ্যে পৌঁছার জন্য সাঈদ পশ্চিমের লেখকদের বিপুল পরিমাণ রচনার বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। সেগুলোর বিন্যাস ও অভিমুখ চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন প্রাচ্যকে দেখার এই দৃষ্টিকোন পশ্চিমের সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।
এহসান হায়দার: চিন্তাচর্চা এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্য অঞ্চলগুলো কী কী ধরনের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ করে বলে আপনি মনে করেন?
ফয়েজ আলম: পুবের চিন্তাচর্চা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী আচরণের একটি ঐতিহাসিক বিন্যাস ও সিলসিলা আছে। একে উপনিবেশি ক্ষমতাকাঠামোর নিরিখেও দেখা যায়। পশ্চিমের জ্ঞানচর্চার ভিত্তি ও ধরন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, চর্চা, প্রতীক, প্রতিষ্ঠানগুলোর ইচ্ছা—এইসব চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয় পুবের মানুষদের উপর। এটি যে কেবল উপনিবেশি আমলে ঘটেছে তাই নয়, এখনো চলছে। রাজনীতির কথাই ধর। বাস্তবে এর প্রয়োগটা কি রকম হয় তার দুএকটা নমুনা দেয়া যেতে পারে। যেমন, পশ্চিম মনে করে জনমানুষের শাসনের একটাই ধরন। সেটি হলো পশ্চিমের নির্দেশিত গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের আর কোন রূপ তাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য না। তুমি যদি ওদের পত্রপত্রিকাও লিখতে যাও তাহলে দেখবে লেখাটা কিভাবে সাজানো হবে, কি কি পয়েন্ট আকারে, সূত্র কিভাবে উল্লেখ করবে, ভূমিকা ও শেষে কি থাকবে এসবই বলে দেয়া আছে। অই পত্রিকায় লেখা পাঠাতে হলে এগুলো মানতে হবে।
ঐতিহাসিক হেজেমনিক সম্পর্কের কারণে পশ্চিমের ধারণাগুলো লুফে নেয় এখানকার এক শ্রেণির মানুষ। ফলে, তুমি দেখবে এখানকার কোনো পত্রিকা একই রকম নোক্তা তৈয়ার করছে লেখালেখির ব্যাপারে। বুদ্ধিবৃত্তিক লেখার ক্ষেত্রে এগুলো চিন্তাকে সীমিত করে। আমাদের অসচেতন সম্মতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমের লেখকদের বিভিন্ন তত্ত্ব বলশালী হয়ে উঠেছে এখানে। এসব তত্ত্বের অনেকগুলোই বিশেষভাবে ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব স্বীকার করে বিকশিত, পশ্চিমের চিন্তার ঐতিহ্য ও সমকালীন জীবন দর্শন হতে উদ্ভুত—যার সাথে আমাদের চিন্তার পরিষ্কার পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমের এইসব ধারণা, মতবাদ, তত্ত্ব যখন আমাদের শিল্পসাহিত্য চর্চায় প্রভাব ফেলে তখন তার মধ্যে গুরুতর অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়। এখন এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বহু লেখক এইসব প্রভাব ঠেকানোর জন্য সচেতনভাবে কাজ করছেন। ধীরে ধীরে হলেও ফিরে আমরা পাচ্ছি নিজেদের কণ্ঠস্বর ও বয়ান।
এহসান হায়দার: বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির দাসত্বকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে কীভাবে দেখেন?
ফয়েজ আলম: বুদ্ধিবৃত্তি বলতে কি বুঝব, কে বুদ্ধিজীবী এইসব বিষয়ে আমাদের এখানে পরিষ্কার ধারণা ছিল না। এখনো অনেকে মনে করেন যিনি লেখেন তিনিই বুদ্ধিজীবী। সাধারণভাবে এর মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। বিশ একুশ শতকে রাজনৈতিক সমাজ যখন ক্রমেই আগ্রাসী, ব্যক্তি ভয়াবহভাবে নিষ্পেষিত তখন অবদমিত গোষ্ঠী ও ব্যক্তির স্বার্থে পরিচালিত নির্দিষ্ট কিছু তৎপরতাকে বুদ্ধিবৃত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তার আলোকে নির্ধারিত হয় বুদ্ধিজীবীর পরিচয়। এন্টোনিও গ্রামসি বুদ্ধিজীবীর একরকম বিন্যাস দেখিয়েছেন, ‘প্রথাগত বুদ্ধিজীবী’ এবং ‘জৈব বুদ্ধিজীবী’ নামে আলাদা করে। এডওয়ার্ড সাঈদও বুদ্ধিৃবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবী নিয়ে আলাপ করেছেন তার ‘রিপ্রেজেন্টেশন অব দি ইন্টেলেকচুয়াল’ বইয়ে। আমি যতদূর জানি বাংলাদেশে এ বিষয়ে প্রথম বিস্তারিত বিশ্লেষণ হাজির করি আমি আমার ‘বুদ্ধিজীবী ও তার দায়ভার’ প্রবন্ধে। কালি ও কলম এটি প্রকাশ করে। পরে ২০০৬ সালে আমার ‘উত্তর-উপনিবেশী মন’ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। ওখানে বলেছি যে, বাংলাদেশে যাদেরকে বুদ্ধিজীবী বলা হয় তারা গ্রামসির প্রথাগত বুদ্ধিজীবী এবং ব্যক্তির অধিকার আদায় বা সংরক্ষণে বিশেষ কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন না, হাতে গোনা দুএকজন ব্যতিক্রম ছাড়া। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলোর সাফাই গেয়ে হালুয়া রুটির ভাগ পাওয়ার জন্য বহু লেখক-সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক কর্মীর উদ্ভব হয়েছে যাদের কাজ হলো রাজনৈতিক দলগুলোর কাজের প্রশংসা করা, স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর লুটতরাজ খুন রাহাজানীকে বৈধতা দেয়া। নানা কুযুক্তি দাঁড় করিয়ে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর অবিরাম প্রশংসা করে মানুষের মধ্যে সম্মতি উৎপাদন করা। এরাই হলো গ্রামসির অর্গানিক বুদ্ধিজীবী, যাদেরকে বলা যায় ক্ষমতার দাস, স্বৈরাচারের দাসবুদ্ধিজীবী।
এই বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর শাসনকে দীর্ঘায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, প্রকৃত মেধাবীরা নৈতিক কারণেই স্বৈরাচারকে সমর্থন করে না, শিল্পসাহিত্যে তেলবাজি-দলবাজির বিরোধিতা করে। দাস বুদ্ধিজীবী শ্রেণিটি এইসব মেধাবী সৃষ্টিশীল মানুষদেরকে ধ্বংস করার জন্য ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। দেশের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এরাই কায়েম করে স্বৈরাচারী ফ্যাস্স্টি পরিবেশ। ফলে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে প্রকৃত সৃষ্টিশীল মেধাবী মানুষের বদলে জায়গা করে নেয় অমেধাবী, নীতিভ্রষ্ট, দাস লেখক-সাহিত্যিক-শিল্পীরা। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি হঠাৎ করে হয়নি, বহু আগে তার সূচনা। এজন্য তুমি দেখবে স্বৈরাচারী শাসনকালে বড় মাপের কাজ হয় না বললেই চলে। গোটা পরিবেশটাই থাকে সৃষ্টিশীলতার বিরুদ্ধে।
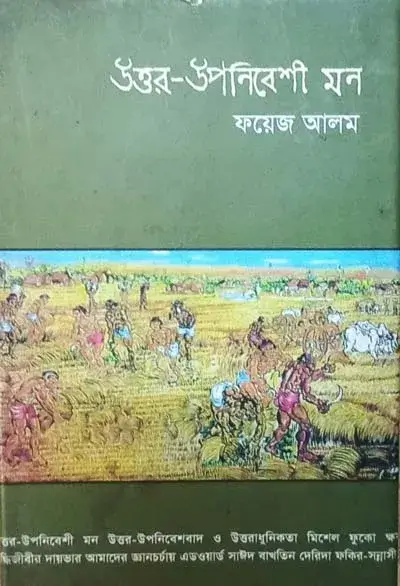
এহসান হায়দার: বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রকে কীভাবে দেখেন?
ফয়েজ আলম: এক লম্বা সিলাসিলার স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সঞ্চয়ের উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য। বার তেরশ বছর আগে লেখা হয়েছে চর্যাপদের মত সমৃদ্ধ রচনা। মধ্যযুগে রচিত হয়েছে ইফসুফ জুলেখা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদ্মাবতী’র মত অমর কাব্য। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির প্রাচীন সাহিত্যের চেয়ে কম সমৃদ্ধ নয় আমাদের পুরানা সাহিত্য। এমন সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে যে উচ্চতায় পৌঁছাটা স্বাভাবিক ছিল আমাদের সাহিত্যের জন্য সেটি কিন্তু ঘটেনি।
এর অনেকগুলো কারণ আছে। উপনিবেশি শাসনে প্রথম আমাদের ভাষা বদলে যায়, মূল ধারার বাংলার বদলে চালু হয় (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়) ‘সংস্কৃতানুযায়ী বাংলা’, যা শিখতে বুঝতে এবং মনে-মজ্জায় রপ্ত করতে বাংলাদশের মানুষের লম্বা সময় চলে যায়। নতুন ভাষার মধ্যে মিশে থাকা নদীয়া-শান্তিপুরের জনসমাজের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা, সমাজস্বভাব, ভারতীয় পুরাণের ঐতিহ্য, ধর্মবোধ, উপনিষদের চিন্তার চিহ্ন ঢুকে পড়ে আমাদের সাহিত্যে। এগুলো প্রায় সবই উত্তরভারতীয় ঐতিহ্যের অংশ। এর সাথে বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ সম্পর্ক নেই।
উপনিবেশি শাসন পর্বে সাহিত্যের যে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি হলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের লেখার মধ্য দিয়ে সেখানেও মুখ্যত পুরাণের ভারত আর ধর্মীয় আবেগই হাজির। আবার তিরিশের দশকে আসে পশ্চিমা আধুনিকতার ঢেউ। ফলে এই দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের জনমানুষের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা, সমাজস্বভাব, ঐতিহ্যিক স্মৃতি, বাসনা-কামনা কখনো বাংলা সাহিত্যে আসার সুযোগ পায়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলাদেশের লেখকরা দুধরনের ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় পুরাণ, ঋকবেদ উপনিষদের চিন্তা হতে উৎসরিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হতে বিশ শতকের চিন্তক-লেখক পর্যন্ত একটা ধারা। আর, এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইসলামী ঐতিহ্যের আলোকে শিল্প-সাহিত্য সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা। ভেবে দেখ, কি দুর্ভাগা জাতি আমরা! দুটো ধারাই ভিনদেশি ঐতিহ্যের ধারক। এগুলো নিয়ে মাতমাতি হলো, এখনো হয়। কিন্তু কেউ এই দেশের জনমানুষের বিকাশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অঙ্গীকার করে নাই। যারা ভারতীয় পুরাণমুখি হলেন তারা আবার নিজেদেরকে নিজেরাই ‘প্রগতিশীল’ হিসাবে প্রচার করলেন। এই দুইদল যে যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং করছেন তার কোনটাই বাংলাদেশের জনাসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। এ পরিস্থিতি আমাদের সাহিত্যকে বার বার দোনামোনায় ভুগিয়েছে, দিকভ্রান্ত করেছে। আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা কখনো ইসলামের, কখনো উত্তরভারতীয়, কখনো বা পশ্চিমা সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরেন। এই বিরোধাত্মক ঐতিহ্যিক-মানসিক পরিস্থিতি কোনমতেই বড় মাপের সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী নয়। এ সত্ত্বেও জসীমউদ্দিন, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত আলী, আবু ইসহাক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসসহ বেশকিছু মেধাবী সৃষ্টিশীলদের পেয়েছি আমরা।
মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয় সংবেদনা, উদ্দীপনা ও কাঁচামাল ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত ছিল। কিন্তু দু:খের সাথে বলতে হচ্ছে এ ক্ষেত্রে বড় মাপের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দরকারী জীবনবোধ, পরিমিতিবোধ, দার্শনিক দৃষ্টির বদলে আমরা লিখতে বসেছি অফুরান আবেগ আর আবেগ। এমন আবেগ যা দিয়ে এই সময়ের বাংলা সিনেমা হয়, বড় মাপের সাহিত্য হয় না।
স্বাধীনতার পরও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। বরং লেখকদের মধ্যে দলবাজি বেড়েছে। ক্ষমতাসীনদের তাবেদার মোসাহেব বেড়েছে। ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তি, প্রচারমাধ্যমকেন্দ্রিক মাফিয়াবাজি, প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক দলবাজি মেধাবী সৃষ্টিশীল মানুষদের প্রকাশের পথে বড় বাধা। রাজনৈতিক বিভাজনের সূত্রে গোটা জাতিকে দুভাগ করে ফেলা হয়। এবং রাজনৈতিক বিভাজনের এই ধারা অনুসরণ করে দলবাজ অমেধাবীরা শিল্প-সাহিত্যেও বিভাজন তৈরি করেছে। এখানে এখন স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক চৈতন্য নিয়ে সাহিত্যচর্চা অসম্ভব প্রায়। এইসব দলবাজ, চাটুকার অপদার্থরা সাহিত্য করতে না পারলেও মেধাবী, সৃষ্টিশীল, দলহীন ব্যক্তি লেখকের প্রকাশের পথ বন্ধ করতে পারঙ্গম; সরকারী সুবিধা বাগিয়ে নেয়া, পুরষ্কার হাতিয়ে নেয়া এসব কাজে সেরা। তোমার সমকালেই দেখ, মেধাবী এবং ভাল কাজ করেছে, কিন্তু দলহীন, এমন ক’জন লেখক প্রচার পেয়েছে কিংবা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে! এ সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর থেকে আমরা বেশ কিছু শক্তিশালী কবি, কথাসাহিত্যিক, চিন্তক পেয়েছি। তরুণ প্রজন্ম থেকে উঠে আসছে অনেক সিরিয়াস লেখক।
যতদিন আমরা এইদেশের জনমানুষের ঐতিহাসিক বিকাশের মূলধারা, তাদের ভাব ও ভাষা, তাদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যকে সাহিত্যে অঙ্গীকার করতে না পারব ততদিন মহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীন হয়েই থাকবে।
তবে, আমি আশার আলো দেখছি তরুণদের মধ্যে। তাদের অনেকে এইসব রাজনৈতিক বিভেদ, মাফিয়াবাজী, দলবাজি এড়িয়ে যেতে পারছে। ভাষার বাধাটাও বুঝতে পারছে অনেকে। অর্থাৎ উপলব্ধি করছে আমাদের লেখার ভাষা ‘প্রমিত বাংলা’ বাংলাদেশের নাগরিক মানুষদের কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশের জীবন রূপায়ণে সক্ষম। বাকি নব্বই-পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের চলমান জীবন আর তার চলমানতা ধরার উপযোগী নয়। তাই জনমানুষের ভাষায় সাহিত্যচর্চা নিয়ে সিরিয়াস কাজ করছে অনেকে। এরা নিজের শেকড়ের সন্ধানে অবিরাম সক্রিয়। তেমনি, প্রচারমাধ্যমকেন্দ্রিক দলবাজির দৌরাত্ম থেকে বাঁচতে বিকল্প পরিসর খুঁজে নিয়েছে ইন্টারনেটে। আমাদের এখন এই জায়গাটায় জোর দেয়া উচিত। ওয়েব ম্যাগাজিন, ফেসবুক, এইসব ইলেক্ট্রনিক পরিসরে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনশীলতার চর্চা দিন দিন বাড়ছে। এই মাধ্যমটি একদিন মূলধারার সাহিত্য চর্চার জায়গা দখল করবে। তখন আমাদের তরুণ লেখকরা শিল্প-সাহিত্যের ফ্যাসিজম এড়িয়ে এগেুাতে পারবে তাদের নিজ নিজ মহৎ সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়ে।
এহসান হায়দার: ভাষা মানুষের বিকাশ ও সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। বলা হয় বাংলা ভাষার আধুনিকায়ন ঘটেছে। তা থেকে বাঙালি জাতি কতটা সভ্যতার দিকে নতুন করে অগ্রসর হয়েছে বলে মনে করেন?
ফয়েজ আলম: সভ্যতার বিকাশে ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। প্রথমদিকে মানুষ অর্জিত জ্ঞান আরেকজনের কাছে তুলে দিত ভাষার সাহায্যে, যেটি ছিলো হাতেকলমে কাজ করার জ্ঞান। মানুষ যখন লিখতে শিখলো তখন সে পেলো হাতবদলি জ্ঞান, ভাষার মধ্যে যে জ্ঞান সঞ্চিত করে রাখা হয় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। হাতবদলি জ্ঞান সভ্যতার গতি অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়ে আজকের জায়গায় নিয়ে এসেছে। এর পেছনে ভাষার অবদান সবচেয়ে অনেক।
এ অর্থে এখানে মানব সভ্যতা বিকাশে আমাদের ভাষার অবদানও গুরুত্বপুর্ণ। কিন্তু যে কথাটা তুললে তুমি সেইটা কিন্তু হয়নি, বাংলা ভাষার আধুনিকায়ন হয়নি, একেবারেই না। বরং বলা যায় বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের নিয়মের দাস বানিয়ে তার প্রকাশ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। ভাষা হচ্ছে একটা মানবগোষ্ঠীর ভাব বিনিময়ের মাধ্যম, তাদের মুখের বুলি। সময়ের সাথে সেই মানুষগুলোর জীবনযাপন, পরিপার্শ্ব, সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। বদলে যাওয়া ভাব বহনের জন্য তাদের ভাষাও বদলাচ্ছে। অর্থাৎ ভাষা সচল জীবনের সাথে জড়ানো একটা ব্যাপার। তাই ভাষাকে জীবন্তই বলা যায়। এখন, এমন এক ভাষার কথা ধর যেটি কোনো মানবগোষ্ঠীর ভাষা না, যেটি কেউ মুখে বলে না। সে ভাষার সাথে জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই, মানবসভ্যতার প্রবাহমানতার যোগ নাই। সে ভাষাটিই হলো সংস্কৃত। সংস্কৃত কোনোকালে কোনো মানবগোষ্ঠীর মুখের ভাষা ছিলো না। তার সাথে জীবনের অবিরাম গড়ানের সম্পর্ক নাই, মানুষের আত্মার উম নাই। সম্পর্ক আছে স্থির ধর্মবিশ্বাস ও আচারপ্রথার। সেটি মূলত লেখার ভাষা, এখানকার কোন কথ্যরীতি থেকে নিয়ে তাকে স্থির অনড় রূপ দেয়া হয়েছিল। সেই ভাষায় মধ্যযুগে নানা ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছে, রামায়ণ, মহাভারতের মত কিছু লোককাহিনী পুরাণ ইত্যাদি লেখা হয়েছে। এমন একটি অনড় ভাষিক চাঁছ যখন গাঙের গড়ানের মত চলমান বাংলা ভাষার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় তখন তার গতি শ্লথ হয়ে আসে, প্রকাশ ক্ষমতা কমে যায়, জনমানুষের জীবনের সাথে তার সরাসরি সম্পর্ক ছিঁড়ে যায় চিরতরে।
এ ভাষার সর্বশেষ রূপ ‘প্রমিত বাংলা’ বাংলাদেশের নাগরিক মানুষদের কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশের জীবন রূপায়ণে সক্ষম। নব্বই-পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের চলমান জীবন আর তার চলমানতা ধরার উপযোগী নয়। একটু উল্টো করে ভেবে দেখ। জনমানুষের ট্যাক্সের টাকায় বানানো রাষ্ট্রীয় যোগাল যেমন ইস্কুল কলেজ পাঠ্যবই আর মিডিয়া ব্যবহার করে আমরা প্রমিত বাংলাকে চাপিয়ে দিয়ে রেখেছি সাধারণ মানুষের উপর। যদি এমন হয় কাল থেকে এগুলো চালাবে প্রকৃত জনমানুষেরা, যারা প্রমিত জানে না, কেবল জানে নিজের ভাষা, নিজের বাপমার ভাষা। তাহলে কি ঘটবে! আমরা প্রমিতভাষীরা নিতান্ত সংখ্যালঘু, বিভাষীতে পরিণত হব। আমরা মনে করি এমনটি ঘটবে না, বিশ্বাস করি রাষ্ট্রযন্ত্র সবসময় এক শতাংশ মানুষের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিয়ে রাখবে বাকি পঁচানব্বই শতাংশের উপর।
ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু এটি উল্টে যেতেও পারে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম যখন জনমানুষের সাধারণ কথ্যবাংলায় দেদারসে লিখছে। তো, প্রমিত বাংলাকে কোন যুক্তিতে আধুনিকায়িত ভাষা বলবো। তাই এ ভাষার আশ্রয়ে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে দিকও ঠিক থাকবে না। গণমানুষ থেকে কেবলই বিচ্ছিন্নতার দিকে এগুবে।
এহসান হায়দার: সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালি যা হারিয়ে ফেলেছে, তা পুনরুদ্ধার সম্ভব কী?
ফয়েজ আলম: অবশ্যই সম্ভব। গোটা বাঙালি জাতি বেশি কিছু হারায়নি। হারিয়েছে আমরা মধ্যবিত্তের সেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যারা নিজেদেরকে নাগরিকতার দেমাগের মধ্যে ঢুকিয়ে অনবরত ভিনদেশি ভাব, সংস্কৃতি, সাহিত্যের অনুকরণ করে চলেছি। এই দেশের আশি ভাগেরও বেশি মানুষ এর বাইরে রয়ে গেছে। হাজার হাজার বছরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের পরম্পরা ধারণ করে এগিয়েছে তাদের জীবন। সেখানে উপনিবেশি জ্ঞান ও সংস্কৃতি খুব একটা হানা দিতে পারে নাই। আমাদের চোখ ফেরাতে হবে তাদের জীবন ও তার যাপনের দিকে, যেখানে প্রায় অটুট রয়ে গেছে ঐতিহ্যিক সঞ্চয়।
প্রাক-উপনিবেশি ভাবচর্চা, সাহিত্য, গান, কিসসা, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজকাঠোমোর ইতিবাচক উপাদান, এইসব এখনো রয়ে গেছে জনমানুষের চর্চার মধ্যে। ভাব ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা কিছু আধিপত্য ঘটে গেছে তার বিউপনিবেশায়ন আর আমাদের জনমানুষের যাপনের ক্রমরেখার মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে আমরা ফিরতে পারি আমাদের নিজস্ব পথে।
এহসান হায়দার: বাংলাভাষার চর্চায় প্রমিত ভাষা যেমন জরুরি তেমনি আঞ্চলিক ভাষাও জরুরি। কারো গুরুত্ব কারো থেকে কম নয়। কারো কারো মতে প্রমিত ভাষা আঞ্চলিক ভাষার উপর চেপে বসে আছে। এই ধুয়ো তুলে পূর্ববঙ্গের ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বলে একটা বিভাজনরেখা তৈরি করা হচ্ছে; একইভাবে এদেশে ভাষাবিকৃতি ঘটানোও হচ্ছে। যিনি ঢাকাইয়া তিনি ঢাকার ভাষায় লিখবেন এটি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু যিনি নোয়াখালীতে জন্ম নিয়ে নোয়াখালীতে বড় হয়ে হঠাৎ ঢাকার ভাষায় লিখতে চান—সেটা তো সম্ভব নয়—সেটি হলে তো বিকৃতি করা হবে ঢাকাইয়া ভাষার। উদাহরণ হিসেবে বলি, জনৈক লেখক কর্পোরেট চাকুরে, তার জীবনযাপনে সবই কর্পোরেট, কিন্তু কেবল ফেসবুক/সোশ্যাল মিডিয়ায় আর লেখার ক্ষেত্রে আধা-ঢাকাইয়া বুলি কপচাচ্ছেন, এই বিষয়টি কী সাহিত্যচর্চা/চিন্তাচর্চা না-কি নিজের মস্তিষ্কবিকৃতির মধ্যে দিয়ে সমাজকে দূষিত করণ প্রক্রিয়ার নামান্তর—এতে নিজের দেশের একটি অঞ্চলের ভাষার বরং অসম্মান করা হয়—আপনার ভাবনায় বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কী?
ফয়েজ আলম: এই বিষয়টা নিয়ে লেখা একটা আস্ত বই আছে আমার: “ভাষার উপনিবেশ : বাংলা ভাষার রূপান্তরের ইতিহাস”, সংবেদ প্রকাশনা বের করেছে ২০২২ সালে। ছোট করে বলা মুশকিল। তবু চেষ্টা করি। “বাংলাভাষার চর্চায় প্রমিত ভাষা যেমন জরুরি তেমনি আঞ্চলিক ভাষাও জরুরি। কারো গুরুত্ব কারো থেকে কম নয়”—বিষয়টাকে এভাবে না দেখে আমি ভিন্নভাবে কিছু বাস্তবতার আলোকে দেখি। যেমন, (১) ‘প্রমিত বাংলা’ হলো নদীয়া-শান্তিপুরের কথ্যভাষার লিখিত রূপ, যার মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বানানো (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়) ‘সংস্কৃতায়িত বাংলা’র সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার পুরাই অটুট রাখা হয়েছে। প্রমিত বাংলা বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা নয়, কখনো ছিল না। এটি একশ বছরের অভ্যাসক্রমে আয়ত্ত করা বাংলাদেশের লেখ্যবাংলা। বাংলাদেশের জনসমাজ থেকে আসা প্রতিটি ছাত্রকে স্কুলে ঢুকে এই ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। (২) সাম্প্রতিক আলাপটা ‘প্রমিত ভাষা’ বনাম ‘আঞ্চলিক ভাষা’ না। আমার বিভিন্ন লেখায় বাংলা ভাষা বিকাশের ধারা তুলে ধরে দেখিয়েছি ‘আঞ্চলিক’ আর ‘প্রমিত’ ছাড়া আরেকটি বাংলা রীতি আছে যেটি বাংলাদেশের জনসমাজের সাধারণ কথ্যরীতি। সব অঞ্চলনির্বিশেষে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে এই সাধারণ কথ্যরীতি বিকশিত হয়েছে হাজার বছরের মূলধারার বাংলা ভাষা হতে, যে ভাষা চর্যাপদ থেকে শুরু করে উপনিবেশের আগে পর্যন্ত আমাদের লেখার এবং মুখের ভাষা ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চেষ্টায় ‘সংস্কৃতায়িত বাংলা’ তৈরির পর হাজার বছরের মূলধারার সেই বাংলা লেখা থেকে নির্বাসিত হলেও বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা হিসাবে টিকে থেকে বিকশিত হয়ে এ পর্যায়ে এসেছে। এটি কোন আঞ্চলিক ভাষা নয়, তথাকথিত ‘প্রমিত’ও নয়। এটি বাংলাদেশের সকল মানুষ বুঝে। আর সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ সাধারণ কথ্যরীতি হিসাবে এটি ব্যবহার করে। ‘প্রমিত ভাষা’ বলে এক কি দুই শতাংশ মানুষ, বুঝতে পারে তার চেয়ে কিছু বেশি লোক। নদীয়া-শান্তিপুরি কথ্যভাষা হওয়ার কারণে এবং বিপুল সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ জোর করে আত্তীকরণের কারণে সে ভাষা এখনো বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ বুঝে না, বলতে পারে না। মন থেকে গ্রহণও করেনি। এই দেশের মানুষের প্রাণের ভাষা হলো ‘সাধারণ কথ্যবাংলা’, যেটার কথা বললাম। জনমানুষের ট্যাক্সের টাকায় বানানো রাষ্ট্রীয় যোগাল যেমন ইস্কুল, কলেজ, পাঠ্যবই আর মিডিয়া ব্যবহার করে আমরা প্রমিত বাংলাকে চাপিয়ে দিয়েছি সাধারণ মানুষের উপর। প্রমিত বাংলা এদেশের মানুষের জন্য কৃত্রিম একটা ভাষা, আর ‘সাধারণ কথ্যবাংলা’ এদেশের মানুষের ভাষা। এই দুয়ের সরাসরি তুলনা করার যৌক্তিক ভিত্তি নাই। (৩) পূর্ববঙ্গ একটা উপনিবেশি ধারণা। উপনিবেশের সময় এটি চালু করা হয়েছে। আদিকাল হতে ‘বঙ্গ’ মূলত বৃহত্তর ঢাকা, বরিশাল এবং কুমিল্লা, নোয়াখালি ও ময়মনসিংহের অংশবিশেষ নিয়ে বিকশিত হয়েছে। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ দিল্লীর বিরুদ্ধ টিকে থাকার কৌশল হিসাবে চৌদ্ধ শতকের মাঝামাঝি বর্তমান বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের হাতছাড়া বিভিন্ন এলাকা যেমন ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে একত্রে বাঙ্গালা নাম দিয়ে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলেন। নদীয়া, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, প্রভৃতি জেলাগুলি বাংলাদেশের অংশ, এগুলো মিলে কোনমতেই আরেকটা বাংলাদেশ না। উপনিবেশি শাসনামলে ‘পুর্ববঙ্গ’ ‘পশ্চিমবঙ্গ’ ধারনাগুলোকে জনপ্রিয় করা হয়। ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চল নিয়ে তৈরি প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের বিপরীতে বাংলাদেশকে ‘পুর্ববঙ্গ’ বললে একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রকাশ পায় না। পুর্ববঙ্গের ভাষা বলে কোন ভাষা নাই। বাংলাদেশের ‘সাধারণ কথ্যবাংলা’ হলো হাজার বছর ধরে বিকশিত মূলধারার বাংলা ভাষা, আঞ্চলিক রীতিগুলো হলো তার এলাকাভিত্তিক বৈচিত্র। একে পুর্ববঙ্গের ভাষা নামে চিহ্নিত করার অর্থ নিজেই নিজের ভাষাকে খাটো করা।
প্রথমে যেটি বলেছিলাম, ‘প্রমিত রীতি’ আর বাংলাদেশের ‘সাধারণ কথ্য কথ্যবাংলা’ তর্কটাকে বুঝতে হবে এই বাস্তবতার আলোকে।
কাজেই ‘যিনি ঢাকাইয়া তিনি ঢাকাইয়া ভাষায় লিখবেন, যিনি নোয়াখালির তিনি নোয়াখাইল্যা ভাষায় লিখবেন’, বিষয়টা এমন না। দুজনই লিখবেন সাধারণ কথ্যবাংলায়, যেটি কোন অঞ্চল বিশেষের ভাষা নয়। এ ভাষাকে পুর্ববঙ্গের ভাষা বলে খাটো করার সুযোগ নেই। এটি মূলধারার বাংলা ভাষার সর্বশেষ রূপ।
অতএব তোমার প্রশ্নের মন্তব্য অংশটায় যা বলেছো অর্থাৎ আঞ্চলিক রীতিতে লিখে ভাষাকে দূষিত করা হচ্ছে কি না, এ রীতিতে লেখা মস্তিষ্কবিকৃতি কি না, সেটি খুব সুস্থমানসিকতার ও যৌক্তিক মন্তব্য নয়। আমি তো মনে করি প্রমিত একটা কৃত্রিম ভাষা, যার প্রকাশ ক্ষমতা অনেক কম, ভাষা হিসাবেও সেটি বেশ আড়ষ্ট। সে তুলনায় সাধারণ কথ্যবাংলা ভাব প্রকাশে অনেক বেশি সক্ষম, সাধারণ মানুষের প্রাণাবেগের খুব কাছাকাছি।
এহসান হায়দার: টিএস এলিয়ট পড়েন, কেন পড়েন এত পুরনো টেক্সট?
ফয়েজ আলম: আমি পড়ি দুটো কারণে। এক মানুষের তাবত অর্জনই ধারাবাহিক। যারা চিন্তাচর্চা করেন, শিল্পসাহিত্য করেন তারা সেই ধারাবাহিকতার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে সামনের পথ ভালো দেখতে পাবেন বলে মনে করি। টিএস এলিয়ট মানুষের অর্জনের ধারাক্রমের একটা বড়সরো বিন্দু। সেটিকে চেনা দরকার, জানা দরকার। এ ছাড়া, পশ্চিমের আধুনিকতার বোধে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ধারণা, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও নি:সঙ্গতা, আধ্যাত্মিকতার সংকট, জীবন যাপনে অর্থহীনতার বোধ হতে উত্তরণের অবিরাম প্রয়াস, এইসব বিষয় বুঝার জন্য এলিয়ট পড়তে হয়। তার ফর্মও কিন্তু অসাধারণ প্রভাবক। ভাষা, চিত্রকল্প, বাকভঙ্গী, রূপক-প্রতীকের ব্যবহার! এমন লেখা পড়া দরকার তো।
এহসান হায়দার: তত্ত্বীয় ক্ষেত্র এবং সৃষ্টিশীলতার জগত—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিতে চান কোনটিকে?
ফয়েজ আলম: এখন আর বুঝতে পারি না। বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালেখি শুরু করার পর মনে করতাম কিছু জরুরি বিষয়ে পরিকল্পিত লেখাগুলো শেষ হলে আর প্রবন্ধ লিখব না। শুধু কবিতা লিখব। এখন পরিষ্কার জানিই না। দুটোকেই প্রধান মনে হয়। তবে সৃষ্টিশীল কাজগুলো করার সময় যে অনির্দেশ্য সংবেদনা জাগে মনে, বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করার সময় তা হয় না। তখন মনে হয় কোন একটা গুরু দায়িত্ব শেষ হলো; আমাকে এটি করতেই হতো, করেছি। এও একরম আনন্দের তো বটেই।
এহসান হায়দার: আধুনিককালে বাংলা গদ্যভাষা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?
ফয়েজ আলম: গদ্য, পদ্য আর পীরিতির গান যাই বলো তার লেখার ভাষা হওয়া উচিত জনসমাজের কথ্যরীতির আদলে। একটু আগে এ বিষয়টি নিয়ে তো বিস্তারিত বললাম। বাংলাদেশে লেখার ভাষা হিসাবে চলছে নদীয়া শান্তিপুরের কথ্যভাষার সাজানো রূপ। আর আছে অঞ্চলভিত্তিক কথ্যরীতি। এ দুইয়ের বাইরে আঞ্চলনির্বিশেষে যে সাধারণ কথ্যবাংলা আছে সেটিই হওয়া উচিত আমাদের সাহিত্যের ভাষা। এ ভাষা বাংলাদেশের সকল মানুষের সাধারণ কথ্যরীতি হিসাবে বিকশিত হয়েছে হাজার বছরের মূলধারার বাংলা ভাষা হতে, যে ভাষা চর্যাপদ থেকে শুরু করে উপনিবেশের আগে পর্যন্ত আমাদের লেখার এবং মুখের ভাষা ছিল। এটি কোন আঞ্চলিক ভাষা নয়, তথাকথিত ‘প্রমিত’ও নয়। এটি বাংলাদেশের সকল মানুষ বুঝে। আর সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ সাধারণ কথ্যরীতি হিসাবে এটি ব্যবহার করে। অন্যদিকে, ‘প্রমিত’ নদীয়া-শান্তিপুরের কথ্যভাষা হওয়ার কারণে এবং বিপুল সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ জোর করে আত্তীকরণের কারণে সে ভাষা এখনো বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ বুঝে না, বলতে পারে না। মন থেকে গ্রহণও করেনি। এই দেশের মানুষের প্রাণের ভাষা হলো ‘সাধারণ কথ্যবাংলা’, যেটার কথা বললাম। সকল পড়ুয়া মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে সাহিত্যকে প্রমিত বাংলার কৃত্রিম বানোয়াট বাকভঙ্গি থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশের জনমানুষের ভাষা ‘সাধারণ কথ্যবাংলা’য় লিখতে হবে।
এহসান হায়দার: একালে সাহিত্য খানিকটা কৃত্রিম, জনবিচ্ছিন্ন, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত, আপনি এ বিষয়টিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেন?
ফয়েজ আলম: এ কালের সাহিত্য প্রধানত জীবন সম্পর্কিত কিতাবী ধারনার রূপায়ণ। এর ব্যতিক্রম আছে বলে আমি ‘প্রধানত’ শব্দটি ব্যবহার করলাম। তুমি দেখবে গল্প, উপন্যাসে যেসব চরিত্র সৃষ্টি করা হয় সেগুলোর সবই অল্প কিছু নির্দিষ্ট চাঁছের বানানো বলে মনে হয়। তারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়ালীউল্লাহ, তারাশঙ্কর প্রমুখের বইয়ের চরিত্রের ছায়া হয়ে ওঠে। কবিতায় চলছে আরো জটিল অবস্থা। বেশিরভাগ কবির কবিতা পরস্পর সম্পর্কহীন কিছু বাক্যের সমাবেশ মাত্র। যার একেকটা বাক্য একেক রকম ভাব-চিত্রকল্পের দ্যোতনা। তুমি পড়তে গেলে কবিতার সামগ্রিক অভিঘাত বা টোটাল ইফেক্ট বলে কিছু অনুভব করবে না।
এই যে অবস্থা এর একটা কারণ হলো এ সময়ের কবি সাহিত্যিকরা গড়পড়তায় জীবনকে গাঢ়ভাবে বুঝে নিয়ে সাহিত্য করার বদলে খ্যাতিমানদের কাজের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অমুক অমুক উপন্যাসের এই এই চরিত্র, বা বিখ্যাত কোন গল্পের প্লট, এসব দ্বারা খুব প্রভাবিত হয় বলে আমার মনে হয়। ফলে অইসব বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের আলোকে একটা ছাঁচ তার মাথায় আগেই তৈরি হয়ে যায়। আরেকটা বিষয় হল বাস্তব জীবনকে বুঝার আগে কিতাবের জগত থেকে শিল্প-সাহিত্যের নানা পদের তত্ত্ব তারা বুঝে ফেলে। তারপর মাথাভর্তি অইসব তত্ত্ব নিয়ে যখন সে সাহিত্য করতে যায় তখন জীবন সম্পর্ক যতটুকু অভিজ্ঞতাও বা থাকে সেটি বেরিয়ে আসে অইসব তত্ত্বের ছাঁচে ঢালাই হয়ে। অর্থাৎ অল্পসংখ্যক যে-কজন জীবনকে ঘনিষ্টভাবে দেখার সুযোগ পায় তারাও সে জীবনকে বুঝে নেয় তত্ত্বের নিরিখে। বলা যায় এ কালের গড়পড়তার সাহিত্য কিতাবী জীবনাভিজ্ঞার বয়ান।
কৃত্রিমতা ও জনবিচ্ছিন্নতার আরেকটি কারণ হলো ভাষার ব্যবহার। এ সময়ের বেশ ক’জন মেধাবী লেখকের গল্প উপন্যাসে দেখা যায় চরিত্রের অন্তর্গত দিকগুলো জাহির করার জন্য মনস্তত্ত্ব নিয়ে এত ঘোরপ্যাঁচের বয়ান সৃষ্টি করেন যে মনে হবে তিনি বা তার চরিত্রটি স্বয়ং এক মনস্তত্ত্ববিদ। তারপর আসে ভাষার প্রসঙ্গ। এরা ভাষাকে প্রধানত বোধ-অনুভুতির প্রকাশ হিসাবে নির্মাণ করতে চান। এজন্য প্রায়শই বিমূর্ত উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প-রূপক নিয়ে যে বিপুল কারিগরি, ঘোরপ্যাঁচ সৃষ্টি করা হয়—তাতে ভাষার মূল ক্ষমতা অর্থাৎ অন্যের সাথে যোগাযোগের গুণটাই হারিয়ে যায়। তখন পাঠকের কাছে প্লট, চরিত্র, অনুকাহিনী সবই দুর্ভেদ্য ফলত বানোয়াট লাগে।
আমাদের লেখার ভাষার কথাটাও এখানে আসে। ‘প্রমিত বাংলা’ বাংলাদেশের নাগরিক মানুষদের কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশের জীবন রূপায়ণের উপযোগী। বাকি নব্বই-পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের চলমান জীবন বয়ান করার ক্ষমতা এর নেই। প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃতায়িত বাংলা পরে প্রমথ চৌধুরীর চেষ্টায় তার চলিতরীতিতে রূপায়ন সবই হয়েছে বাংলাদেশের জনমানুষের কথ্যভাষাকে বাইরে রেখে। মূলধারার বাংলাভাষা বাদ দিয়ে যখন গদ্যের ভাষা ‘নির্মাণ’ করা হল তখনই সে ভাষায় লেখা সাহিত্যের সাথে বাংলাদেশের জনমানুষের জীবনের সরাসরি সম্পর্ক ছিঁড়ে গেছে চিরতরে। এমন এক ভাষার সাহিত্যকে তো জনবিচ্ছিন্ন, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাহীন মনে হবেই।
এহসান হায়দার: নূতন সাহিত্য কেমন হতে পারে?
ফয়েজ আলম: ‘কেমন হতে পারে নতুন সাহিত্য’ ধরনের নির্দেশনা দেয়া যায় না। সাহিত্য বুঝ আর মনের আবেগের মিশেলে তৈরি হয়, নির্দেশনা দিয়ে তার রোখ ফেরানো অনুচতি। তবে, ‘কেমন চাই নতুন সাহিত্য’ প্রসঙ্গে আমার বুঝ আর ইচ্ছার কথাটা বলা যেতে পারে। প্রথমত, এইদেশের জনমানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের মূলধারা চলমান সাহিত্যে আসেনি বললেই চলে। বাংলাদেশ ছিল প্রধানত অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর বৌদ্ধ মতাবলম্বী দেশ। সেই জনগোষ্ঠীর সমাজকাঠামো, ধর্মবোধ, সংস্কৃতি চর্চা ও ভাষায় অস্ট্রিক ঐতিহ্য আর বৌদ্ধ ধর্মের মিশেল। এরপর হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, আরবী ফারসি ভাষা ও দর্শনচিন্তা শামিল হয়েছে জনমানুষের যৌথ বিকাশের ধারায়। এই যে ঐতিহাসিক বিকাশের ধারাক্রম তার প্রতিফলণ আমাদের সাহিত্যে একেবারেই অনুপস্থিত। বাংলাদেশের জনমানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের ঐতিহাসিক সিলসিলা, তাদের ভাব ও ভাষা, তাদের জীবনযাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া জরুরি।
এদেশের জনমানুষের প্রতিদিনের যাপনের মধ্যে যে বাস্তব জীবন বহমান সেই জীবনকে সাহিত্যে তুলে আনতে পারল সেটি হবে প্রকৃত মহৎ সৃষ্টি। তত্ত্ব, মতবাদ, নন্দনতাত্ত্বিক তাফসিরে জর্জরিত আমাদের সাহিত্য। এর উপর আছে নানান ট্যাবু। কোন কথা বলা যাবে, কোনটা বলা যাবে না, কোন বিভাজন মানতে হবে, এইসব। সাহিত্য এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার।
ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা ও যুদ্ধোত্তর বাস্তব পরিস্থিতি সাহিত্যে আসা দরকার নির্মোহ বয়ানে। তেমনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষের জীবনের যথাযথ রূপায়ণ দরকার। ১৯৭১ পরবর্তী সময় থেকে ২০২৪ পর্যন্ত রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিফলন, যুগে যুগে স্বৈরাচারী শাসকদের দমনপীড়নে প্রায় অস্তিত্বহীন ব্যক্তির বাস্তবভিত্তিক নির্মাণ সবচেয়ে জরুরি।
ভাষার বিষয়টা ভাবতে হবে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে। নদীয়া-শান্তিপুরের কথ্য উপভাষার আদলে চালু হওয়া প্রমিত বাংলা এদেশের মানুষের আবেগ-অনুভূতি-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন প্রকাশে যথেষ্ট সক্ষম নয়, তেমনি সাধারণ পড়ুয়াদের বুঝ ও আবেগের কাছে পৌঁছাতেও পারে না। তাই নতুন সাহিত্যের ভাষা হওয়া দরকার বাংলাদেশের জনমানুষের সাধারণ কথ্যবাংলা। আমাদের ভাষায় আমাদের জনমানুষের জীবন ও তার যাপনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত হোক বাংলাদেশের নতুন যুগের সাহিত্য।
এহসান হায়দার: সাহিত্যে গোষ্ঠীবাদিতার বিষয়গুলিকে কীভাবে দেখেন?
ফয়েজ আলম: এখানেই আমি এক জায়গায় বলেছি যে, এই দেশে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির পথে গোষ্ঠীবাদিতা বা দলবাজিও একটা বাধা। এটি এত বাজে একটা ব্যাপার একেবারে গ্রামের মোড়লগিরি বা শহুরে পাড়ার চিঁছকে মাস্তানীর মত মনে হয়। এই যে অপদার্থের দলবাজি এর আবার দুটো রূপ আছে। একটা হলো নিছক সুবিধার জন্য দল গড়া। নিজেরা লিটলম্যাগ করে দলের লোকদের লেখা প্রকাশ করা, সাহিত্য পাতার সম্পাদক হয়ে অনুগত লোকদের প্রকাশ-প্রচার করা, একজন আরেকজনের প্রশংসা করা এবং দলছুট একাকী মেধাবী মানুষকে ঈর্ষাবশত প্রচারবঞ্চিত করে রাখা—এসবই হলো ঢাকার সাহিত্যের দলবাজির একটা রূপ। একান্ত ব্যক্তিগত ঈর্ষা, স্বার্থ, প্রচারপ্রচারণার সুযোগ লাভ, লেখকখাতায় নাম লেখানো এসবের জন্যই গড়ে তোলা হয় দল। এইসব দলের আবার একজন ডন থাকে, দুএকজন প্রধান চেলা থাকে। পুরা মাফিয়া স্ট্রাকচার আরকি।
গোষ্ঠীবাদিতার আরেকটা রূপ হলো মতবাদপন্থী দলপাকানো। বামপন্থী, ডানপন্থী, মধ্যপন্থী, রাজাকার, মুক্তির চেতনাপন্থী, এইসব। মজার বিষয় হলো এই দলগুলো নিজেদেরকে মতবাদভিত্তিক সমাবেশ হিসাবে ঘোষণা করলেও আসলে ভিতরে ভিতরে থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের মতলব। মতবাদের বিশ্বাস সামান্যই প্রতিফলি হয় তাদের লেখায়। গোষ্ঠীবাদিতার আরেকটা ভয়ঙ্কর দিক হলো মুক্তবুদ্ধির দলছুট মেধাবী লেখকদেরকে নানা ট্যাগ দিয়ে বর্জন করা, তার প্রচারের পথ রুদ্ধ করা। আল মাহমুদের মত কবিকেও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী মানুষ অভিহিত করে তাকে বর্জন করা হয়েছিল। অথচ যারা এ কাজ করেছে তারা নিজেরা সর্বাংশে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার বিরোধী। ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, নুন্যতম নাগরিক অধিকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা, এগুলোই তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সারমর্ম। যেসব লেখক-শিল্পী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে জাহির করে তাদের প্রধান কাজই হচ্ছে মানুষের এইসব অধিকার হরণ। কেবল তাই না, পছন্দের ক্ষমতাসীন দল ও রাষ্ট্র যখন মানুষের অইসব অধিকার হরণ করে, মানুষকে বোবা দাসে বানাতে উদ্যত হয় তখন এরা সামান্য হালুয়া-রুটির লোভে সেই ক্ষমতার দাসে পরিণত হয়। ক্ষমতাসীন দলের সকল কাজের বৈধতা দেয়ার প্রোপাগান্ডায় আত্মনিয়োগ করে। অথচ এরাই নিজেদেরকে প্রগতিশীল বলে প্রচার করে। দলবাজির শিকার হয়ে লেখাই ছেড়ে দিয়েছে এমন সৃষ্টিশীল মেধাবীর সংখ্যাও কম না। গোষ্ঠীবাদিতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষত্রিগ্রস্ত হয় দলহীন মেধাবী লেখকরা। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজে যেমন বহুমতের মেল গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি শিল্প সাহিত্যের ভিন্নমতকে নিয়মিত দমন করা হয়। সৃষ্টিশীলতার পথে এটি ভয়াবহ বৈরি এক পরিবেশ।
তবে, আমি আশা করছি তরুণরা এ অবস্থার অবসান ঘটাতে পারবে। তাদের অনেকে এইসব রাজনৈতিক বিভেদ, মাফিয়াবাজী, দলবাজি এড়িয়ে যেতে পারছে। প্রচারমাধ্যমকেন্দ্রিক দলবাজির দৌরাত্ম থেকে বাঁচতে বিকল্প পরিসর খুঁজে নিয়েছে ইন্টারনেটে। ওয়েব ম্যাগাজিন, ফেসবুক, এইসব ইলেক্ট্রনিক পরিসরে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনশীলতার চর্চা দিন দিন বাড়ছে। আমি প্রায়শই বলে থাকি এই মাধ্যমটিই একদিন মূলধারার সাহিত্য চর্চার জায়গা দখল করবে। তাহলে আমাদের তরুণ লেখকরা গোষ্ঠীবাদিতার নোংরা রাজনীতির বাইরে গিয়ে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির স্বপ্ন দেখতে পারবে।
এহসান হায়দার: ঢাকার সাহিত্যচর্চার বলয় থেকে প্রান্ত বা আঞ্চলিক সাহিত্যকর্মীর চর্চার ক্ষেত্র কতটা মুক্ত বলে মনে করেন?
ফয়েজ আলম: ঢাকার সাহিত্য চর্চার বলয় বাইরের সাহিত্যকর্মীদেরকেও অনবরত প্রভাবিত করে। দেশটা এখনো ঢাকাকেন্দ্রিক। প্রচার মাধ্যম, শিল্পসাহিত্যের সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পুরস্কার, আর্থিক প্রণোদনা এ জাতীয় সকল সুবিধার মূল সূতাটা হলো ঢাকায়। এ জন্য যিনি লেখক হতে চান তাকে ঢাকার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, ঢাকায় যোগাযোগ করতে হয়। তো, ঢাকায় যোগাযোগ মানে ঐসব দলবাজ ডনদের পাল্লায় পড়া। গোটা নেটওয়ার্কটা ঢাকা থেকে দূরপ্রান্ত অবধি সক্রিয়। এ অবস্থাটা ঢাকার বাইরের মুক্তবুদ্ধির সৃজনশীলতার চর্চার উপর সারাক্ষণই সক্রিয়। মফস্বলের লেখকদেরকে ঢাকার পত্রিকায় লেখার সুযোগ করে দিয়ে তার বদলে মফস্বলের সেই লেখকের উদ্যোগে সাহিত্য সভায় প্রধান অতিথি হওয়া, পুরস্কার নেয়া এগুলো তো হর হামেশাই হচ্ছে। কি আর বলব! এসব এখন এতটাই প্রকাশ্যে হয় যে, লজ্জশরমের কোন ব্যাপার থাকে না।
এহসান হায়দার: শিল্পকে অস্বীকার করা, নতুনকে না মেনে নেওয়া, দৃষ্টিভঙ্গির অনুদারতা না-কি এগুলিকে সাহিত্যের রাজনীতি বলবেন?
ফয়েজ আলম: শিল্পকে অস্বীকার করার দুটো ধরন আছে। একটা মতবাদে বিশ্বাসীসের কারণে সকল ভিন্নমতাবলম্বী মানুষদের সৃষ্টিকে পাইকারী হারে অস্বীকার করা। আবার ব্যক্তিগত ঈর্ষার কারণে দলের মাধ্যমে এ কাজটা করা। যেভাবেই হোক, ফলাফল একই, মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিকূল পরিবেশ।
নতুনকে মেনে না নেয়ার মধ্যে অনুদারতা আছে, অভ্যাসের প্রতি বিশ্বস্ততা আছে, গুরুত্বহীন হয়ে পড়ার ভীতি আছে। এমনিতেই মানুষ অপেক্ষাকৃত নিয়মিত বিষয়গুলোয় অভ্যাসের মধ্যে থাকতে চায়। তার অভ্যাস ও বুঝের বাইরের কিছু যখন এসে হাজির হয় তখন তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় বাতিল করার দিকে। যা তার গভীর বুঝের সাথে মিলে না তাকে সে ভুল ও বর্জনীয় মনে করে। এটি হলো একরকম মানবীয় স্বভাবের বিষয়, যেটি প্রায় সার্বজনীন। এটি মনের সঙ্কীর্ণতা, সহজাত রক্ষণশীলতা।
আবার, অনেকে সব বুঝেও নতুন মতকে বাতিল করতে চায়। এ যাবত পাওয়া তার অর্জনগুলো হারানোর ভয়ে নতুন ধারনা, মতবাদ, বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে। ব্যক্তিগত স্বার্থ হানি হওয়ার ভয় থেকেই নতুন সব কিছুকে বাতিল করতে চায়, চাপা দিয়ে পার হয়ে যেতে চায়। এটিই সাহিত্যের রাজনীতি। আমাদের এখানে সাহিত্যের রাজনীতির কারণে নতুন সবকিছুকে প্রথমেই বাতিল করে দেয়ার প্রবণতাটা বেশি জোরদার।
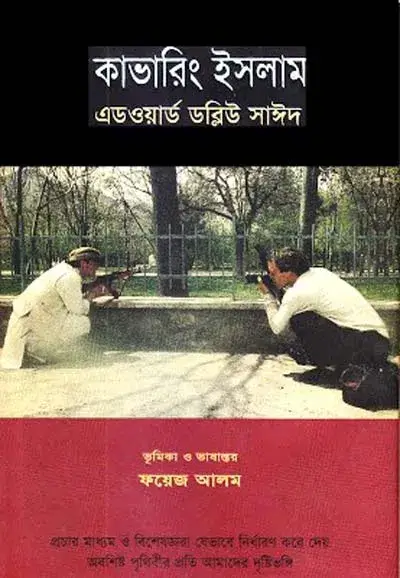
এহসান হায়দার: ভিনদেশি সাহিত্য পাঠ কতটা জরুরি বলে মনে করেন?
ফয়েজ আলম: ভিনদেশি সাহিত্য পাঠ খুব জরুরী। মানুষের কিছু বিষয় আছে স্থানিক। সেগুলোর নির্দিষ্ট ঠায়ঠিকানা আছে, ভূগোল ও পরিপার্শ্ব আছে। আবার কিছু অনুভুতি, ধারণা, বিশ্বাস সার্বজনীন। সার্বজনীন বিষয়গুলো অন্য সাহিত্যে কিভাবে রূপায়িত হচ্ছে সেটি জানার জন্য সেই সাহিত্য পড়া দরকার। আবার এ দুয়ের বাইরেও কোন কোন মানবিক বুঝ, মতবাদ, আন্দোলন, আলোড়নেরও সার্বজনীন রূপ থাকে। যেমন, উপনিবেশি শাসন, উত্তরউপনিবেশবাদ, নারীবাদ, এগুলো দেশে দেশে কোন দৃষ্টিভঙ্গি ও ধরনে সাহিত্যে জায়গা নিচ্ছে তা জানা প্রয়োজন। তাহলে এসব বিষয় নিয়ে লেখালেখি আরো গ্রহণযোগ্য ও শিল্পিত হবে। তাছাড়া, বিশ্বসাহিত্যে কারো কারো সৃষ্টি সমকালের বহু শিল্পিত প্রয়াসকে ছাড়িয়ে গিয়ে সার্বজনীন রুচি ও বুঝের ভিত্তিতেই মহৎ সাহিত্য হিসাবে বিখ্যাত হয়। সেগুলো তো পড়তে হবেই।
তবে বলে রাখা দরকার ইংরেজি সাহিত্যসহ গোটা ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে এসব লেখকের ও তাদের রচনার খ্যাতির পিছনে উপনিবেশি দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ছিলো। ইংরেজ উপনিবেশের শাসন আমাদেরকে শিখিয়েছে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য দুনিয়ার সেরা সৃষ্টি। প্রজন্মক্রমে এ জাতীয় কথা শুনতে শুনতে আমরা এক পর্যায়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সত্যিই দুনিয়ার সেরা। এরূপ উপনিবেশি হেজেমনিক সম্পর্ক থেকে যেসব সাহিত্যকে আমরা মহত্তম মনে করে আসছি সেগুলো পড়ার আগে অবশ্যই পুরা ধারণাটিরই বিউপনিবেশায়ন দরকার। মুক্ত, নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকে বুঝে নেয়া দরকার এসব ‘মহৎ’ সাহিত্য বাস্তবে কতটা মহৎ। তা না হলে কাফ্কার লেখা মাত্রই অবশ্যপাঠ্য মনে হবে, ব্রেখটের নাটক মাত্রই মনে হবে সেরা।
এহসান হায়দার: একজন সৃষ্টিশীল মানুষ আপনি, আপনার নিকট সমাজের দায়বদ্ধতার জায়গাটি ব্যাখ্যা করবেন কীভাবে?
ফয়েজ আলম: আমার বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালেখির শুরু একটা সামাজিক দায় বোধ থেকে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। একটু আগে আমরা এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছি। এখানে পুনরাবৃত্তি না হয়ে যায় আবার!
কম বয়সেই আমি বুঝতে পারি যে, আমাদের জ্ঞানজগতে চলমান বিভিন্ন ধারণা, আধিপত্যশীল জ্ঞানভাষ্য এদেশের জনমানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সিলসিলা ও বাস্তব জীবনযাপনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাঙালি তথা বাংলাদেশের জনমানুষের ঐতিহ্য হিসাবে যা সাধারণে চলমান জ্ঞানে পরিণত হয়েছে তার অনেক কিছুই অনুমাননির্ভর ধারণা থেকে সৃষ্ট। বিশেষ করে উনিশ বিশ শতকে ‘বাঙালির রেঁনেসা’র নামে যা কিছু নির্মাণ করা হয়েছে তার বেশিরভাগটাই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য থেকে রচিত। এইসব উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞানভাষ্য ও বয়ানের ধরণ, নির্মাণের কারণ ও ইতিহাস জানার পর আমি একটা গভীর সামাজিক দায় বোধ করি। মনে হয় এ বিষয়ে আমি যা জেনেছি বুঝেছি তা এদেশের আগ্রহী সচেতন মানুষদের জানানোটা আমার পবিত্র দায়িত্ব।
এই দায়বোধে তাড়িত হয়ে আমার সকল বৃদ্ধিবৃত্তিক শ্রম-ঘামের বেশিরভাগটাই ব্যয় করেছি এইসব উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞানভাষ্য ও বানোয়াট বয়ান নির্মাণের ইতিহাস ও লক্ষ্য তুলে ধরা এবং এইজাল ভেদ করে সত্যের কাছে পৌঁছানোর কাজে।
অন্যদিকে, আমি একই দায় বোধ করি ব্যক্তির কাছেও। চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসে একাকী ব্যক্তি ভয়াবহভাবে নিষ্পেষিত, বাকহীন। আমাদের রাজনৈতিক বিন্যাসটাই এমন যেখানে দলছুট ব্যক্তির অস্তিত্বরক্ষা কঠিন। এই নিষ্পেষিত ব্যক্তির অধিকারের জন্য, তার কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে দেয়ার জন্যও সবসময় একটা দায় অনুভব করি। এই দুই সামাজিক দায়বোধ থেকে আমার বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালিখি।
আমি মনে করি প্রতিটি লেখকই তার সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। যে সমাজে তিনি জন্মেছেন, তার খাবার আলো বাতাস উম ভোগ করে বেড়ে উঠেছেন সে সমাজের প্রতি তার দায় থাকবেই। লেখার সময় এই দায়বোধের কথা তার মধ্যে জাগ্রত থাকতে হবে।
‘শিল্পের জন্য শিল্প’ মার্কা কথাবার্তায় মনে করা হয় শিল্পীর কোন সামাজিক দায় নাই। সেক্ষেত্রে আমি বলব, তাহলে শিল্পীর প্রতিও সে সমাজের কোন দায়বোধ থাকার দরকার নেই। কে তাকে মারল, কাটলো, আহত করল সেটি দেখার দায় সমাজের আর থাকবে না। সমাজ এমন একটা সমাবেশ যেটি টিকে থাকার অন্যতম জরুরি উপাদান হলো পারস্পরিক দায়বোধ।
এহসান হায়দার: আপনার নিজের সাহিত্যচর্চার মূল্যায়ন আপনার নিকট কেমন, এবং আপনার সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে জানতে চাই…
ফয়েজ আলম: নিজে নিজের সৃষ্টির মূল্যায়ন করার কাজটা বেশ বিব্রতকর বলা যায়। তবে এগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আমার বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের ধরন, উদ্দেশ্য ও সামাজিক দায়বোধ নিয়ে তো আলাপ করলাম। কবিতা বিষয়ে কিছু বলি।
স্কুল-কলেজ জীবন থেকে সাহিত্য শুরু করলেও পরিণত চিন্তা নিয়ে সৃজনশীল লেখালেখি নব্বই দশকের গোড়া থেকে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। সমকালের কাব্য ভাষাকে আমার কাছে মনে হয় খুবই একঘেঁয়ে। সেই পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে একই ধরনে বাকভঙ্গি, বিমূর্তের স্বরচর্চা, উপমা-প্রতীক-রূপক নির্মাণে সাধারণ অর্থের বিপর্যাস ঘটিয়ে শব্দাতিরেক সাদৃশ্য আরোপ। এগুলো কবিকে একদিকে যেমন জীবন ও জগতকে দেখার একই রকম দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি ফর্মের দিক হতেও বাধ্যতামূলক অনুকরনশীলতার দিকে ঠেলে দেয়। পাশাপাশি উত্তরউপনিবেশি চিন্তিাচর্চার সূত্রে আমি বুঝতে শুরু করি উপনিবেশি ভাবাধিপত্যের মধ্য দিয়ে কিভাবে বাংলা কবিতা ইউরোপের শিল্পবোধ অঙ্গীকার করে একমুখি বিকাশের দিকে এগোয়। এর ফলে আমাদের কবিতায় গৌণ হয়ে যায় বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যিক ধারা এবং বাঙালির বাস্তব জীবনের যাপনের অনুসঙ্গগুলি। বরং ইউরোপের কবিতায় যে জীবন সে জীবনবোধকে আমরা আরোপ করতে থাকি আমাদের নিজেদের এবং পাঠকের মন ও মগজে। সেই সব অনুভুতি ইউরোপীয় শিল্পবোধের ফর্মের অনুকরণে রূপায়ন করতে গিয়ে আমাদের কাব্যভাষা এমন এক রূপ ধারণ করে যা আর সাধারণ পাঠকের সাথে যোগাযোগের উপযোগী থাকে না।
কবিতা লেখার শুরু থেকেই আমি এ অবস্থা থেকে বেরুতে চাই। আমার মনে হয় এ জন্য প্রথমেই দরকার নয়া একটি কাব্যভাষা। এমন কাব্যভাষা যেটি গড়পড়তার পাঠকের সাথেও যোগাযোগের উপযোগিতা হারাবে না, আবার কাব্যিক সংবেদনা ধারণেরও উপযোগী হবে। এ জন্য বাংলাদেশের মানুষের সাধারণ কথ্যভাষাকে কাব্যচর্চার সবচেয়ে উপযোগী বাহন বলে মনে হয়। কারণ এ ভাষাতেই রয়ে গেছে আমাদের জনসমাজের শত শত বছরের ভাব ও সংস্কৃতি চর্চার নির্যাস।
আমার প্রকাশিত কবিতার বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি। এর মধ্যে প্রথম বইটি প্রমিত বাংলায় লেখা। বাকি চারটি সাধারণ কথ্যবাংলায়। কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি, মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপন ও চিন্তাচর্চা, তার সমাজকাঠামো ও রাজনৈতিক বিন্যাসের বাস্তবতা সেঁচেই আমি আমার কবিতার রূপকল্প, বাকভঙ্গি, উপমা-চিত্রকল্প-রূপক-প্রতীক খুঁজে নিই। আমার পাঠকরা তার মধ্যে স্বচ্ছন্দ বোধ করে বলে মনে হয়।
কবিতায় আমার এই নিজস্ব স্বর আমার সাহিত্য চিন্তার সাথে যায়। আমি মনে করি সাহিত্যের ভাষা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষার আদলে গড়ে তোলা। লেখকের সামাজিক দায়বোধ থাকতে হবে। তিনি যে সমাজের মানুষ সেই সমাজ তার সাহিত্যে উপস্থিত থাকতে হবে। বাংলাদেশের জনমানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের ঐতিহাসিক সিলসিলা, তাদের ভাব ও ভাষা, তাদের জীবনযাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া জরুরি। আমার আশা আমাদের ভাষায় আমাদের জনমানুষের জীবন ও তার যাপনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত হবে বাংলাদেশের নতুন যুগের সাহিত্য।
এহসান হায়দার: জাতীয় সংস্কৃতির সর্বজনীন বয়ান, কবিতায় নতুন কাব্যভাষা—ইতিহাস, সংস্কৃতির পুনর্লিখন—বিষয়গুলি নিয়ে বলবেন?
ফয়েজ আলম: আলোচনার বিষয় হিসাবে এটি বিভিন্ন কারণে বেশ জটিল, গুরুত্বপূর্ণও। গত শদেড়েক বছর আগে থেকে ‘বাঙালিত্ব’, বাঙালির ‘ভাষা-সংস্কৃতি’ প্রভৃতি ধারণার একচ্ছত্র বাখানকার হয়ে দাঁড়িয়েছে কলিকাতার বুদ্ধিজীবীরা। মূলত উপনিবেশি শাসনের প্রশ্রয়ে ঘটে যাওয়া তথাকথিত ‘বাঙালি রেনেসা’র পর থেকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় কলিকাতার লেখক-সংস্কৃতিকর্মীরা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব ‘ইতিহাস-বর্জিত উদ্দেশ্যমূলক বয়ান’ উপস্থিত করে যাতে বাঙালির সকলকিছুর কেন্দ্র বলে দেখানো হয় পশ্চিমবঙ্গকে। শুধু তাই না, বহু সাম্প্রদায়িক আচার, প্রথা, প্রতীক, চর্চা চালিয়ে দেয়া হয় বাঙালি সংস্কৃতির নামে।
এ বিষয়টি বুঝার জন্য আমি কয়েকটি ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি পড়ুয়াদের নজর দাবী করব। প্রথমত, বাঙালি জাতি, জাতিত্ববোধ ও সংস্কৃতি মূলত বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমানায় গড়ে উঠা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। ফরিদুপুর-ঢাকা-বরিশাল-ময়মনসিংহ-কুমিল্লার অংশ বিশেষে যে প্রাচীন বঙ্গ রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল সেটিই বিবর্তিত হয়ে রূপ নিয়েছে আজকের বাংলাদেশে। এ বিষয়ে লিখিত ইতিহাসে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়ত, এখন থেকে বার-তেরশ বছর আগেও এ জাতি বঙ্গাল বা বাঙ্গাল হিসাবে পরিচিত ছিলো। যার উল্লেখ পাওয়া যায় চর্যাপদের কবি ভুসুকু পা’র লেখায়। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ নামক যে দেশটিতে আমরা বাস করছি এর মাটিতে এর সীমানাতেই বাঙালি জাতির উৎপত্তি ও বিকাশ। মধ্যযুগের শুরুতে সেই জাতি পরিচয়ে এসে যুক্ত হয় মধ্যএশিয়া, ইরান, ইরাক, আরব অঞ্চল থেকে দেশান্তরী হয়ে বাংলায় আসা প্রচুর মানুষ। তৃতীয়ত, সাহিত্যের সাক্ষ্য এবং ভাষার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি এও প্রমাণ করে যে প্রাচীন যুগ হতে বাংলাভাষাভাষী এলাকার পরিসর আরো বড় ছিল। বর্তমানে ভারতের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ নামের গোটা প্রদেশ, ত্রিপুরা এবং ঝাড়খন্ড, আসাম, উড়িষ্যার কিছু অংশ বাঙালির আবাসস্থল। তবে এরা রাজনৈতিকভাবে ‘বাঙালি’ জাতিগত পরিচয়ে শামিল হয় আরো অনেক পরে, চৌদ্দ শতকে। ১৩৫২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত অঞ্চল, উড়িষ্যা ও বিহারের কিছু অংশ নিজের শাসনে এনে গোটা অঞ্চলটার জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে ‘বাঙালি’ নামে পরিচিত করান। এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা সবশেষে, সাড়ে ছয়শ বছর আগে রাজনৈতিকভাবে ‘বাঙালি’ জাতি পরিচয়ের শরিক হয়।
উনিশ শতকে কলিকাতার বুদ্ধিজীবীরা বাঙালি সংস্কৃতির আলোচনায় এ তিন ঐতিহাসিক বাস্তবতা এড়িয়ে, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতায় তাড়িত হয়ে নিজেদের মনমত বয়ান নির্মাণ করেন। ভারতীয় পুরানের প্রচুর সাংস্কৃতিক আখ্যান, প্রতীক, রূপক এবং নিজেদের ধর্মীয় আচারপ্রথাকে বাঙালির সংস্কৃতি হিসাবে হাজির করে। খোদ বাংলাদেশের জনসমাজের আশি-নব্বই শতাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম, সাধারণ হিন্দু এবং বৌদ্ধদের বহু আচার-বিশ্বাস-চর্চা-প্রতীক বাদ দেয়া হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির বাঙালি হিসাবে প্রচার করা হয় বাংলাদেশের জনসমাজকে।
সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হতে সৃষ্ট বাঙালি সম্পর্কিত এই বয়ান পাঠ্যপুস্তক মারফত প্রচরিত হয়ে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে গোটা বাঙালি জাতিকে। একদল আছেন যারা বিশ্বাস করেন উনিশ শতকের কলিকাতার বর্ণহিন্দুরা হলো বাঙালি জাতিত্বের একচ্ছত্র মালিক। অতএব বাঙালি জাতিত্ব সম্পর্কে তারা যে বয়ান হাজির করেছে সেটিই সঠিক, আর সব ভুল, বিভ্রান্তি মাত্র। এর প্রতিক্রিয়ায় সংস্কৃতি বিষয়ে পাল্টা বয়ান তৈয়ার হয় যার মূল কথা হলো মুসলিম হিসাবে বাংলাদেশের মানুষ ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করবে। দুর্ভাগ্যজনক সত্যি হলো এ দুদলের কেউ-ই বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহ্যিক সঞ্চয় ও জীবন যাপনের বয়ানকে বাঙালি সংস্কৃতি হিসাবে হাজির করার চিন্তাও করেননি। হয় উনিশ শতকের কলিকাতার বর্ণ হিন্দুদের ‘বাঙালি বয়ান’, না হলে ইসলামী সংস্কৃতি এই দুই মেরুতে বিভক্ত হয়ে আছে সবাই। এ দুয়ের চাপে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং নিজস্ব কণ্ঠস্বরবিহীন হয়ে যাচ্ছে মূলধারার বাঙালি সংস্কৃতি অর্থাৎ মূল বঙ্গ ভূখণ্ডের মানুষের ঐতিহ্যিক সঞ্চয় ও জীবনাচার।
বাংলাদেশের জনসমাজের জাতীয় সংস্কৃতির যথার্থ বয়ান দাঁড় করাতে হলে প্রথমেই দরকার ইতিহাসের যথাযথ পাঠ। ইতিহাস থেকে আমরা জানি অস্ট্রিকরাই বাংলার আদি বাসিন্দা। গ্রীক ভূগোলবিদ ও ইতিহাসকারদের বিবরণে এরাই গঙ্গারিড়ি বা গাঙ্গাড়ি রাজ্যের মানুষ হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। আদিকাল হতে বাংলাদেশ ছিল একটি বৌদ্ধপ্রধান দেশ। ৪১৪ খ্রিস্টাব্দে ফাহিয়েন এবং ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙের বাংলায় সফরের বিবরণে তার সাক্ষ্য মেলে। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন তখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ছিলো বৌদ্ধধর্মের মানুষ, তারপর জৈন, এরপর অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে আছে পাল উপাধিধারী বৌদ্ধ রাজাদের ধারাবাহিক ইতিহাস, একেবারে ১১৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
সেনরা বা বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের সূত্রে মুসলমানরা আসার আগেই বৌদ্ধবাংলায় এদেশের জনসমাজের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি হয়ে গিয়েছিল যার বিবরণ আছে চর্যাপদে। তারও আগে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার আদিরূপ। সে ভাষাতেই চর্যাপদ লেখা।
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদি অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি আর বাংলাদেশে আগত মুসলমানদের ভাষা ও সংস্কৃতির মিলমিশের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠে বাংলাভাষা, যার নমুনা পাওয়া যায় মধ্য যুগের জনসাহিত্যে। একইভাবে বিকশিত হয় বাঙালি সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ। সুফিবাদী ইসলামের খোদাপ্রেমভিত্তিক অধ্যাত্বসাধনার সাথে এক হয়ে যায় বৌদ্ধদের জ্ঞানমুখি ধর্মসাধনা। চর্যাপদের বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মদর্শন ও ধর্মসাধনা মিশে আছে বাংলাদেশের জনমানুষের বাউল ও মুর্শিদী গানের ধারায়, যা আজো একইমাত্রার বিশ্বাস ও গভীর আত্মিক প্রেমের টানে সমান তালে বহমান। বাংলাদেশের জনমানুষের সংস্কৃতি মূলত স্থানীয় অস্ট্রিক-বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাথে বহিরাগত নানা দেশীয় মুসলমানদের সংস্কৃতির মেলবন্ধনে গড়ে উঠা। বৌদ্ধদের তুলনায় সংখ্যাল্প হলেও হিন্দু ধর্মানুসারী এবং স্থানীয় প্রকৃতি ধর্মের অনুসারীরাও ছিলো অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এইসকল মানুষের জীবনাচার, ভাব ও শিল্পচর্চার সম্মিলিত রূপই বাংলাদেশের জনসমাজের মূলধারার সংস্কৃতি। এটি এক ঐতিহাসিক সত্য, যা চেপে যাওয়া হয়েছে কলিকাতাকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চায়। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির রূপ খুঁজতে হবে এই পথে।
আমাদের ভাষা-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিকাশের সিলসিলা আর জনমানুষের জীবনযাপনের বাস্তবতার ভিত্তিতে জাতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ পরিস্কার বয়ানের মধ্যে নিয়া আসা দরকার। তা হলে অন্তত আমাদের পরের প্রজন্মের মানুষেরা আত্মপরিচয়ের দোনামোনা ও সঙ্কট হতে বের হয়ে আসতে পারবে। বড় মাপের শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্য আঁতুড়ঘরের জন্য তা অত্যন্ত জরুরি।
ফয়েজ আলমের সাক্ষাৎকার গ্রহণে: এহসান হায়দার

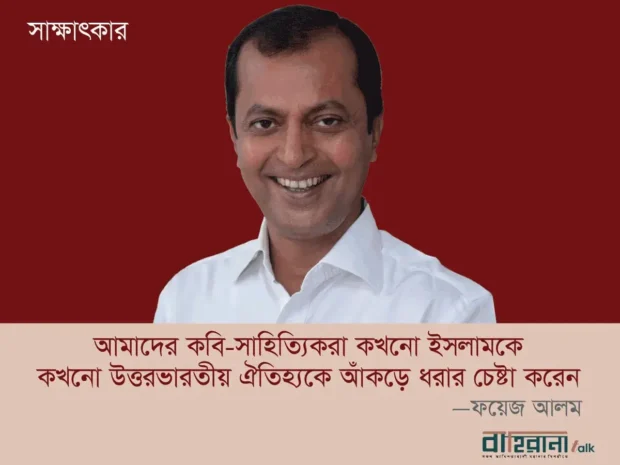
“ফয়েজ আলমের সাক্ষাৎকার: আমাদের সাহিত্যিকরা কখনও ইসলামকে কখনও উত্তর-ভারতীয় ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেন”-এ 9-টি মন্তব্য
অনেক বড় লেখা। সময় লেগেছে পড়তে। দারুণ একটা সাক্ষাৎকার। আমাদের অনেক লেখকের কলিকাতামুখি হীনমন্যতার কারণটা বুঝতে পারলাম। ফয়েজ আলমের সাক্ষাৎকার পড়লে বুঝা যায় এইসব লেখকরা সচেতনভাবে ভিন্ন সংস্কৃতির দাসত্ব করেন না. দাসত্ব করেন অসচেতনভাবে, না বুঝে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির বিরোধিতা করে গালাগালও করেন না বুঝে। এ জাতীয় আলোচনা চলতে থাকুক। তাহলে, একদিন এইসব লেখকের বোধবুদ্ধির উদয় হবে, তারা এই দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ভাষা সংস্কৃতির প্রতি টান বোধ করবে।
বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন ফয়েজ আলম। ভাল লেগেছে সাক্ষাৎকারটি। আমাদের দেশের একশ্রেণির লেখক কেন কলিকাতার লেজুড়বৃত্তি করে এসেছে এতদিনও সেটিও আলোচনায় এসেছে। তবে, বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতিতে উপজাতিদের সাংস্কৃতিক অবস্থান কি হবে সেটি পরিস্কার হয়নি।
বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন ফয়েজ আলম। ভাল লেগেছে সাক্ষাৎকারটি। আমাদের দেশের একশ্রেণির লেখক কেন কলিকাতার লেজুড়বৃত্তি করে এসেছে এতদিন সেটিও আলোচনায় এসেছে। তবে, বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতিতে উপজাতিদের সাংস্কৃতিক অবস্থান কি হবে সেটি পরিস্কার হয়নি।
অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক লেখা।
👌👌🌹🌹💖💖
বিস্তারিত পড়লাম। অনেক কিছু জানার সুযোগ হলো। ধন্যবাদ স্যারকে।
লেখকের অসাধারণ কথন আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে । সত্যিই তাই,কোলকাতাকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চার বলয় থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির মূলে ফিরে আসতে হবে!
দীর্ঘদিন পর একটি সুন্দর লেখা পড়লাম ।লেখার গভীরতা , শিল্প শৈলী ,তীক্ষ্ণতা অনেক অনেক ভালো। এমন লেখা আরো পড়তে চাই।
অনেক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। তবে অনেক তথ্যবহুল। দেশের সামাজিক সংস্কৃতি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে উঠে এসেছে। আমাদের দেশের অনেক কবি ও সাহিত্যিকরা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি কে যে আকরে রাখতে চায় তা লেখকের কথায় উঠে এসেছে। তবে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে ফয়েজ আলমের বিশ্লেষণ ভালো লেগেছে। সর্বোপরি অসাধারণ একটি সাক্ষাৎকার।
জনাব ফয়েজ আলম স্যার এর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সাহিত্য রচনা কারিদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। স্যার কে ধন্যবাদ সাহিত্য সংস্কৃতির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার জন্য।