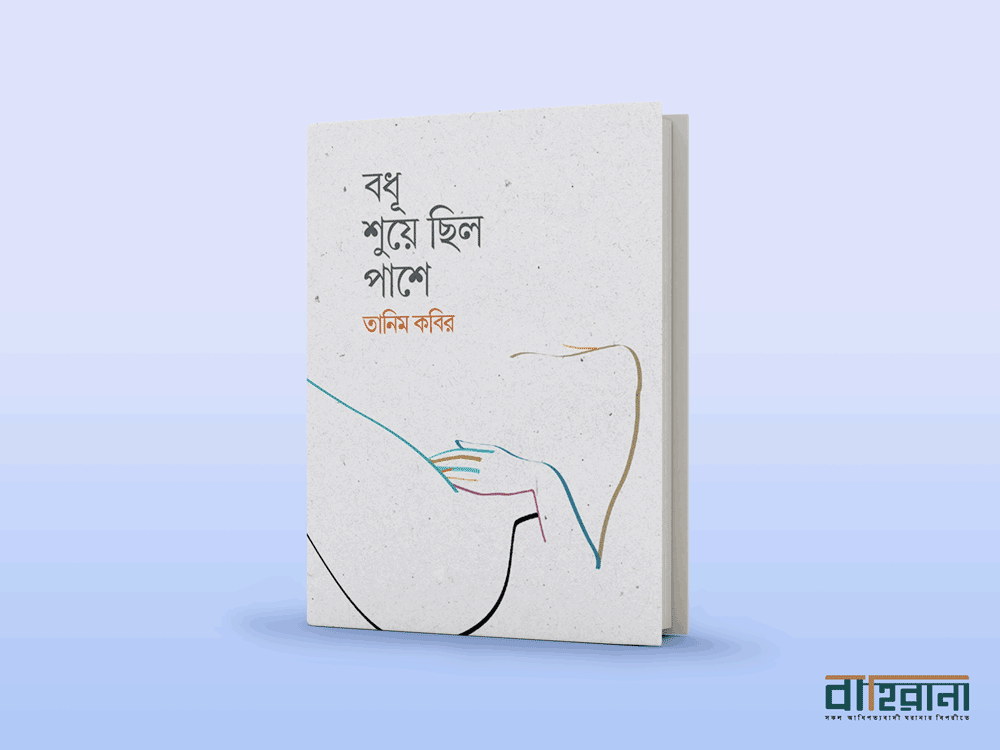একজন কবি যখন গল্প লেখেন তখন তাকে গল্পকারই হতে হয় অন্যকিছু নয়, কিন্তু যেহেতু তিনি কবি, তাই একটু বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন বলে ধারণা অনেকেরই। এরমধ্যে বহুলচর্চিত ধারণাটি হলো ভাষা, কবির গদ্যের ভাষা কাব্যিক হয়। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে এ কি অসুবিধা নয়? গল্প আর কবিতা দুইটি আলাদা শিল্প মাধ্যম, গদ্য নিজস্ব নিয়মে যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি কবিতারও নিজস্ব নিয়মবিধি আছে। কবি কি সেসব ভুলে কাব্যিক গল্প লিখবেন? নাকি গল্পই লিখবেন? তানিম কবির এর একটা ফায়সালা করেছেন, তিনি কবি হলেও গল্প লেখার সময় গল্পটাই লিখতে চান, কথাসাহিত্যের শর্ত মেনে। তবে, আরেকটু এগিয়ে, এই এগিয়ে বলতে নিজের নির্মিত ভাষায়। তানিম কবির ইতোমধ্যে তার গদ্যে আমাদের প্রাত্যহিকতার জগতের ভাষা নিজস্ব আঙ্গিকে নির্মাণ করে নিয়েছেন। তাই তার চরিত্রদেরকে আমাদের কাছে মনে হয় চেনা-জানা, কিন্তু আবার একইসাথে কবিতার রহস্যময়তাও লুকিয়ে থাকে তাদের মনস্তত্ত্বে, এখানে এসে চরিত্রগুলো আলাদা হয়ে যায়, নতুন হয়ে ওঠে। এ এক বাড়তি গুণ আরোপ করেছে তার নির্মাণে, তার গল্পবয়নে। “ইয়েলো ক্যাব”-এর পর তানিম কবিরের বধূ শুয়ে ছিল পাশে তার দ্বিতীয় গল্পের বই। বইটিতে গল্প আছে ছয়টি।
গল্পটি ছোট পরিসরে পৃথিবীতে চলা বাণিজ্যমূল্যের ধারণাটিকেই দাঁড়িপাল্লায় তুলে দেয়, বাণিজ্য ছাড়াও যে বস্তুর মূল্য থাকতে পারে তা তো এখন আর স্বীকৃত নয়, কিন্তু সেই মূল্য আছে, তাও খুব ভালোভাবেই, নাহলে তো ব্যবসা-ই দাঁড়াতো না। গল্পটির ফলবিক্রেতা যখন মেয়েটিকে তরমুজটি দিতে পারে না, তখন তার ভেতরের মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়াটি ভেঙে পড়ে, সে তখন সেটি পুনরুদ্ধার করতে প্রকৃত মূল্যের দ্বারস্থ হয়, আর তখনই গল্পটি সার্থক হয়ে ওঠে যখন সেই তরমুজটিই কিনতে চাওয়া তরুণকে সে এর অসীম একটি মূল্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে উৎসাহিত করে, কিন্তু মেয়েটিকে সে বীনামূল্যেই এটি দিয়ে দিতে চায়।
তানিম কবিরের বধূ শুয়ে ছিল পাশে বইয়ের প্রথম গল্পটির শিরোনাম “শহরতলীর বিচ্ছিন্ন ইঞ্জিন”। গল্পটিতে নামহীন একজন কথক আমাদেরকে জানায় সবকিছু। কথক, তার বন্ধু রবীন এবং তার স্ত্রী, কথকের স্ত্রী সুতপা (যার সাথে কথকের ডিভোর্সের আয়োজন চলছে)— এই চারজনের রসায়নে গড়ে উঠেছে গল্পের পটভূমি। ট্রেনের বিচ্ছিন্ন ইঞ্জিনও এখানে একটি চরিত্রের মর্যাদ পেয়েছে। ইঞ্জিনটি এখানে নগর জীবনের অসার সম্পর্কের প্রতীক। রবীনের বউ (যিনি এই সম্বোধনেই পরিচিত) আর রবীনের সাথে থাকবে না, সে দূরে কোথাও যেতে চায় এইকারণে তার টাকার প্রয়োজন, কথকের কাছে তাই সে ফোনকলে টাকা চায়। কথকের স্ত্রী অস্ট্রেলিয়া থেকে কথককে কল দিলে সে এই টাকা ধার চাওয়ার কথা জানতে পারে, সে কথককে টাকা দিতে নিষেধ করে। তখন ঘটনাসূত্রে কথকের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি তার স্ত্রীর সাথে স্টুয়ার্ট নামে একজনের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি। টাকা দিতে গিয়ে রবীনের বউয়ের সাথে যখন কথকের দেখা হয় তখন ঘটনা বিভিন্ন দিকে মোড় নিতে থাকে। রবীন তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের উত্তাপ ফিরিয়ে আনতে কীভাবে তার স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়ানোতে উত্সাহিত করে, এসব। বিবাহবহির্ভূত এই প্রেমের ঘটনাগুলো রবীনের বউ একটি বিচ্ছিন্ন ইঞ্জিনে বসে কথককে বলে। এক পর্যায়ে তারা খিঁলগাওয়ে কথকের পুরনো বাসস্থান একটি চিলেকোঠায় এসে উপস্থিত হয়, আর তখনই কথক একটি অস্বাভাবিক পরিণতির বিষয় আঁচ করতে পারে। খুবই স্বাভাবিকভাবে চলা গল্পের গতিপথ তখন এমনভাবে বদলে যায় যে এতক্ষণ পাঠ করার সময় যারা ভেবেছিলেন এরকমই তো স্বাভাবিক, তখন তারাই আবিষ্কার করতে শুরু করেন তারাসহ সবাই আসলে একটি সিজোফ্রেনিক বিচ্ছিন্ন ইঞ্জিনে চড়ে বসেছেন, যেখানে আর কাউকেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে আরেকটি সম্ভাবনাকেও তানিম কবির এই গল্পটিতে নিয়ে আসেন, বাস্তবতার পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা অবাস্তবের বীজগুলো সময়-পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে কিভাবে চারা হয়ে ওঠে তারই এক মনোলগ যেন গল্পটি।
আরেকটি গল্প “পিলখানার বিদ্রোহে ঐতিহাসিক প্রেম”-এ তিনি মফস্বলের এক তরুণ লেখকের ঢাকার এক মেয়ের সাথে প্রেমের সমান্তরালে খুবই দক্ষতার সাথে পিলখানা বিদ্রোলের ঘটনাপ্রবাহ আর এর প্রভাব তুলে এনেছেন। আশ্চর্য হতে হয় যে এত সিরিয়াস একটি ঘটনার মোকাবেলার সময় তানিম কবির তার হিউমার বজায় রেখেছেন। তখনকার অস্থির সময়ে সদ্য প্রেস থেকে আনা লিটলম্যাগ নিয়ে যখন ঢাকা বইমেলায় যাবে তরুণ লেখকটি, তখন সে প্রথমে পিলখানা বিদ্রোহের অভিঘাতটি বুঝতে পারে না, কিন্তু যখন সে ঢাকায় পৌঁছায়—ট্রেনে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ অবস্থায় সারা দেশে বিদ্রোহের গুজব শুনতে শুনতে আর এর অভিঘাতে—তার প্রেমিকার সাথে প্রতীক্ষিত দেখা হওয়া স্থগিত হয়ে যায়, বইমেলায় পৌঁছে যখন লিটলম্যাগচত্ত্বর নির্ধারিত সময়ের আগেই বন্ধ হয়ে গেছে দেখতে পায় তখন সে বিষণ্ণতার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। তার এই বিষণ্ণতা যেন বাংলাদেশের বিষণ্ণতম ইতিহাসটিকেই আবার নতুন করে জীবন্ত করে তোলে। গল্পটির শেষে দেখা যায় লিটলম্যাগ সম্পাদক লেখকটি আবার তার বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছে, তার এই যাওয়া শব্দটি ফেরা অর্থে নিলে যদিও সেটি আশা জাগায় কিন্তু তরুণ লেখকটির ভগ্নস্বপ্ন আশাটিকে লক্ষ্যহীন ভবিষ্যতের কাছেই নিয়ে যায়। এই ফেরা বাংলাদেশের ইতিহাসের বদলে যাওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে। এই বিডিআর বিদ্রোহ নিয়েই একদম ভিন্ন এক প্রেক্ষিতে ও নতুন এক জায়াগা থেকে বিশ্লেষণ পাই রাশিদা সুলতানার শূন্যমার্গে উপন্যাসে। রাশিদা সুলতানা এই উপন্যাসটি দিয়ে বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেন আমাদের।
“বেসরকারী ট্রেনের নিজস্ব জগৎ” নামক গল্পটি একজন সুদর্শন অস্থায়ী টিকেট চেকার সাইদুলের সঙ্গে নরসীংদির এক মেয়ের প্রেম নিয়ে। আবেগ আক্রান্ত কিন্তু নির্বিকার স্বীকারোক্তিতে সে প্রেমের পুরো সময়পর্বটার কথা বলে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্বীকার সাইদুল সম্পর্কে সে যা জেনেছিল তা যে সব ভুল ছিল একদিন একথা জেনেও তার কোনো গভীর ব্যথা জাগে না। একে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে সে। কিন্তু প্রেম চলাকালীন সময়ে সে যে বিনা টিকেটে ট্রেনে চড়ার ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিল সেটা হারিয়ে ফেলার একটা অতৃপ্তি তাকে ঘিরে ধরে মাঝে মাঝেই। এই ক্ষমতা হারানোর অতৃপ্তিটিকে মনে হতে পারে সাইদুলকে হারানোর প্রতীক হয়ে আসে এখানে, বা খোদ নিজের জীবনের উপর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার অতৃপ্তি থেকেই সে বেসরকারী ট্রেনের নিজস্ব জগৎ-এর গল্প বলে। সব শেষ হয়ে গেলেও যেহেতু অতীত এখনও তার কাছে হারানো ক্ষামতার মোহরূপের বেসরকারী জানালা হয়ে হয়ে ধরা দেয়, যা দিয়ে তাকালে তার জীবনকে বেদনার স্ফিটিকস্বচ্ছ অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়, যেটি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির শেষে আনন্দমুহূর্তস্মৃতি হয়েই জীবনের চলার রসদ জোগায়।
বইয়ের চার নাম্বার গল্পটি “ছাদ থেকে সদ্য ফিরে এসে তখন” গল্পটিতেও প্রেম আছে তবে এটি প্রেমকে প্রেমরূপে না বুঝতে পারার আখ্যান। বাবা হারানো সদ্য কিশোরী বয়স পেরুনো এক মেয়ে যে বাসায় থাকে সেটির ছাদের চিলেকোঠায় থাকা এক তরুণের প্রতি তার এক অচেনা কামনা নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্পটি। মেয়েটি দ্বৈতসত্তাবোধে আক্রান্ত, সে তার মৃত বাবার সাথে প্রায়ই কথা বলে আবার তার মা কারো সাথে প্রেম করছে বলে সন্দেহ করে। তার দ্বৈতসত্তার এসব ঘটনাবলি—যার কোনোটি কাল্পনিক যেমন মৃত বাবার সাথে কথা বলা, আবার কোনোটি বাস্তব যেমন মায়ের প্রেম নিয়ে সন্দেহ— থেকে জেগে উঠা তার ভেতরের অস্থিরতার নিভৃতি চায় যেন সে তরুণটির কাছে। কিন্তু তরুণটি তাকে বারবার ফিরিয়ে দেয়, আর এই বিনিময়ের দ্বন্দ্বটিকে লেখক একসময় পাঠকদের হাতেই সমর্পণ করেন। অস্থির মেয়েটিকে, গল্পটিকে অসমাপ্ত রেখে আমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে বলেন আপনারাই নিজেদের ভেতরে ডুব দিয়ে দেখুন মেয়েটির ভাঙাচোরা জীবনের সমাধান আছে কীনা। গল্পের উন্মোক্ত কাঠামোটি এভাবেই শিল্পের দ্বার অতিক্রম করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, নাহলে হয়তো এটি গতানুগতিকতার কাছে নুয়ে যেতো।
বইয়ের নামগল্প “বধূ শুয়ে ছিল পাশে”-এও “শহরতলীর বিছিন্ন ইঞ্জিন”-এর ডিভোর্সের জন্য অপেক্ষারত নায়কের দেখা পাই, তবে ভিন্নভাবে। এখানে কথক তার স্ত্রীর পুরনো প্রেমিকের সাথে পানাহার করে, তাকে আবার পুরনো প্রেমিকার কাছে যেতে উৎসাহিতও করে। এর সমান্তরালে আখ্যানে তার একজন বান্ধবী এবং সদ্য বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রেমিকার কথা আসে। আসে আরো কিছু পার্শ্বচরিত্র, তবে একসময় মনে হতে থাকে এই গল্পের কারোরই দাঁড়ানোর জায়গা নেই, সবাই অতল বিষণ্ণতা থেকে বাঁচতে খড়কুটোর মতো কিছু না কিছু আকড়ে ধরতে চাইছে। গল্পের নায়কও তা-ই, সেও মুক্তি চাইছে, কিন্তু কিসে মুক্তি তারা কেউই সেটা জানে না। তাই তার মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করা বান্ধবী দিপ্তীকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে কারে চড়ার পর যাত্রাপথেই গল্পের শেষ হয় উপসংহারহীনভাবে, তখন কারটির ক্যাসেট প্লেয়ারে একটা হিন্দিগান বাজতে থাকে। এই গল্পটিও স্বভাবে পূর্বোক্ত গল্পের মতোই, যেখানে পাঠকদের হাতে ছদ্ম উপসংহারের ভার দেওয়া হয়েছে, ছদ্ম বলছি এই কারণে যে গল্পটি আদতে এই দাঁড়ানোর জায়গাহীনতার কথাই বলছে জীবনের অস্থির এক পর্বের রূপকের মাধ্যমে। তাই কারে চড়ার পর রূপকটি সার্থক হয়, কিন্তু কারটি থামে না, আবার গান এক চলমানতার ইঙ্গিত দেয়, এসব বিষয় গল্পটিকে খোলা কাঠামোর মধ্যে ফেলে, তাই পাঠকরা এখানে নিজেরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। তানিম কবিরে গল্পে এই আঙ্গিক এক বিশেষ গুণ আরোপ করেছে বলা যায়।
শেষ গল্প “ওয়াটারমেলন”-এ আমরা এক ফলবিক্রেতা গল্পকথক আর এক তরুণীর দেখা পাই। তরুণীটির সাথে দোকানদারের দামদরের মাঝে তরমুজের মূল্য নির্ধারণ নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ঘটনাটির বর্ণনাকারী গল্পের প্রধানচরিত্রটি তরমুজটি কিনতে চায়। কিন্তু তখন তরুণীটিকে তরমুজ না দিতে পারার আক্ষেপে দোকানদার হঠাতই তরমুজের প্রকৃত মূল্য চেয়ে বসে, যা কিনা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। তরমুজটি তখন যেন বোর্হেসের “জহির” নামক মুদ্রার সমতুল্য এক রহস্য আর অবসেশন হয়ে ওঠে। “ওয়াটারমেলন” বোর্হেসের জগতের নয়, তবে তরমুজের মূল্য নির্ধারণের তুলনা দেওয়ার জন্য জহির-এর তুলনা এখানে যু্ক্তিযুক্ত মনে হলো। গল্পটি ছোট পরিসরে পৃথিবীতে চলা বাণিজ্যমূল্যের ধারণাটিকেই দাঁড়িপাল্লায় তুলে দেয়, বাণিজ্য ছাড়াও যে বস্তুর মূল্য থাকতে পারে তা তো এখন আর স্বীকৃত নয়, কিন্তু সেই মূল্য আছে, তাও খুব ভালোভাবেই, নাহলে তো ব্যবসা-ই দাঁড়াতো না। গল্পটির ফলবিক্রেতা যখন মেয়েটিকে তরমুজটি দিতে পারে না, তখন তার ভেতরের মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়াটি ভেঙে পড়ে, সে তখন সেটি পুনরুদ্ধার করতে প্রকৃত মূল্যের দ্বারস্থ হয়, আর তখনই গল্পটি সার্থক হয়ে ওঠে যখন সেই তরমুজটিই কিনতে চাওয়া তরুণকে সে এর অসীম একটি মূল্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে উৎসাহিত করে, কিন্তু মেয়েটিকে সে বীনামূল্যেই এটি দিয়ে দিতে চায়। তখন পণ্যসর্বস্ব বাজারব্যবস্থার ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কটি একভাবে সুফিবাদী আশেক-মাসুকের সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়ে যায়, ক্রেতা মেয়েটি এখানে মাসুক, আর বিক্রেতা আশেক, যেহেতু তরুণ ক্রেতাটি অনিচ্ছাসত্ত্বে তরমুজটি কিনতে চাচ্ছে তাই তার কাছেই বিক্রেতা তার পণ্যের আসল মূল্যটি বলতে চায়, যেহেতু সে একজন সাক্ষীও।
তানিম কবিরের বধূ শুয়ে ছিল পাশে গল্পবইটি আমাদের আধুনিক নগরসভ্যতার অবতলহীনতার, শেকড়হীনতার কথা শোনায় খুব সুকৌশলে। তার গল্পের শক্তির একটা বিরাট দিক হলো হিউমার। জটিল-কুটিল আর ভাঙাচোরা জীবনের মুখোমুখি হয়েও তার চরিত্ররা রসবোধ হারায় না, তাই পাঠকদেরকেও তারা ক্লান্ত করে না, উল্টো নিজেদের জগতে টেনে নেয়। অবাক লাগলেও, তার গল্পে প্রেম আসে শেকড়হীনতার রূপক হয়ে, যেখানে শেকড়হীনেরা মুক্তির জন্য ছোটে কিন্তু তাদের বাস্তবজীবনের রূপান্তর ঘটে না। কিন্তু এদতসত্ত্বেও তারা হার মানে না, যেকোনোভাবেই হোক তারা জীবনকে চালিয়ে নেয়, বেঁচে থাকার যুদ্ধ করে, বেঁচে থাকাকে মূল্য না দিয়েই। জীবনানন্দের আটবছর আগের একদিন-এর নায়ক ঘুমন্ত স্ত্রীর পাশ থেকে উঠে আত্মহত্যা করতে যায়, কিন্তু তানিম কবিরের “বধূ শুয়ে ছিল পাশে”র নায়কের স্ত্রী তার কাছেই নেই, মৃত্যুর বিরুদ্ধে এ যেন এক পরিহাস। তানিম কবির অস্তিত্ববাদী আবার উত্তরাধুনিক গন্তব্যহীন জীবনকে গড়ে তোলেন তার গল্পে।
বধূ শুয়ে ছিল পাশে
লেখক: তানিম কবির
বিষয়: গল্প
প্রকাশকাল : ২০২৩
প্রকাশক : বৈতরণী
দাম : ২৫০ টাকা।
বাংলাদেশের আশির দশকের গুরুত্বপূর্ণ কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ বাহিরানা Talk-এ কবি ও গল্পকার তানিম কবির-এর নাম উল্লেখ করেছেন।
বইটি কিনতে চাইলে:
বধূ শুয়ে ছিল পাশে-Bodhu shuye chilo pashe – বাহিরানা