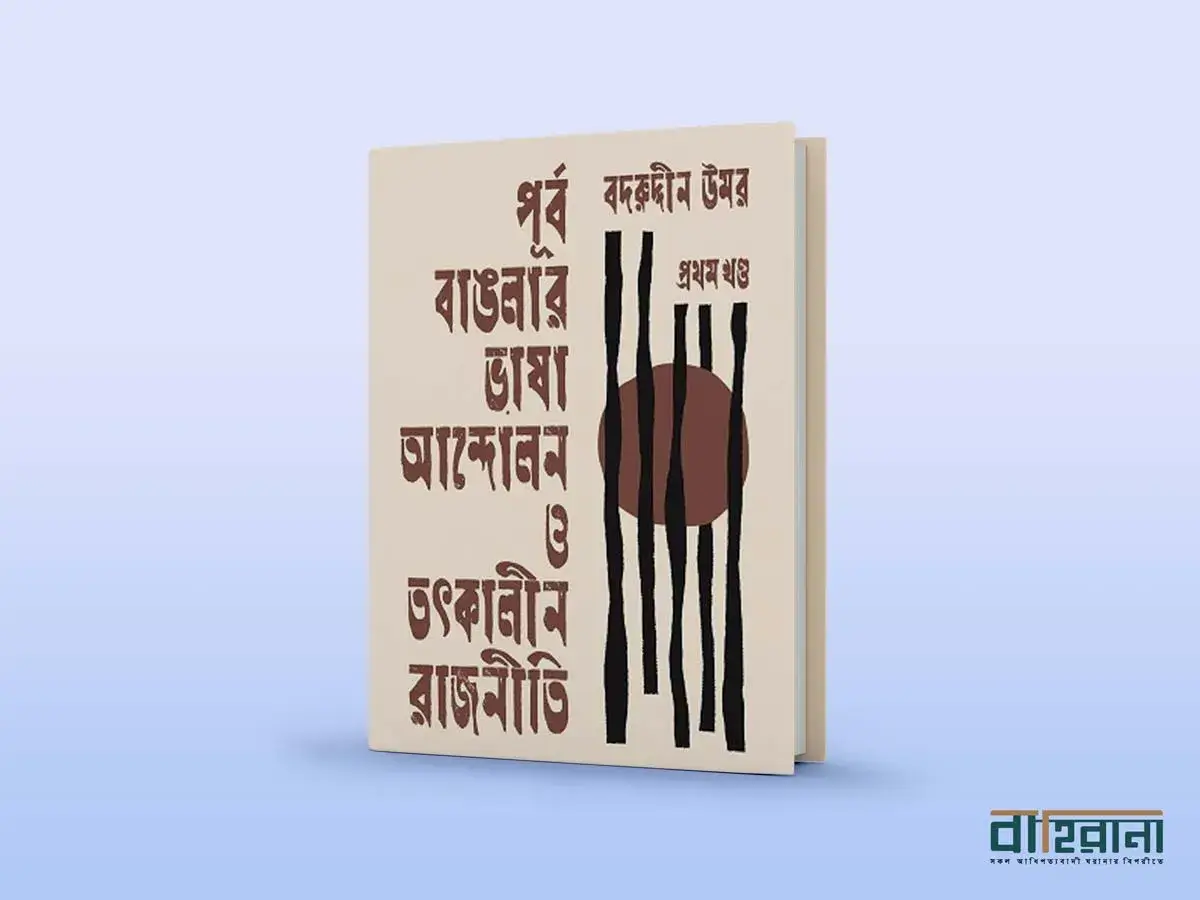যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ-এর রচয়িতা তিনখণ্ডে সমাপ্ত বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড) এখন পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের উপর গবেষণাধর্মী কাজের মধ্যে সর্ববহৎ ও একইসাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই গবেষণায় উমর ভাষা আন্দোলনকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং ভাষা আন্দোলনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকা রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। শোষণ বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস কীভাবে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপ নিয়েছিল তার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪৮ ও ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে। এই বিষয়টিই বদরুদ্দীন উমর স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।
বইটির আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে এতে থাকা বিরল সব দলিলপত্র। বইটি লেখা পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের সম্মৃদ্ধ সব নথি যেমন পার্টিগুলোর দলিলপত্র, ইস্তাহার, সাক্ষাৎকার, খবরের কাগজ ও সাময়িকি, গ্রন্থ—নষ্ট হয়ে যায়। এরপর উমরের কয়েকবছরের চেষ্টায় যে দলিলপত্রাদি উদ্ধার ও সংগ্রহ করা হয়, সেগুলো এই বইয়ে সংযোজিত হয়েছে। ফলে বইটিতে থাকা তথ্যগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এই সুদীর্ঘ কাজটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে, আলোচ্য লেখায় আমরা বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড) নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।
বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড) বইটির মতোই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই আছে। যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনকে দেখা হয়েছে। বইটি হলো আবুল মনসুর আহমদের আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। দুইটি বইয়ের পার্থক্য হলো উমর যেখানে গবেষণামূলক কাজ করেছেন সেখানে আবুল মনসুর আহমদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তার অভিজ্ঞতার বয়ান করেছেন।
বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড) বইয়ে প্রবেশের আগে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া ভালো হবে। ভাষা আন্দোলনের দুইটি পর্যায়, প্রথমটি ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ ও দ্বিতীয়টি ১৯৫২ সালের জানুয়ারি-মার্চ। ভাষা আন্দোলন মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও এর পেছনে ছিল রাজনৈতিক ভিত্তি এবং ক্রমেই সেটি ভাষা আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রামে যুগপৎভাবে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৪৮ থেকে কীভাবে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন রূপ নিল তার জন্য যদি মাঝের চার বছরের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অগ্রগতির খতিয়ান না দেখা হয় তাহলে ৫২ ও ৪৮কে আলাদা করে বোঝা সম্ভব নয়। এই কথাগুলোর সবই বদরুদ্দীন উমরের ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি প্রথম খণ্ডের ভূমিকার সারসংক্ষেপ। এর সঙ্গে এটাও উল্লেখ্য, যে, ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক দল ছিল শুধুমাত্র দুইটি, এক মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি। ফলে এই দুই দলের ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।
বদরুদ্দীন উমরের মতে, “একপ্রান্তে মুসলিম লীগ ও অন্যপ্রান্তে কমিউনিস্ট পার্টিকে রেখে পূর্ব বাঙলায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী সংগঠন।” এর সঙ্গে ভাষা আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে একে ইতিহাস বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলবে না, বরং একে দেখতে হবে, “পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস ও তার শ্রেণী চরিত্র; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণীসমূহের বিকাশ, বিন্যাস ও দ্বন্দ্ব; সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নীতি কর্মসূচির মধ্যে তার অভিব্যক্তি” (পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ), এসবের আলোকে। বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে এতোই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে একে বাদ দিয়ে আলোচনায় বাংলাদেশই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, “আমাদের দেশে সামগ্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনকে দিয়ে যেমন অস্পূর্ণ থাকে ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনাও সেই পরিস্থিতি বাদ দিয়ে দাঁড়ায় তাৎপর্যহীন এবং অন্তঃসারশূন্য। বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতির সাথে একই গ্রন্থিতে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত এবং সেই অনুসারে পরস্পরের সাথে নিবিড় ও গভীরভাবে একাত্ম।” (ঐ)
উপরের এই বিষয়গুলোতে নজর দিলে এখন আমরা বুঝতে পারব বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি বইটিতে তিনি কী বলতে চান ও কী বিষয় পরিষ্কার করতে চান। ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমাদের এখানে একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত আছে এবং সেটিই মূলধারার হয়ে উঠেছে, যে, ভাষা আন্দোলন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সেইকারণে শুধুমাত্র বাংলা ভাষার প্রতি আবেগের জায়গা। এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষতিকর দিকটি হলো এটা খণ্ডিত, এতে ভাষা আন্দোলন থেকে রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উমর এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছেন এবং ভাষা আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন—এর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক (পশ্চিম পাকিস্তান ও তৎসঙ্গে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিরোধীতা ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিল) দিকসহ। উমরের বহু পরে, উত্তর ঔপনিবেশিক বুকারজয়ী লেখক ও কবি বেন ওকরির কবিতার বই আফ্রিকার শোকগাথা-তেও এ বিষয়টির সাক্ষাৎ পাই আমরা। ওকরি রাজনীতি, ভাষাপ্রশ্ন ও জাতীয় ঐতিহ্যকে দেশীয় ও বৈশ্বিক দৃষ্টিতে দেখেছেন, ফলে উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসন তার খোলনলচে ফেলে উন্মুক্ত হয়ে ওঠেছে। একইচিত্র আমরা দেখতে পাই ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানপর্বে, সেখানেও সংস্কৃতি ও রাজনীতি ইতিহাসের মঞ্চে যৌথতা নিয়ে ওঠে এসেছিল। বদরুদ্দীন উমরের কাছ থেকে কোনো ইতিহাসকে খণ্ড-খণ্ড করে পাঠ করার মানসিকতা থেকে বের হওয়ার পাঠ নিতে পারি আমরা। এই এক ভাষা আন্দোলনই কত বিচিত্র দিকে যে ডালপালা ও শেকড় ছড়িয়ে রেখে পুষ্ট হয়েছিল তা তার এই বইটি না পড়লে সম্যকভাবে বোঝা কঠিন। সেই ছড়িয়ে থাকা শেকড় ও ডালপাতার মিলিতরূপই তো ভাষা আন্দোলন। বা যেকোনো আন্দোলনের মূলগত কথা এটাই।
বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)-এ অধ্যায় রয়েছে ১০টি। শেষে রয়েছে পরিশিষ্ট, তথ্য নির্দেশ, সাক্ষাৎকারের তালিকা ও নির্ঘন্ট। অধ্যায়গুলোর হলো, সূত্রপাত, প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম, পূর্ব বাঙলায় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, নাজিমুদ্দীন সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা, ভাষা আন্দোলন ও উত্তর ঘটনাপ্রবাহ—১৯৪৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের অগ্রগতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের উত্থান, আরবী হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র, পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ও পরবর্তী পর্যায়।
উমর বইটির সূচনা অধ্যায় শুরু করেছেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটন যখন তার ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ভাগবাটোয়ারার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তৎপরবর্তী গণ-আজাদী লীগ কৃত একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশের বিবরণ ও বিশ্লেষণ দিয়ে। এখানে লক্ষণীয় তিনি ভাষা আন্দোলনকে ৫২ বা ৪৮-এ না নিয়ে একদম শুরুতে ১৯৪৭-এ নিয়ে গেছেন, মেনিফেস্টোটির মূল ভাষ্য হলো, স্বাধীন দেশ হলেও অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি সম্ভব নয়। এরপরই আসে ডক্টর মুহম্ম শহীদুল্লাহর প্রসঙ্গ, কারণ ১৯৪৭ সালেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার অনুকরণ করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার আহ্বান জানান। তার এই অভিমত নিয়ে মুসলিম লীগ সহ কেউই প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রতিবাদ জানায়নি। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, তিনি জনগণের পক্ষে “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা” নামে একটি প্রবন্ধ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।
প্রবন্ধটিতে তিনি যুক্তি দেন এই বলে যে, পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের মাতৃভাষাই উর্দু নয়, “যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোনো কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য।” (ঐ) এরপর আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন তিনি “পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার ভাষা সমস্যা” শিরোনামে সেখানে বাংলাকে শিক্ষার প্রাথমিক ভাষা হিসেবে রাখার মত ব্যক্ত করেন। উমর জানান তখন একটি শ্রেণী উর্দুর সঙ্গে ধর্মের যোগ তৈরির চেষ্টা করছিল, কিন্তু শহীদুল্লাহ তার প্রবন্ধে ধর্মের প্রসঙ্গ একবারও আনেননি। কারণ তার মতে বিশ্বের মুসলমানদের ভাষা আরবী, উর্দু নয়। আমরা দেখতে পাই উর্দু বনাম বাংলা নিয়ে প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই শুরু করেছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
এরপর ছাত্র সংগঠন তমুদ্দীন মজলিস একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে, যাতে কাজী মোতাহার হোসেনসহ অনেকেই বাংলার পক্ষে তাদের যু্ক্তি তুলে ধরেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই বাদ প্রতিবাদ চলতে থাকে, যে ভাষা সমস্যার শুরু হয়েছিল ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ-এর এর কল্যাণে। এবার পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি কীভাবে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ তে পৌঁছাল সেই ঘটনাগুলো থেকে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা তুলে ধরা যেতে পারে,
পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি
ভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যলয় প্রাঙ্গনে প্রথম সভা
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ঢাকাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে।
করাচীর শিক্ষা সম্মেলন নিয়ে বাদ প্রতিবাদ
১৯৪৭-এর ৬ই ডিসেম্বর মর্নিং নিউজ পত্রিকায় জানানো হয় পূর্ব বাঙলা সরকারের মন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার তাদের জানিয়েছেন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।৭ ডিসেম্বর মন্ত্রী সৈয়দ আফজাল ও আবদুল হামিদের কাছে ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা নিয়ে ছাত্রদের মিছিল।
মর্নিং নিউজে উর্দুর সমর্থনে দীর্ঘ সম্পাদকীয় ও সিলেটের কিছু নাগরিকের পূর্বপাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট উর্দুর সমর্থনে স্মারকলিপি প্রেরণ
স্মারকলিপিতে তারা বলেন, “একদল লোক নিজেদের বিরাট সাহিত্যিক, শিল্পী ও পণ্ডিত বলে জাহির করে উর্দুর বিরুদ্ধে দারুণ প্রচারণা শুরু করেছে। পূর্ব বাঙলার লোকেরা একটি জাতি, এই উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা উর্দুকে জাতীয়তাবাদী ও বিদেশী ভাষা হিসেবে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশপ্রেমের মুখোশ পরে তারা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার জন্যে চারিদিকে তোলপাড় আরম্ভ করেছে।” (ঐ) এখানে তারা পূর্ববাংলা লোকেরা যে একটি জাতি হতে পারে তাই স্বীকার করছেন না।
প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড) থেকে উদ্ধ্বৃতি তুলে দিচ্ছি, “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আলাপ আলোচনা সভাসমিতি ইত্যাদি ব্যাপারে প্রথম থেকেই বেশ কিছুটা সক্রিয় হয়। তারা ১৫ই সেপ্টেম্বর ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা-না উর্দু?’ এই নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।” আর এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।
সোহরাওয়ার্দীর ঢাকায় না আসা ও শেখ মুজিবুর রহমান, মোশতাক আহমদ ও শামসুল হকসহ প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতার বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ
দেশভাগের পর সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানে আসেননি। এবং ১৯৪৮ এর জানুয়ারিতে শেখ মুজিবর রহমানসহ আরো কয়েকজন মুসলিম লীগ নেতা বামপন্থীরা যেন মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যে অংশগ্রহণ করতে না পারে তার জন্য কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন।
প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম
২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান গণ-পরিষদে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণ-পরিষদের ভাষা হিসেবে যুক্ত করা হোক বলে প্রস্তাব দেন।
জিন্নাহর ঢাকা আগমন
২৯শে মার্চ জিন্নাহ ঢাকায় পৌঁছান, হাজার হাজার মানুষ রেসকোর্স ময়দানে জড়ো হয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলন নিয়ে ছাত্রদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে জনতা তার সম্মানে কোনো ধ্বনি দেয়নি। জিন্নাহ তার বক্তৃতায় বিদেশি মদদ, ভাষা প্রশ্ন, কমিউনিস্টদের নিয়ে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের অধীন করার ষড়যন্ত্র বিষয়ে বলেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ-এর এই ভারতীয় ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আমরা প্রায় সব পাকিস্তানি বড় নেতা ও কর্মকর্তাদের মধ্যেও দেখি। রাও ফরমান আলী খান তার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আত্মস্মৃতি বাংলাদেশের জন্ম বইয়েও মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন।
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে জিন্নাহর তীক্ত কথাবার্তা: ২৪শে মার্চ সন্ধায় কমুরুদ্দিন আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, আবুল কাসেম প্রমুখদের সাথে জিন্নাহর সাক্ষৎ হয়। সাক্ষাৎকারটি অনুষ্ঠিত হয় সেক্রেটারি চিফ আজিজ আহমদের বাসভবনে। সেখানে তাদের প্রতি জিন্নাহ তিক্ত কথাবার্তা বলেন।
আমি আর এখানে বই থেকে ইতিহাস টেনে লম্বা করব না। আমার এই ঘটনাগুলো দেখানোর মূলে রয়েছে ভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ ও ১৯৫২-এর একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা ছিল না। যেখানে পুলিশের গুলিতে অনেকে শহীদ হন। বরং ১৯৪৭-এর পর থেকেই পূর্বপাকিস্তানের রাজনীতিতে বাংলা ও উর্দুভাষা প্রশ্ন একটি বড় চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। এই ভাষাকে কেন্দ্র করে বহুবার বাংলা ভাষার পক্ষের ছাত্রদের উপর স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় আক্রমণ করা হয়। গ্রেফতার করা হয়। পাল্টাদিকে মওলানা ভাসানীকে মুললিম লীগে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয় (ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা নিয়ে আবদুল হাই শিকদারের জানা অজানা মওলানা ভাসানী বইটিতেও অনেক অজানা তথ্য পাওয়ার যায়)। সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানে না ফেরায় তাকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের মধ্যে সুবিধাবঞ্চিত একটি শ্রেণী ক্ষমতায় ফিরতে চায়, কিন্তু সোহরাওয়ার্দী তাদের বিশেষ সাহায্য করতে পারেন না, এসব বহু বহু ঘটনা।
মুসলিম লীগের আবুল হাশিমের রক্ষণশীল হয়ে পড়া ও বামপন্থীদের সঙ্গে মুসলিম লীগের পথ অন্য দিকে মোড় নেওয়া। এই বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ভাষাষড়যন্ত্র কত গভীর হতে পারে সেটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা লেখার অক্ষরকে আরবী হরফে রূপান্তরের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি, “উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা বিরোধী চক্রান্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশ ধ্বংস করার অন্যতম উপায় হিসেবে তাঁরা বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু করেছিলেন।
বাঙলাদেশের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমানই ছিলেন এই হরফ পরিবর্তন প্রচেষ্টার ‘দার্শনিক’ এবং মূল প্রবক্তা।” (ঐ) এ নিয়ে শুরু থেকেই প্রতিবাদ জারি ছিল, এবং আমরা উমরের লেখায় দেখতে পাই সেটা থামেনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৪৯ সালেও এ নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান ও প্রতিবাদ সমাবেশ পর্যন্ত করে। ঐ একইসালে মৌলানা আকরাম খান-এর সভাপতিত্বে পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি গঠিত হয় বাংলা ভাষাকে প্রমিতকরণ, ব্যাকরণ, বানান, এবং বিদেশি ভাষার বাংলা প্রতিশব্দ যুক্ত করার উদ্দেশ্যে। এই বিষয়গুলোতেই আমরা বুঝতে পারি ষড়যন্ত্র কত আগে থেকে এবং কত গভীর ছিল।
পূর্ব বাঙলার রাজনীতি, কৃষক বিদ্রোহের ভাষা আন্দোলন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র আলোচনা
ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি: পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি বইয়ের মধ্যে রাজনীতির স্বতন্ত্র আলোচনার প্রকৃত সূত্রপাত আমরা দেখতেই দশম আধ্যয়ের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আলোচনায় এবং সেটাও মাউন্টব্যাটনের ভারতের ভাগভাটোয়ারার ঘোষণার পর থেকে। এর আগে ভাষা আন্দোলন ও রাজনীতির আলোচনা পাশাপাশি চলছিল। এখান থেকে রাজনীতি স্বতন্ত্র হয়ে আলোচনায় রূপ নিয়েছে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে সোভিয়েত প্রভাব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্য দেশগুলো ভারতভাগকে কী নজরে দেখেছে সেসবের কথা এখানে আমরা পাই। যেমন যুগোশ্লাভ পার্টির মুখপাত্রদের একজন দিয়াকভ ‘দি টাইমস’ পত্রিকায় ‘ভারতে নোতুন ব্রিটিশ পরিকল্পনা’ নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন এই বলে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কায়েমের ষড়যন্ত্রই বাস্তবায়িত হচ্ছে এর (ভাগভাটোয়ারা) মধ্য দিয়ে। এবং কংগ্রেস ও জওহর লাল নেহরু সরকার মাউন্টব্যাটনের ভাগভাটোয়ারা মেনে নেওয়ার ফলে বাম বলয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল উমর তাও জানান আমাদের।
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি
ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বীতিয় কংগ্রেসের সময় গৃহীত সিদ্ধান্তে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়। পার্টির সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রায় সবাই আত্মগোপনে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আত্মগোপনে কার্যক্রম চালানোর সময়েই “১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় ১২ই মার্চ মুসলিম লীগের গুণ্ডারা কাপ্তেন বাজার এবং কোর্ট হাউজ স্ট্রিটে অবস্থিত পার্টির প্রাদেশিক ও শহর অফিস আক্রমণ করে। কিছু বইপত্র ব্যতীত অন্য কোনো কাগজপত্র সেখানে না থাকায় আসবাবপত্র এবং বইগুলি তছনছ করে তার চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। ১৩ই মার্চ রণেশ দাশগুপ্ত এবং ধরণী রায়কে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু ভাষা আন্দোলনের অন্যান্য বন্দীদের সাথে তাঁরা দুজনেও ১৫ তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।” (ঐ)
তখন থেকেই সরকারী দমননীতি শুরু হয় কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দলের উপর। উমরের কথায়, বেশিরভাগ আক্রান্তের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মানুষজনই ছিলেন। এরপর আসে কৃষক বিদ্রোহের কথা ১৯৪৭-এর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বীতিয় কংগ্রেসের পর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে অনেকগুলো কৃষক বিদ্রোহ হয়। এরমধ্যে ময়মনসিংহের নেত্রকোণা মহকুমার সুসং দুর্গাপুরের হাজং প্রধান একটি এলাকায় বিদ্রোহ কয়েকবছরব্যাপী চলেছিল। এর কারণ কমিউনিস্ট পার্টির মনি সিংহ ও নগেন সরকারের কৌশলী নেতৃত্ব। এছাড়াও সিলেট, খুলনা, যশোর, রাজশাহীতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কৃষক বিদ্রোহের মতো ভাষা আন্দোলনও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, এ নিয়ে কিশোরগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের সবিস্তার বর্ণনা পাই মু আ লতিফের ভাষা আন্দোলনে কিশোরগঞ্জ ইতিহাস গবেষণা বইয়ে।
বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি প্রথম খণ্ড শুধু ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং একবার কি দুইবার ১৯৫১ সাল পর্যন্ত গিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির উপর আলোচনার সূত্রে। উমরের ভাষা আন্দোলন প্রথম খণ্ডের মূল কেন্দ্র ১৯৪৮ ও ১৯৫২ এর মধ্যেকার ৪ বছর সময়ে ঘটা ভাষা সম্পর্কিত রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং রাজনীতির উপর বাংলা ভাষা প্রশ্নের প্রভাব দেখানো। যে কাজ বদরুদ্দীন উমর খুব সফলতার সঙ্গেই করেছেন।
পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি
লেখক: বদরুদ্দীন উমর
বিষয়: প্রবন্ধ, গবেষণা
প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ১৯৭০
বাতিঘর সংস্করণ: ২০২৫
প্রকাশক: বাতিঘর
দাম: ১০০০ টাকা।
পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড) বইটি কিনতে চাইলে