মোস্তাক আহমাদ দীনের সাক্ষাৎকার
গত শতকের নয়ের দশকের কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক মোস্তাক আহমাদ দীন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক সৃজনশীল ও মননশীল—গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। জন্ম সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায়, ১৯৭৪ সালে। তাঁর লেখায় ভাষার শৈল্পিকতা, দর্শনচেতনা ও মানবিক সংবেদন একসাথে মিশে যায়। কবিতা, প্রবন্ধ ও গবেষণার ক্ষেত্র—সব জায়গাতেই তিনি দেখিয়েছেন গভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি ও শিল্পবোধ। বাংলা কবিতার ভাষা ও ভাবের রূপান্তর নিয়ে তাঁর নিরন্তর অনুসন্ধান তাঁকে দিয়েছে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য।
তাঁর কবিতার বই কথা ও হাড়ের বেদনা, যা প্রকাশের পরই পাঠকমহলে সাড়া জাগায় ভাবনাগত গভীরতা ও নতুন কাব্যভাষার জন্য। মূলত এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি সমালোচক ও কবিতাপ্রেমিদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো—কবিতা যাপন, মননচিন্তা বিবেচনা, ভিখিরিও রাজস্থানে যায়, মাটির রসে ভেজা গান, মাটির বইয়ের পাতা, আটকুঠুরি, বাঙ্গালাদেশে যে সকল দুর্ব্বৃত্ত জাতি প্রভৃতি।
কবি মোস্তাক আহমাদ দীনের রচনায় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানবজিজ্ঞাসা মিলেমিশে তৈরি করে এমন এক বৌদ্ধিক নন্দনচিত্র, যা আজকের বাংলা সাহিত্যচিন্তাকে করে তোলে আরও প্রখর ও সমৃদ্ধ।
বাহিরানা Talk-এ আমার সঙ্গে মোস্তাক আহমাদ দীনের সাক্ষাৎকার-এ উঠে এসেছে বাংলাকবিতার নানান বাঁক, খণ্ড খণ্ড মেঘপূর্ণ তুলোর মতোন ঘটনা, যেখানে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের সুফি কবিতার চর্চা এবং বাংলাদেশের সাহিত্যের অদ্ভুত ঘোঁট এবং সৌকর্যও।
বাহিরানা Talk-এ প্রকাশিত সব লেখক, কবি ও চিন্তকদের সাক্ষাৎকার পড়ুন।
এহসান হায়দার: আপনার ছেলেবেলায় বেড়ে ওঠার সময় সম্পর্কে জানাবেন?
মোস্তাক আহমাদ দীন: ছোটোবেলায় রাতে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে বসে কাঁদতাম, দীর্ঘ সময় ধরে অবিরাম সেই কান্না— সকালবেলায় মা বলতেন—সে তার বাবার জন্য কাঁদে। বড় হয়ে শুনেছি, বাবা ব্যবসার কাজে বেশির ভাগ সময় ঢাকায় এবং মাঝে
মাঝে সিলেটে থাকতেন। ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে বসলে এবং সেইসময় বাবা কাছে থাকলে নাকি পাশে টেনে নেওয়ামাত্রই কান্না বন্ধ হয়ে যেত আমার। কিন্তু বাবা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন সেই চার বছর বয়সে। আমার মনে পড়ে, মারা যাওয়ার পরের দিন বাবার খয়েরিরঙা ব্যাগের বাইরের পকেট থেকে কতগুলি সিকি ও আধুলি বের করে সবাইকে দিলেন—আমাকে একটু বেশিই দিয়েছিলেন—তাতেও বাবার জন্য হাহাকার এতটুকু কমল না। তবে, তার কিছুদিন পর থেকে খেলাধুলার দিকে মন চলে গেল, সবধরনের খেলাই খেলতাম, সামান্য সাফল্যেও আনন্দ হতো। এরপর, আমাদের ঘরের ভেতরের টানা ছাদে একদিন প্রচুর বইপত্রের খোঁজ পেলাম, বুঝি আর না বুঝি নানারকম নিষিদ্ধ-প্রসিদ্ধ বই পড়তে লাগলাম। তবে আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায় লেখা বাবার সংগ্রহের কিতাবগুলি পড়তে পারতাম না বলে শুধু নাড়াচাড়া করতাম, শূন্যতা আনন্দে ভরে উঠতে লাগল। আশেপাশের পাঠাগার থেকে আরও বই এনে, কখনো কখনো নিজে বই কিনেও পড়তে থাকলাম। সেই যে বইপড়ার নেশা শুরু হলো, আর কমল না।
তবে বইপড়ার পাশাপাশি ছেলেবেলার আরেকটি ভালোলাগার ব্যাপার ছিল একা একা গ্রামের ভেতরের রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি। দুপুরবেলাটাই ছিল বেশি উপভোগ্য। কত ধরনের গাছপালা, কত প্রকারের মর্মর আওয়াজ, পাখির ডাক, ব্যাঙ আর কীটপতঙ্গের ডাক, গোপাট, পুরকায়স্থবাড়ির দেওলা-লাগা দিঘি, পালহাটির বইট্টা, ছিনাউরার কবরস্তান, আদুবাড়ির বিরাট তেঁতুল গাছ, আতিক উল্লার লম্বা নারকেল গাছ (যার চূড়ায় উঠলে নাকি পঞ্চাশ মাইল দূরের মর্মর পাথরে তৈরি পাগলার মসজিদ দেখা যেত), গ্রামের দুই বংশীধারীর তীর্থস্থল শিমুলতলা—এইসবই ছিল আমার পথহাঁটা জগৎ। ফলে, পরবর্তীসময়ের জীবনানন্দ দাশ আর বিভূতিভূষণের লেখাগুলো সেই স্মৃতি উসকে দিত।
আর, বিষয় আর পট-পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও প্রিয় হয়ে উঠল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দেবেশ রায় ও হাসান আজিজুল হকের কয়েকটি দুপুরপ্রধান গল্প। রফিক আজাদসহ অনেক লেখকের যেমন রাত্রি, সেরকম আমার চিরকালের আবিষ্টতা হলো দুপুর। ভালোবাসার ভয়ের শিহরনের সেইসব দুপুরগুচ্ছ। এই দুপুরই আমাকে কতবার আত্মঘাতী গ্লানির মুখোমুখি করেছে আর অদৃশ্য ছেলে-ধরা খোঁজকরের হাতে হারিয়ে যেতে প্ররোচিত করেছে, তার ঠিক নেই। মনে পড়ে, কোনো এক সকালে প্রিয় কারও দূরে কোথাও চলে যাওয়ার কারণে একটি পেটকাটা ঘুড়ি বানানোয় ব্যস্ত হয়ে—পালিয়ে—এক আত্মহত্যাময় ঝিমমারা দীর্ঘ দুপুর যে কোনোভাবে কাটাতে পেরেছিলাম, সে আমার সৌভাগ্য।
আজও আমার কাছে ছেলেবেলা আর কিশোরবেলা মানে সারাদুপুর…নিঃসঙ্গতা…অবিরল পাতার মর্মর…
এহসান হায়দার: কবিতা লেখার শুরুর সময় কেমন ছিল, আপনার কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল তখন?
মোস্তাক আহমাদ দীন: প্রস্তুতি যদি কিছু থেকে থাকে তো, তা অচেতন প্রস্তুতি, যা আগের প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা বলা হয়েছে। আমাদের এলাকার ‘জাগরণী সমাজকল্যাণ সংঘ’ নামের একটি সংঘ আমাদের স্কুলের কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করে এবং কিছু বই ও সংগঠনের মুখপত্র একটি ম্যাগাজিনও উপহার দেয়। সেই ম্যাগাজিনে আমার গ্রামের পরিচিত কারও কারও লেখা দেখে বিস্মিত হই। আমার ধারণা ছিল, যারা কবিতা লেখেন, বইয়ে যাদের কবিতা পড়ি, তারা কোনো এক দূরজগতের মানুষ। তারপর, দশ-এগারো বছর বয়সেই কবিতা লেখার ভূত আমার মাথায় চাপে, পাঠ্যবইয়ের বাইরের বই কোথায় পাওয়া যায় তার খোঁজ করতে থাকি, মনে মনে কবিতালেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকি এবং কবিতার গোপন খাতা ভরতে থাকে। এইসবের বাইরে কবিতালেখার জন্য কোনো বিশেষ প্রস্তুতি আগে যেমন ছিল না, এখনো নেই। বই-মানুষ-প্রকৃতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর এই আমি। ঘটমান বা চলমান দৃশ্য, চিত্র ও ঘটনাবলি যখন তাড়িত করে, তখন তা আদি স্মৃতি ও শ্রুতির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে সেই সৃষ্টিক্ষণের মুখোমুখি করে। এ এক অনির্বচনীয় আনন্দমুহূর্ত। নিঃসকোচ বলতে চাই, আনন্দ না পেলে, কষ্ট করে লেখা তো দূরের কথা, পড়তেও পারি না আমি।
কবিতা তো দূরের কথা, আমার যা সামান্য গদ্যচেষ্টা, তাও পূর্বের, দীর্ঘদিনব্যাপী আনন্দপাঠ ও প্রতিক্রিয়ার ফল—বলতে পারেন তা-ই আমার অচেতন প্রস্তুতি।
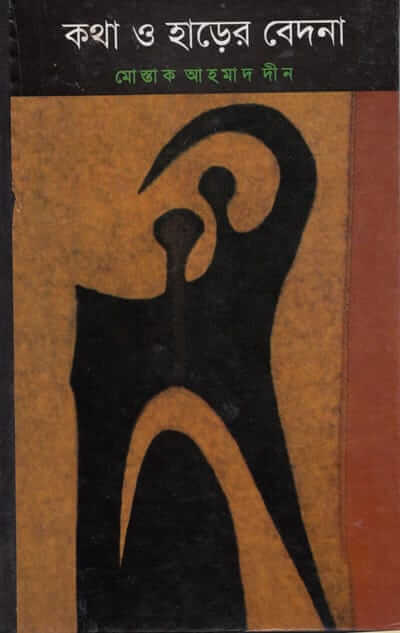
এহসান হায়দার: কবিতা লেখা আপনার কাছে কি তবে সচেতন প্রয়াস? অনেক কবি বলেন, কবিতা আমি লিখি না, কেউ আমাকে দিয়ে লেখায়—আপনার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কী বলবেন?
মোস্তাক আহমাদ দীন: এর উত্তরও অনেকটা আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। আপনি নিজেও কবিতা লেখেন, তাই আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয় যে, আজ বা সর্বশেষ যে-কবিতাটি আপনি লিখেছেন তা যেমন নিকটসময়ের ক্রিয়া, সেইসঙ্গে, তা, পূর্বাভিজ্ঞতার অনিবার্য ছায়াপাতও বটে। যারা বলেন, অভিজ্ঞতা ছাড়াই তাকে দিয়ে কেউ কোনো কিছু লিখিয়ে নেয়, তারা তাদের নিজেদের মনোজগৎ, ভাবজগৎ ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণেই বলেন। গতশতকের আশির দশকের প্রয়াত কবি কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার তাঁর অভিজ্ঞতার কথা—অলৌকিক ও অশরীর কারও কাছ থেকে শোনা নানারকম স্বরের কথা আমাদেরকে বলতেন, কিন্তু আমরা জানতাম—নিজেও জানতেন—তিনি তখন সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত, আর এ কথা কে না জানে যে যে-কোনো নির্ণীত রোগই ব্যাখ্যাযোগ্য। আমি নিজেও কয়েকবার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে কবিতার পঙ্ক্তি পেয়েছি, মনে পড়ে, একবার নিখুঁত মাত্রাবৃত্তও পেয়েছি—কিন্তু আমি জানি তা আমার তখনকার আবিষ্টতা বা পূর্বভাবনারই প্রতিক্রিয়া, অব্যাখ্যেয় কোনো ব্যাপার সেখানে ছিল না।
তবে একথা অস্বীকার করব না যে, যে-কোনো সময় যে-কোনো বিষয় নিয়ে ফরমায়েশি লেখা লিখতে আমি অভ্যস্ত না, তাই অস্বস্তি হয়। জীবনে দু-একবার বন্ধুবান্ধবদের চাপে তাৎক্ষণিকভাবে এই কাজ করতে হয়েছে বটে, সেগুলোকে আমি অভ্যস্তের বাক্যরচনা বা চিত্রকল্প-নির্মাণচেষ্টাই বলব, কবিতা নয়। শুনেছি এবং পড়েছিও, কেউ কেউ এভাবেই অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন (তাও হয়ত আদিভাবনার অচেতন ক্রিয়া), কিন্তু এমন কাজে আমার ভরসা কম, আমি নিরন্তর-প্রবাহ ও তার প্রতিক্রিয়ায় আস্থাশীল।
এহসান হায়দার: কবিতায় কল্পনার দরকার বলে মনে করেন?
মোস্তাক আহমাদ দীন: কল্পনা ছাড়া কবিতা কেন, কোনোকিছুই হয় না; কেউ বাস্তবকে কল্পনায় সাজান, কেউ সেই বোধকে কল্পনার আকারে বাস্তবে বিন্যস্ত করেন যা সুদূর-অদূর অতীত অভিজ্ঞানেরই শীলিত রূপান্তর। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, তাঁর বন্ধু সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলতেন, ‘তুই একদমই বানাতে জানিস না। তোর কোন ইমাজিনেশন নেই।’ শ্যামল সরাসরি তার কোনো উত্তর দেননি, তবে পরে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, ‘কোথায় বানাই—কোথায় আসলের সঙ্গে মিশেল দিই, তা বাইরের লোক কী করে বুঝবে’। আমরা আরেকটু এগিয়ে বলতে পারি, নিজের জীবনের বিষয়আশয় নিয়ে শ্যামলের এত যে অব্যাহত নিরীক্ষা, তা তাঁর কল্পনারই বাস্তবায়ন এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলনও স্বভাবী ও মুগ্ধকর। রুশদির ‘ইমাজিনারি হোমল্যান্ডস’ লেখাটি যেদিন পড়লাম, সেদিনই বুঝেছি তাঁর একাধিক লেখার বীজ এই স্মৃতিগদ্য। কোনো কবিই নিরেট বাস্তবে অবস্থান করেন না, থাকতে পারেন না, কথাটি অধিক বিমূর্ত না লাগলে হয়ত বলতাম, কবি কতগুলো প্রতীকের মধ্যেই বসবাস করেন, তা না বলে বলছি, কবি কল্পনায়—হয়ত অতীতে, নয়ত ভবিষ্যতে—বেঁচে থাকেন, তার জীবনে বর্তমান বলে কিছু নেই।
এহসান হায়দার: একালে এসে কবিতার মাধ্যমে সমাজ-বদল বা এ রকম কিছু সম্ভব?
মোস্তাক আহমাদ দীন: কবিতা কোনোকালেই সমাজবদলে সরাসরি কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি, আর একালে তো পরিপ্রেক্ষিত আরও ভিন্ন। তবে কবিতা সমাজ-মানুষের মনে যে-অন্তঃশীল প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, তা লক্ষগোচর নয় বলে তার প্রভাবটাও গোপন থেকে যায়। পৃথিবীর সেরা কবিতাগুলোর পাঠকেরা এমনই এক ঐকসূত্রে গাঁথা যাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হয় না ঠিক, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে এক অদৃশ্য আলাপ চলে। এক বাউল মানুষের আত্মিক সম্পর্ক বিষয়ে বলতে গিয়ে এই আলাপকে ‘মনগপ’ বলে সম্বোধন করেছিলেন, আমার ভালো লেগেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কোনো কবি বা নিবিড় কবিতাপাঠক যখন দূরদেশ ভ্রমণ করেন, তখন, হঠাৎই কোনো এক সমপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আসলে পৃথিবীজুড়ে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর অদৃশ্য পাঠ চলছে, এবং তার প্রভাবও ক্রিয়াশীল।
এর বাইরে কিছু কবিতা আছে যেগুলো বিভিন্ন গণ-আন্দোলন বা গণ-জোয়ার সৃষ্টিতে সরাসরি ভূমিকা না রাখলেও উদ্দীপনার কাজ করে। তাই কবিতা, তা অন্তঃশীল ভাবের হোক বা উদ্দীপক, সমাজে তার প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান না হলেও গুরুত্বপূর্ণ।
এহসান হায়দার: গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে আপনি যখন লিখতে শুরু করলেন, বাংলা সাহিত্যের একপাশে সে সময় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, তিরিশের আধুনিক কবি জীবনানন্দ, আহসান হাবীব-ফররুখ আহমদ, ষাট দশকের উৎপল-বিনয়-শক্তি, শামসুর রাহমান-আল মাহমুদ-শহীদ কাদরীর মতো অসংখ্য গুণী কবি এসেছেন—এঁদের দুই জগৎ, দুই ভাষা। এই দুই জগৎ ও ভাষার বিপরীতে নিজের কাব্যভাষা তৈরির ক্ষেত্রে আপনার বিবেচনাগুলো কেমন ছিল?
মোস্তাক আহমাদ দীন: লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে যেসকল লেখকের যাত্রা শুরু, তাদের মধ্যে প্রথম থেকেই, নাহলে কিছু দিন পর থেকেই, এই বোধ তৈরি হয় যে, আমাকে অন্যদের মতো লিখলে চলবে না, নিজের মতো করে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে আমি আমার বোধের/মনের জগতের সঙ্গে নিজের অঞ্চলের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ ও জীবনপ্রবাহকে যুক্ত করে নিজের ব্যথিত স্বরকে খোঁজার চেষ্টা করেছি, কারণ, আমাদের ইতিহাস শুধু অর্জনের নয়, হারানোরও, এবং অপহরণেরও বটে; কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে একথাও জানিয়ে রাখি, আমার সৃষ্টিক্ষেত্রে আমি প্রবলভাবে স্মৃতিময় বটে, কিন্তু কোনোভাবেই অতিকাতর নই, বৃহত্তর সমাজের কথা মনে রেখে আমার দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত…
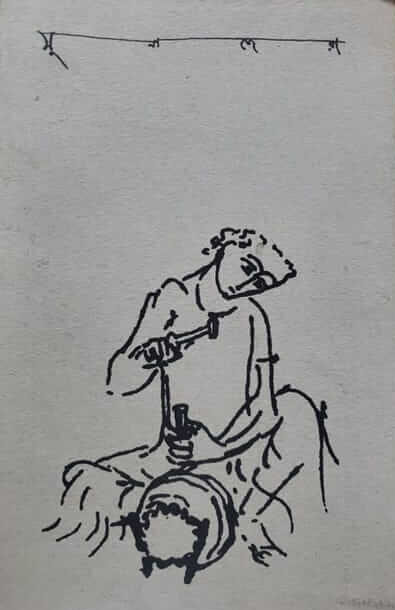
এহসান হায়দার: আপনার কবিতায় প্রেম-দ্রোহ অত্যন্ত সহজ-সাবলীলভাবে উঠে এসেছে, যা আমাদের চমৎকৃত করে, এ বিষয়ে কিছু বলবেন?
মোস্তাক আহমাদ দীন: আমার কবিতা বিষয়ে আপনি যা বললেন, সে-বিষয়ে আমার কী বলবার আছে জানি না, শুধু এটুকুই বলব, প্রেম-দ্রোহ কেন, যেকোনো বিষয়কে নিজের-মতো-করে সাবলীল প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করবার জন্যই একজন লেখক অবিরাম চিন্তা করেন, আর যেহেতু শিল্পলোকে শ্রেষ্ঠত্বের/পূর্ণতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, তাই আজীবন এই চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়।
এহসান হায়দার: গদ্য পড়েন, কোন ধরনের গদ্য ভালোবাসেন?
মোস্তাক আহমাদ দীন: সময়ে সময়ে বহুধরনের গদ্য পড়তে হয়, ভালো লাগে, তবে আত্মজৈবনিক গদ্য পড়তেই বেশি আগ্রহী। অনেকে আত্মজীবনীতে নিরেট সত্য খোঁজার চেষ্টা করেন এবং তা না পেয়ে হতাশ হন, সমালোচনা করেন, কিন্তু তারা বোঝেন না যে বইটি একটি ভাষায় প্রণীত হচ্ছে আর লেখকও অনেক সময় সেই ভাষার নিজস্ব অভিব্যক্তির কাছে অসহায়। তাই বইটি সুলিখিত হলে, তা থেকে যা পাওয়ার কথা, তা ঠিকই উদ্ধার করা যায়।
এহসান হায়দার: ক্রিয়েটিভ গদ্য উপভোগ করেন কীভাবে?
মোস্তাক আহমাদ দীন: কখনো কবিতা, কখনো গান হিসেবে।
এহসান হায়দার: প্রকৃতার্থে বাঙালিয়ানার যে প্রকাশ, হোক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ কিংবা উপন্যাস—কেমন হতে পারে তা…
মোস্তাক আহমাদ দীন: আমাদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ যে-বাংলার উত্তরাধিকার ধারণ করবার কথা, সেই বাংলা আমাদের লোকায়ত বাংলা; কারণ, ইতিহাস বলে, আমাদের দেশে নগরায়নের পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছিল ওই বাংলারই সম্প্রসারণ, যা এতদিনে প্রায় হারানো-বাংলায় পরিণত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার এবং ঔপনিবেশিক প্রভাব ও তৎপরতার পরও যা এখনো বর্তমান, তাতেও অসাম্প্রদায়িক ও নির্ভেদ সমাজ প্রতিষ্ঠার উপাদান আছে যা সৃষ্টিশীল কাজের উৎস ও প্রেরণা হতে পারে। তবে, এখনকার সৃষ্টিশীল ও মননশীল রচনার যারা সম্ভাব্য পাঠক, তাদের মনোজগতের দিকেও সবিশেষ খেয়াল রাখা জরুরি। এদের অনেকেই নিজেকে বিশ্বনাগরিক মনে করে, জন্মভূমি ও মাতৃভূমির ধারণা তাদেরকে তাড়িত করে না, আমাদের যে-নাড়িগত সংস্কার, জাতিগত উপলব্ধি, তা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তারা এমন এক জগতের বাসিন্দা—আমাদের কাছে এখনো যা অপেক্ষাকৃত অলীক—তাদের কাছে তা-ই বাস্তব। এখনকার লেখকদেরকে এই প্রজন্মের চরিত্র ব্যাখ্যা করে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।
এহসান হায়দার: কবিতায় বিভাজন করেন কি?
মোস্তাক আহমাদ দীন: পেশাগত কারণে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদেরকে প্রতিদিনই এ কাজ করতে হয়, ছন্দদক্ষ কবির কবিতা আলোচনা করতে গেলেও এ-কাজ না করে উপায় নেই, কিন্তু এর বাইরে আমি যখন মুক্ত পাঠক, তখন আর তা করতে হৃদয়-মন সায় দেয় না। আপনার মনে পড়বে হয়ত, কমলকুমার দত্ত সম্পাদিত দাহপত্র পত্রিকায় একসময় কথাসাহিত্যিকদের লেখা তুলে দিয়ে বলা হতো, এটাও কবিতা;, মনে পড়ে তাঁরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখাও তুলে দিয়েছিলেন, আমাদের কাছে তখন সেগুলো কবিতাই মনে হয়েছিল। মণীন্দ্র গুপ্তের অক্ষয় মালবেরি ছাড়াও আরও বহু গদ্যের অংশবিশেষ কবিতা বলেই মনে হয়, বরং তার কিছু কবিতাকেই মনে হয় গদ্য। ইতালো কালভিনো আর কমলকুমার মজুমদারের গল্প-প্রবন্ধ বহু জায়গায় তো সেই ‘কবিতা’ই। কবিতার কাগজ কৃত্তিবাস-এ কেন ছাপা হয়েছিল কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস? এছাড়া, প্রাচীন ভারতে কবির সংজ্ঞা তো আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এত আদিতেই-বা যাচ্ছি কেন, আমার গ্রামের পল্লিচিকিৎসক মতিলাল ডাক্তারকে আমি একসময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা পড়িয়েছিলাম, তিনি পড়ার কয়েক দিন পরে আমাকে বললেন, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো কবি।’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতা পড়ে তিনি একথা বলেননি, বলেছিলেন এই উপন্যাস পড়েই। তার অনেকদিন পরে আমি যখন দিবারাত্রির কাব্য পড়লাম, তখন ভাবলাম, এটি পড়লে মতিলাল বাবু নিশ্চয়ই তাকে মহাকবিতা বলতেন। সৈয়দ শামসুল হক লিখেছিলেন, ‘ঔপন্যাসিক দু’ধরনের হন, কবি অথবা উন্নতমানের সাংবাদিক।’
তাই মনে হয়, বিভাজনের দিন শেষ হয়ে এসেছে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বহু আগেই তাঁর একাধিক উচ্চাশী গদ্যে একথা বলেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আমিও যে এই কথাটা বললাম, আগামীকাল ক্লাসে হাজির হয়ে তো কায়দাকানুন দেখিয়ে সেই বিভাজনটাকেই দেখাতে হবে।
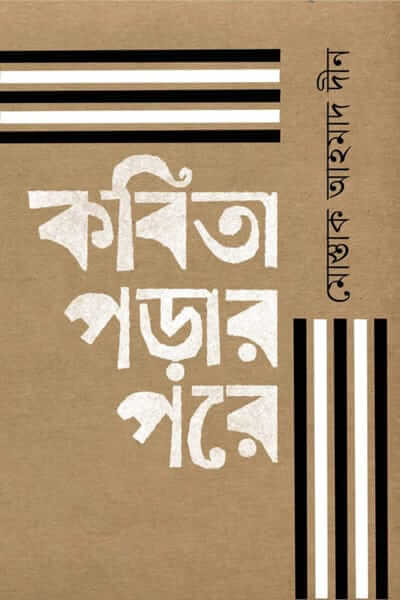
এহসান হায়দার: আপনি ফোক রচনা ও গবেষণায় বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন বলে মনে হয়, যেমন ধরুন বাউল গান, বাউলদের জীবনাচরণ, এ বিষয়ে বলবেন?
মোস্তাক আহমাদ দীন: ফোকলোর বিষয়ে আমার আগ্রহকে আহত মানুষের অস্থির অনুসন্ধান বলতে পারেন, পরে অস্থিরতা কমেছে কিছু রত্ন-মাণিক আর যাকে বলে মানুষরতন, তারও সন্ধান মিলেছে। এই কথার মধ্যেই আমার আত্মভ্রমণের স্মুতি-অভিজ্ঞতা মিশে আছে। বিদ্যায়তনের শিক্ষা এবং শিক্ষিতজনের লেখা বইপত্রের শিক্ষা যে-ধাক্কাটা দিতে পারেনি, একদিন এক ঝান্ডাধারী ধার্মিকের কথায় আমার গ্রামের এক তিক্ত-বিরক্ত দীর্ঘকেশ রিকশাচালকের একটি বাক্য আমাকে সেরকম একটা ধাক্কা দিল এবং চেতনায় ঝড় তুলল। এই লোক বারোমাসই রিকশা চালান, সময়ে সময়ে বাউল-ফকির-দরবেশদের সঙ্গ করেন। অথচ এইসব মুখের কথা আর লেবাস নিয়ে আরেক ফকিরের গান আছে: ‘মুখের কথায় হয় না ফকিরালি রে লাম্বা চুলী/ মুখের কথায় হয় না ফকিরালি।’ আমরা সচরাচর কবিতায় যা লিখতে পারি না বা বলতে পারি না বাউল-ফকিরেরা অনায়াসে তা লিখতে পারেন এবং কখনো নিজের গোত্রকেও ভয়ানক আক্রমণও করে বসতে পারেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, বাউল-গানের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে কবিতালেখা শুরু করার একদশকর পর। আগ্রহ তৈরি হওয়ার পর মাঝে মাঝে মায়ের কাছে ফিরেছি, মায়ের কাছের মানুষদের কাছে ফিরে গেছি, যারা দিনের বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছে আসত। তিনি একা একা নিভৃতে গাইতেন সৈয়দ শাহনূর, দীন ভবানন্দ আর রাধারমণ দত্তের গান। গাঁয়ের বিভিন্ন আসর থেকে টেপরেকর্ডারে তোলা শাহ আবদুল করিম, মুজিব সরকার, তরুণ বয়সের ক্বারী আমির উদ্দীনের গান শুনতেন ফুফাতো ভাই গুলাম আলি, কাছে বসে আমিও শুনতাম—শৈশবের সেইসব স্মৃতির কাছেও ফিরে গেছি পরে।
উপরের মুখপদটি এক গায়কের কণ্ঠে শোনা আরেক মহাজনের গান, যা শোনার পর আর কখনো ভুলিনি। কয়েক বছর আগে খুঁজে পাই শেখ মদন বাউলের সেই মর্মান্তিক গানটি: ‘ও তোর পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে/ ও তোর পথ ঢাক্যাছে গুরুতে মুরশিদে।’ এখানে ‘তোর’ স্রষ্টারই সর্বনাম, কিন্তু তাকে পাওয়ার পথের বাধা হলো উপাসনালয় এবং গুরু ও মুর্শিদ—এমন বাউল-তত্ত্ববিরোধী বাউল গান আমি আর কোথাও খুঁজে পাইনি। এই গানটি আমাকে লালনপূর্ব এই বাউলকে নিয়ে কাজ করতে বাধ্য করে। এইসব গান এবং গানের পদর্কতাদের জানার চেষ্টা করে তাদেরকে নিয়ে যথাসাধ্য লেখার চেষ্টা করেছি। আমার এইসব লেখার একটি লক্ষ্য গান ও গানের মানুষের অনুসন্ধান, যখন লেখা শুরু করি, তার শিরোনাম দেই ‘অমুক ও তাঁর গান’, পারতপক্ষে নাম বদলাই না, যদি লেখা কখনো লক্ষ্যকে ছাপিয়ে উঠতে চায়, তখনই বদলাই, বদলাতে বাধ্য হই। এভাবে লেখার বা জানার চেষ্টার কারণ হলো, পদকর্তা ও তাদের গান আলাদা কিছু নয়। এমনিতে দীর্ঘদিন বাউল-গান শুনলে বা পড়লে তাতে বিষয় ও শৈলীর দিক থেকে খুব বেশি ভিন্নতা খুঁজে পাওয়া যায় না, সুরের বৈবিত্র্যও কম, কিন্তু সেগুলো পদকর্তার মুখে বা তাঁর জীবনভাবনা বা সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে শুনলে ও পড়লে একেকটি চরণ কখনো কখনো আলো হয়ে আসে, অপরিচিত লাগে এবং বিস্ময় জাগায়।
এহসান হায়দার: আপনার রচনা বিষয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, একদিকে কবিতা অন্যদিকে প্রবন্ধ এবং বিশ্লেষণাত্মক রচনা, কেমন উপভোগ করেন গদ্য?
মোস্তাক আহমাদ দীন: উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতা ও সংগীতের মতোই আনন্দ দেয়, শিহরিত করে। কবিতাকে সৃষ্টিশীল ও বোধের কাজ বলে যারা গদ্যের চেয়ে কবিতাকে আলাদা মহিমা দিতে চান, তারা কেন তা করেন জানি না, আমি সেই গোত্রের নই, কারণ দুটি মাধ্যমের ভাব ও অভিব্যক্তি আলাদা। বিভাজন করলে করা যায়, না করলেও অসুবিধা নেই, বিষয়ই নির্ধারণ করে দেয় কী লিখব এবং কোন পথে এগোব। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি নানারকম গদ্য লিখি, লিখে আনন্দ পাই বলেই লিখি।
এহসান হায়দার: কবিতায় মৌলিকতা বিষয়টিকে বাংলা কবিতায় কীভাবে দেখেন?
মোস্তাক আহমাদ দীন: তিরিশের দশকের কবিদের ওপর যখন ইউরোপীয় প্রভাবের কথা বলা হচ্ছিল, আলোচনা হচ্ছিল, তখন তার একমাত্র না হলেও প্রধান মানদণ্ড ছিল রবীন্দ্রনাথ; এরপর, জানলাম রবীন্দ্রনাথও নাকি বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় কবিতা লিখেছেন! কয়েক দিন আগে জ্যোতির্ময় দত্তের একটি সাক্ষাৎকার দেখলাম, তিনি বলছেন, টি.এস.এলিয়ট তাঁর খুব পছন্দ নয়, তার কারণ তার লেখায় প্রচুর পরিমাণে পূর্ববর্তী মহাজনদের উল্লিখন, ফলে তাঁর প্রিয় কবি ইয়েটস। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সাক্ষাৎকারটি যখন শেষ হচ্ছে তখন জ্যোতির্ময় দত্ত তাঁর স্মৃতি থেকে সেই এলিয়টই আবৃত্তি করলেন আর নিজে নিজেই বললেন, দেখলেন তো, এলিয়ট পছন্দ করি না বটে, কিন্তু তাকেই আবৃত্তি করতে হলো! এইসব কথার অর্থ এই নয় যে, কবিতায় মৌলিকতা/নিজস্বতা বলতে কিছু নেই, বরং ‘মৌলিকতা’র বা নিজস্বতা বা নিজস্ব মুদ্রা সকলের মধ্যেই থাকে, কিন্তু সকলের পক্ষে সেই মুদ্রা খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না। এই আলাপের একাধিক উত্তরে বারবার স্মৃতির উপর জোর দিয়েছি আমি, কিন্তু একজন লেখককে লেখার সময় পূর্ববর্তী লেখকদের স্মৃতি ও মুদ্রা ভুলে গিয়ে/অতিক্রম করে নিজের আপন মুদ্রাকে খুঁজে নিতে হয়। তা নিঃন্দেহে জটিল এবং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। জীবনানন্দ দাশ দেশ-বিদেশের বহু কবির কবিতা/মুদ্রা মন্থন করেও নিজের মুদ্রা যে খুঁজে পেয়েছিলেন, তা আমাদের ভরসার ইতিহাস।
এহসান হায়দার: বাংলাদেশের কবিতায় সুফিতত্ত্ব কিংবা এর প্রভাব লক্ষ করেছেন, গত কয়েক দশকে সুফি ধারণাকে যারা আঁকড়ে চর্চায় যুক্ত হয়েছিলেন, শেষাবধি কি তা সুফিতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত [মেলানো যায়]?
মোস্তাক আহমাদ দীন: বাংলাদেশের কবিতায় সুফিতত্ত্বের নিবিড় প্রভাব আমি লক্ষ করিনি কখনো, বিচ্ছিন্নভাবে দেখেছি। আশি আর নব্বইয়ের দশকের কয়েকজনের কবিতায় মাঝে মাঝে কিছু প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ এসছে। খোন্দকার আশরাফ হোসেন, মোহাম্মদ সাদিক এবং সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কবিতায় প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে, শোয়েব শাদাব ও কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ারের কিছু কবিতায় এসেছে, এর বাইরে এই মুহূর্তে আমার আর কিছু মনে পড়ছে না। এখানে কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ারের দু-একটা কবিতার উল্লেখ করা যেত, যেগুলো পড়লে বু আলি কলন্দর আর খাজা মঈন উদ্দিন চিশতির ‘দেওয়ান’-এর কথা মনে পড়বে, কিন্তু ইচ্ছে করেই তার উল্লেখ করলাম না। কারণ আমরা এখন চুলের জটিলতা খোলার চেষ্টা না করে তা কেটে ফেলতে আগ্রহী। সময় হোক, আরও কথা হবে, অনেক কিছু না-বলেই আপনার কথার উত্তরগুলো দিচ্ছি, আমি এখন কথা না-বলার পক্ষে।
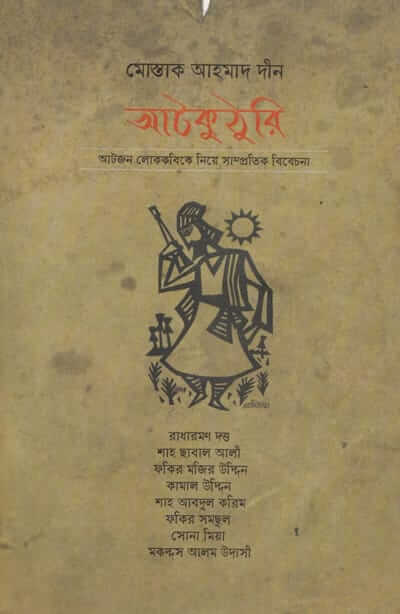
এহসান হায়দার: নির্মোহ পাঠের বেলায় কাদের কবিতায় আপনি স্বস্তি পান?
মোস্তাক আহমাদ দীন: এই প্রশ্নটি আমার জন্য একারণেই খুবই বিব্রতকর হয়ে গেল যে, বেশ কিছুদিন ধরে কবিতা পড়ে কোনো স্বস্তি পাচ্ছি না, আনন্দ পাচ্ছি না। বেশিরভাগই কবিতা পড়া শুরু করলে তার শেষটাও দেখা যায়, এটি আমার জন্য ভালো না মন্দ তা জানি না, কিন্তু এটুকু জানি, কবিতার ক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশা বেড়ে যাওয়া বিপজ্জনক। এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে আত্মজৈবনিক গদ্য, চিঠিপত্র, জার্নাল এবং ধ্রুপদি সাহিত্যে ডুব দিয়েছি, ফলে আনন্দে আছি, মনে হচ্ছে কবিতাই পড়ছি।
এহসান হায়দার: সিলেট শহর নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ, তবুও তো দেশের রাজধানী থেকে দূরে, সাহিত্যচর্চায় এই প্রান্তিকে থেকেও আপনি নিজের সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে সবখানে দারুণ প্রভাব তৈরি করেছেন; রাজধানীর সাহিত্যরাজনীতি [সিন্ডিকেট/গ্রুপিং] আপনাকে স্পর্শ করে না?
মোস্তাক আহমাদ দীন: লেখার জগতে এসে যতটুকু প্রচার ও প্রসার পেয়েছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট, এর চেয়ে বেশি প্রচার যদি চাইতাম, তাহলে মনে অসন্তোষ তৈরি হত। বরং যে-সামান্য পরিচিতি তৈরি হয়েছে, তার জন্যই তো লেখার চাপ সামলানো কঠিন হচ্ছে, লেখা না দিতে পারায় বহু সম্পর্কে চিড় ধরছে, ফলে ‘রাজধানীর সাহিত্যরাজনীতি [সিন্ডিকেট/গ্রুপিং]-এর কথা মাথায় এলেও তা নিয়ে (মাথা)ব্যথা তৈরি হয়নি কখনো।
এখন আমার মনে হয়, দূরত্বটাই বরং স্বস্তিকর ছিল। দূর থেকে ধারণাগতভাবে বহু কিছুর মোকাবেলা করা সহজ হয়েছে।
এহসান হায়দার: গত শতকের ৯০ দশকে সিলেট বাংলাসাহিত্যের বিকল্প রাজধানী হয়ে উঠেছিল বলে আমরা জানতাম, এ সময়ে বাংলাদেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কবি ও সাহিত্যিকেরা সিলেটে মিলিত হতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এমন কী হয়েছিল সে প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়ে- এ বিষয়ে আপনার বিস্তারিত মতামত জানাবেন কী?
মোস্তাক আহমাদ দীন: আপনাদের এই মূল্যায়নে/বিবেচনায় কত জন একমত হবেন জানি না, তবে একথা ঠিক যে সিলেট থেকে নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে শূন্যের দশকের কয়েক বছর পর্যন্ত যেসকল ছোটোকাগজ বের হতো, সেখানে বাংলাদেশের সেইসময়কার তরুণ লেখকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেক ছোটোকাগজ বের হতো এখান থেকে, একই জেলা থেকে একই সময়ে এত কাগজ যে কীভাবে বের হতো তা নিয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করতেন। বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকেরা লিখতেন বলে সেসব অঞ্চলে কাগজগুলো দ্রুত ছড়িয়েও পড়ত। তবে, সেইসময় আমাদের এখানে সাহিত্যসম্মেলন হতো না, আমরা তার কিছুটা বিরোধী ছিলাম, বা, হয়ত, আমরা লেখাপড়া আর আড্ডায় এতটাই লিপ্ত থাকতাম যে, সাংগঠনিক তৎপরতায় আগ্রহ তৈরি হত না। তবে, লেখকবন্ধুরা ছুটিছাটায় আসতেন নিয়মিত, রাত-দিন একাকার করে আড্ডা দিতাম, ভাব-বিনিময় হতো। পরে কয়েক বছর তা একটু স্তিমিতহয়ে পড়ে, তার কারণ আমরা সবাই জীবন-জীবিকার চাপে ছড়ে-চিতরে পড়ি। তার মানে সেই সময়ে যে অন্যরা কাগজ বের করেননি তা নয়, ভালোভাবে, সমৃদ্ধরূপেই বরং বের হয়েছে কাগজ, তবে তাদের মধ্যে এতটা সংঘবদ্ধতা ছিল না, নিজেদের কাগজ সমৃদ্ধ করার দিকে তাদের মন ছিল, নবীনদের তুলে আনার চেয়ে ভালো লেখকদের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি, এতে কাগজ সমৃদ্ধ হয়েছে, পাঠক আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছে, অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব আর নবীনদের পৃষ্ঠপোষকতা একটু কম হয়েছে, এই যা।
তবে, এখন আবার সিলেট থেকে কয়েকটি কাগজ একসঙ্গে বের হচ্ছে, ভালোও হচ্ছে সেগুলো, সবাই যার যার জায়গা থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন দেখে ভালো লাগছে।
এহসান হায়দার: তরুণদের মধ্যে যারা লিখছেন, এ বিষয়ে কিছু বলবেন?
মোস্তাক আহমাদ দীন: তরুণদের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ লক্ষ করেছি, তার আঁচও গায়ে লেগেছে, এখন দাবানলের অপেক্ষায়। কিন্তু সমস্যা হলো, অধিকাংশ কবির চেতনায় নেই প্রকৃতির সুনিবিড় পাঠ, ক্লাসিক পড়ার অভিজ্ঞতা; ফলে আনন্দ নেই, উল্লাস ও অস্থিরতা আছে। একারণে অনেকেই একটু খ্যাতি পেয়ে তা ভাঙানো শুরু করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছেন।
আগেই বলেছি, এ হলো, অধিকাংশের অবস্থা, এর বাইরে যারা সক্রিয়, তাদের লেখার আমি আগ্রহী পাঠক।

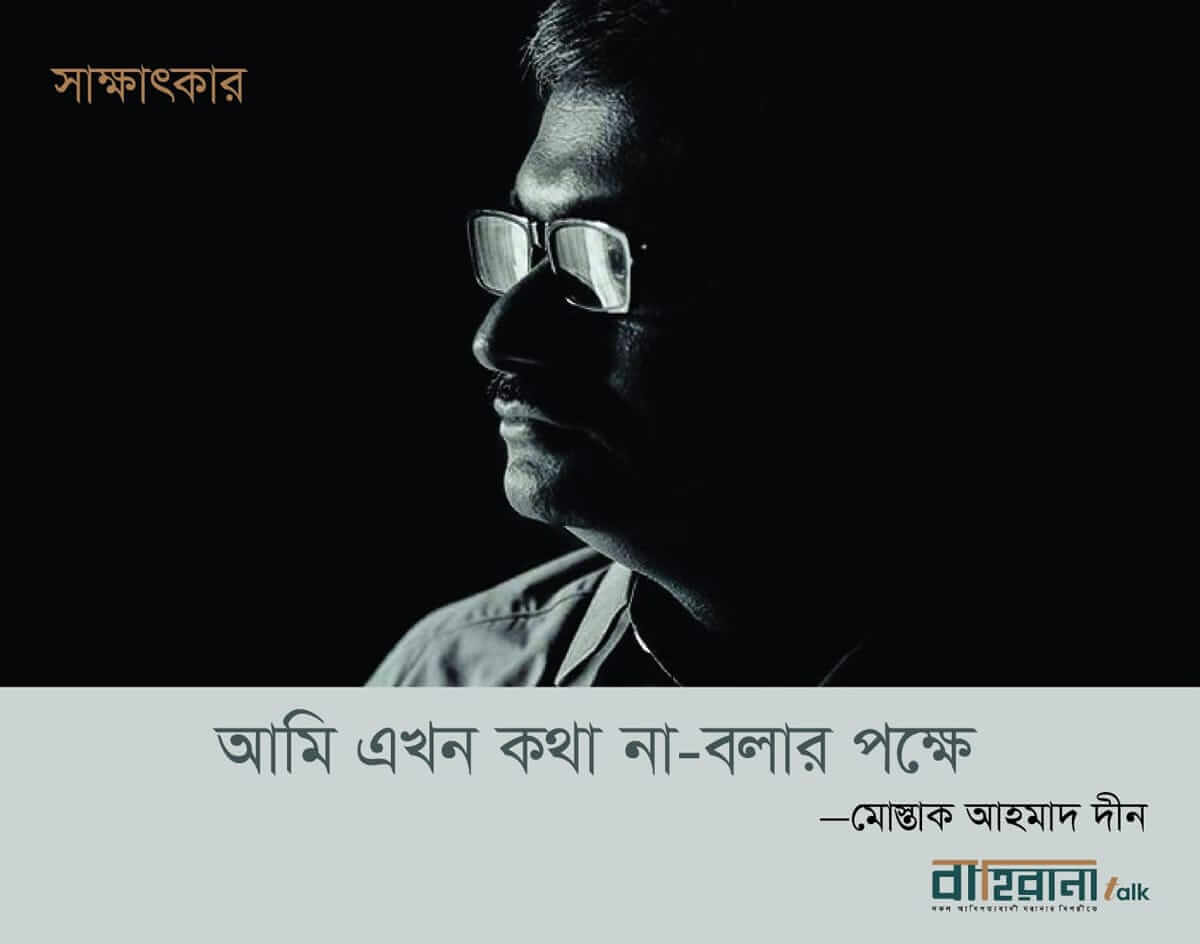
নিবিড়ভাবে পাঠ নিলাম। একজন পছন্দের মানুষ, কবি। সাক্ষাৎকারটি কি আমার মনে ধরেছে!? হ্যাঁ অথবা না, বলতে পারছি না। শিরোনামটি ভালো লেগেছে। দাতা এবং গ্রহিতা উভয়কেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।