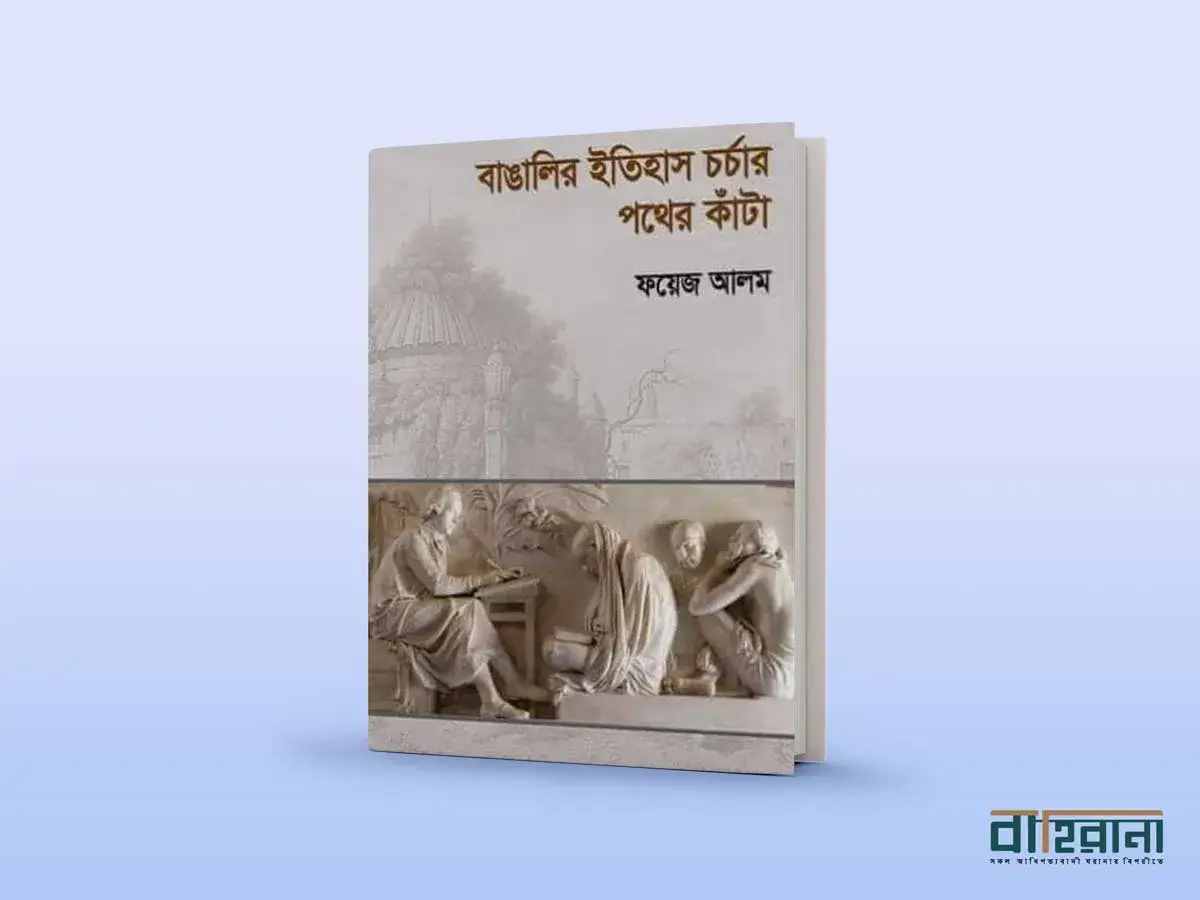আমাদের ইতিহাস নিয়ে নিজের মনে একটা জিজ্ঞাসা ছিলো অনেক দিনের। বাঙালির অতীত ইতিহাস কি স্থির নিস্তরঙ্গ একটি বিদ্যা? যেমনটি বিজ্ঞান বা গণিত? বিজ্ঞানের অতীত আবিষ্কার সুনির্দিষ্ট এবং চিরস্থায়ীভাবে প্রমাণিত। সে নিয়ে আর কথা বলার সুযোগ নেই। কেবল নতুন আবিষ্কার বা সূত্র নিয়ে কথা বলা যায়। নতুন আবিষ্কার এলেও পুরানা জ্ঞানের ভিত্তিতেই তা রচিত হয়। কাজেই বিজ্ঞান বা গণিতের অর্জিত জ্ঞান স্থির। সেই স্থির জ্ঞানের উপর দাঁড়িয়েই সামনের দিকে এগোনের চেষ্টা।
বাঙালির অতীত ইতিহাসও কি তেমনই কোনো বিদ্যা? অতীত বলতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের কথাই বলছি। নিজের মনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়ার কারণ হলো বহুযুগ ধরে আমরা হুবুহু একই ইতিহাস পড়ে আসছি। একটি দাড়িকমারও যেন হেরফের নেই। সেই কতকাল আগে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার যা বলে গেছেন তা-ই আমাদের ইতিহাস।
সাধারণত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আর পুরোনো দলিলদস্তাবেজ ও বইপুস্তকের বিবরণ নিয়ে ইতিহাস রচিত হয়। বিবরণগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এভাবে সব মিলিয়ে লিখিত হয় ইতিহাস। গত কয়েকযুগে বাংলাদেশে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক জায়গা আবিষ্কৃত হয়েছে। নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বর, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, গাজীপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে নানা ধরনের তৈজসপত্র, ঘরবাড়ি ও শহর-নগরের চিহ্ন। প্রত্নতত্ত্বের গবেষকরা বলছেন এগুলোর কোনো কোনোটা দুই হাজার বছরের চেয়ে বেশি প্রাচীন।
ইতিহাসে এসব আবিষ্কারের উল্লেখ করা হয় মাত্র। কিন্তু এগুলোর ফলে আমাদের অতীতকালের বিবরণ পরিবর্তিত হওয়ার কথা, নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত হওয়ার কথা। সেটি কিন্তু হচ্ছে না। সেই সত্তর-আশি বছরের পুরোনো বিবরণই আমরা পড়ছি। এজন্যই প্রশ্নটা জেগেছে মনে। আমাদের ইতিহাস কি স্থির ঐশ্বরিক জ্ঞানের এক বিদ্যা। যতই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হোক, যতই ভিন্ন সভ্যতার ইঙ্গিত পাওয়া যাক আমাদের ইতিাসের বক্তব্য যেন আর কখনো বদলাবে না! যা লেখা হয়েছে তা নিয়ে যেন আর কখনো প্রশ্ন তোলা যাবে না! অথচ বিভিন্ন জাতির প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে নিয়মিত যোগ বিয়োগ হচ্ছে। কারণ প্রায়ই আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু। তবু আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস এক জায়গাতেই স্থির।
বাঙালির ইতিহাসের এইরূপ অমোঘ সত্য সেজে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার দিকটা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছেন ফয়েজ আলম তার বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা বইয়ে। তিনি বলছেন বাঙালির ইতিহাসের বেশ কিছু বিষয় ইতিহাসের সত্য বিবরণ হিসাবে দাড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে সেগুলো সবার নিকট গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত সত্য নয়। কোনো কোনোটা অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মাত্র। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকরা এ হেন অনুমান নির্ভর বিবরণ সম্পর্কেও প্রশ্ন করেননি। দুএকজন ব্যতিক্রম বাদ দিলে বলতে হয় আমাদের ঐতিহাসিকরা আগের লেখা ইতিহাসেরই চর্বিত চর্বন করেছেন মাত্র। কোনো বিষয়ে প্রশ্ন তুলেননি, সন্দেহ করেননি, পাল্টা যুক্তি দেননি।
ফয়েজ আলমের অভিযোগ, “বাংলা আর বাঙালির ইতিহাস উনিশ শতকের ধর্মীয় উন্মাদনার ময়লা-আবর্জনায় ভরা। যুগে যুগে আমাদের বহু নির্বোধ লেখক-বুদ্ধিজীবী-ইতিহাসকার ইতিহাস চর্চার নামে সেই ময়লা-আবর্জনা মিশানো ইতিহাসরেই আবার নিজ নিজ ভাষায় নতুন কইরা লেখছেন মাত্র। এইভাবে দিন দিন আরো বেশি ময়লাছয়লার নিচে চাপা পড়ছে ইতিহাসের আসল সত্য।” (বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা, পৃষ্ঠা ১২)
উনিশ শতকের কলিকাতায় ইংরেজদের মোসাহেবী করে প্রচুর অর্থবিত্ত অর্জন করেছিলো একদল সংখ্যালঘূ ব্রাহ্মণবাদী মানুষ। কাঁচা অর্থ, সম্পদ ও ক্ষমতার ভাগপাওয়া এ শ্রেণিটি কলিকাতার বাঙালি সমাজের মাথা হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বশত এরা নিজেদের আর্য পরিচয় ও আর্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়ে দেখতে পায় প্রাচীন বাংলায় আর্যদের গৌরবের ইতিহাস নেই, কোনো তথ্যপ্রমাণও নেই। তখনই তারা পুরাণ লোকসাহিত্য ইত্যাদি অবলম্বনে বাংলায় আর্য গৌরবের বানোয়াট ইতিহাস উপস্থিত করে।
এখানেই ফয়েজ আলমের বইটির বিশেষত্ব। তিনি আমাদের মধ্য ও প্রাচীন যুগের ইতিহাসের নিস্তরঙ্গ জলভাগে তীব্র আলোড়ন হওয়ার মত কথা তুলেছেন। বলতে চেয়েছেন আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে বেশ কিছু বিবরণ অনুমান-নির্ভর, তথ্য-প্রমাণবিহীন। এর কোনো কোনোটা আবার বাঙালির ইতিহাসের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ফলে অনুমান নির্ভর ভিত্তির উপর রচিত যে ইতিহাস তাতেও রয়ে গেছে অনেক ফাঁকফোকর আর গোজামিল।
সন্দেহ নেই লেখকের অভিযোগ মারাত্মক। কিন্তু তার অভিযোগ বাঙালির ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে জরুরি কোনো বিষয় সামনে নিয়ে এসেছে কি না সেটি জানা দরকার। বোঝা দরকার সেই অভিযোগের নিজের ভিত্তিটাই কতটা শক্ত বা নড়বড়ে।
লেখক প্রথমেই বলে নিয়েছেন যে, ইতিহাস রচনা তার লক্ষ্য নয়। তিনি বলছেন বাঙালির প্রচলিত ইতিহাসে কিছু আনুমানিক বা ভুল বিবরণকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব বিবরণের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে ইতিহাসের নানা অধ্যায়। ফলে আমাদের গোটা ইতিহাসই নানান ভুলে আক্রান্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি তিনটি বড় বড় বিষয় সামনে নিয়ে এসেছেন। এগুলো হলো বাংলায় আর্য সভ্যতার বিস্তার, বাঙালির আদিপরিচয় এবং বাঙালির ইতিহাসের পুরাণ-নির্ভরতা।
ইতিহাসের প্রচলিত বইগুলোতে দেখা যায় বাংলাদেশে সেই প্রাচীন কালেই আর্য সভ্যতার বিস্তার হয়েছিলো বলে দাবী করা হয়। প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় হিন্দু ধর্মীয় পুরানের তথ্য। পুরান ইতিহাস। পুরাণ রচিত হয়েছে বিভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের হাতে। ভারতীয় পুরানগুলিতে অঞ্চলভেদেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন রামায়নের উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় কাহিনীগুলোর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সবচেয়ে বড় কথা পুরানের বিবরণগুলো নির্দিষ্ট কাল নির্নয় করা যায় না। এসব কাহিনীর সবই যে কল্পনা তাও হয়ত নয়। হয়ত কোনো কোনো ঘটনা প্রাচীন ভারতের কোনো রাজ্যে সত্যিই ঘটে থাকবে। কিন্তু তার কাল আমাদের জানা নেই। পুরাণও এ বিষয়ে চুপ। তাই এগুলোকে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে আনা উচিত না। আবার আনা যেতেও পারে যদি অন্য কোনো সূত্র থেকে তার ঐতিহাসিকতা ও সময় সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।
ফয়েজ আলম বলছেন প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে আর্যদের বসতি স্থাপন এবং তাদের সভ্যতার বিস্তারের বাস্তব তথ্যভিত্তিক প্রমাণ নেই। এক মাত্র পুরাণের কথা দিয়ে সেগুলো প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। অতঃপর সেগুলোকেই ইতিহাসের সত্য হিসাবে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। তথ্যপ্রমাণহীন এইসব দাবীর নমুনা তিনি তুলে ধরেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের গ্রন্থ থেকে। যেমন ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস-এ দাবী করেছেন: “ইহা এক প্রকার অবধারিত হইয়াছে যে অতি পূর্ব্বকালে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতিই এ দেশে বাস করিত। পরে ‘আর্য’ নামধারী হিন্দুরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এ দেশ দখল করেন। পরাজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ জঙ্গলে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কেহ কেহ বিজেতাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। এতদ্দেশীয় বর্তমান অসভ্য জাতিগণ এবং নিম্নশ্রেণির হিন্দুগণ তাহাদিগেরই সন্তান সন্তুতি”। কিভাবে তা অবধারিত হলো সে প্রমাণ কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবু উল্লেখ করেননি।
ফয়েজ আলম এটিই বার বার জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, বাংলাদেশে আর্যদের বসতি ও আর্য সভ্যতার বিকাশের কথা বলা হয় কেবলই অনুমানের ভিত্তিতে। কোনো প্রামাণিক তথ্য সেখানে উল্লেখ করা হয় না। অথচ আমরা এসব কথাবার্তাকেই ইতিহাসের বয়ান হিসাবে মেনে নিয়েছি। কেউ-ই প্রশ্ন তুলিনি।
এরপর ফয়েজ আলম দেখিয়েছেন সেই ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস-এ তথ্য প্রমাণবিহীন এই বিবরণ বার বার লেখা হয়েছে পরবর্তী কালের ইতিহাসবিদদের রচনায়। তাদের অনেকের নামও উল্লেখ করেছেন। যেমন, নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী (১৮৯৭), নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (প্রথমভাগ ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথম অংশ, ১৩০৫; রাজন্যকাণ্ড কায়স্থকাণ্ডের প্রথমাংশ, ১৩২১; দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড প্রথমখণ্ড, ১৩৪০), শ্রীদুর্গাচন্দ্র স্যান্যালের বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস (১৯০৮), রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তির গৌড়ের ইতিহাস (১৯১০), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র গৌড় লেখমালা (১৯১২), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড-১৯১৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৭), যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদিত History Of Bengal Vol-I ও Vol-II, রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ) প্রথমখণ্ড প্রভৃতি। আমরা দেখতে পাই রাজকৃষ্ণ বাবুর ঐ বিবরণই পরবর্তীকালের সমস্ত লেখকরা ইতিহাসের সত্য হিসাবে লিখে গেছেন। এমনকি স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের যেসব লেখক ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন, বা পাঠ্যবই লিখেছেন তাদের কেউই এই দিকটায় দৃষ্টি দেননি। এভাবে তথ্যপ্রমাণবিহীন একটি দাবী ইতিহাসের সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
ইতিহাস বিকৃতির পিছনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফয়েজ আলম আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসের আরেক ধুঁয়াশাময় নেতিবাচক অধ্যায়ের মুখোমুখি। সেটি হলো উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের নামে হিন্দুত্ববাদী পুনর্জাগরণ। আমরা সকলেই জানি উনিশ শতকে কলিকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে বাংলায় শিল্পসাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-সমাজচিন্তা সর্বত্র এক নবজাগরণ ঘটে গিয়েছিলো। ইউরোপের রেঁনেসার অনুকরণে বাংলার নবজাগরণ ঘটে থাকবে, এমত অনুমান করা হয়।
গত কয়েক দশকে বাংলার নবজাগরণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে। এখন আর কেউই একে নবজাগরণ বলতে চান না। ফয়েজ আলমও মনে করেন এটি বাংলার নবজাগরণ তো নয়ই, বরং একে কলিকাতার একদল ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী জাগরণ বলা যায়। এর উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। সেই সঙ্গে প্রাচীন বাংলাদেশ হিন্দুরাজ্য ছিলো বলে প্রচার করা। যার মূল লক্ষ্য ছিলো হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা।
এরা ছিলেন কলিকাতায় ইংরেজদের মোসাহেবী মারফত সুবিধাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র একদল ব্রাহ্মণ্যবাদী মানুষ। সাধারণ বাঙালি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধের সাথে এদের বা এদের নবজাগরণের কোনো যোগাযোগই ছিল না। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ বা প্রকৃতি ধর্মের সাধারণ মানুষদের নিয়ে এদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ফয়েজ আলম বলছেন এদেরকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে দেখা ঠিক হবে না। এই দলটিকে তিনি উগ্র হিন্দুত্ববাদী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন তিনি।
ফয়েজ আলমের মতে এরা ছিল ইংরেজদের সহযোগী শক্তি। তাই উনিশ শতকের শুরু থেকেই ইংরেজের চাকুরি ও ব্যবসা বাণিজ্য করে তারা অনেক টাকার মালিক হন। স্কুল কলেজ চালানো, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রচারণার ক্ষমতা চলে আসে তাদের হাতে। তখনই তারা ধর্মীয় বিদ্বেষের বশীভুত হয়ে হিন্দু ধর্মের মানুষদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে মাঠে নামে। এদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন চেষ্টা করে গেছেন ভারতকে আর্য হিন্দুত্ববাদী দেশ হিসাবে দেখানোর। বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলাসহ ভারতে প্রাচীনকাল হতে আর্য সভ্যতার জয়জয়কার ছিলো বলে প্রচার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকেই লেখক দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমবাবু আর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রাচীন বাংলাদেশে আর্য সভ্যতার বিস্তারের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার তাগিদ দেন। একে ফয়েজ আলম বলেছেন ‘বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস প্রকল্প’। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস অন্যরকম হওয়ায় হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসবিদরা চালাকি করে পুরাণের তথ্যের আলোকে প্রচার করেন যে, বাংলায় প্রাচীন কাল থেকেই আর্যসভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। উনিশ শতকের শেষ হতে আরম্ভ করে ইতিহাসের যত বইপত্র লেখা হয় তার সবগুলোতে আর্য সভ্যতা সম্পর্কে একই কথার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে।
বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস প্রকল্পের লক্ষ্য কেবল আর্য সভ্যতার জয়গান গাওয়া নয়। আরো গুরুতর উদ্দেশ্যেও ছিলো। ফয়েজ আলমের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস প্রকল্পের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো “নিম্নশ্রেণির হিন্দু থেকে বাঙালি মুসলমান জনসমাজের উদ্ভব”-এর তত্ত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। আমরাও এ তত্ত্বটির কথা অনেকদিন ধরে শুনে আসছি। সেখানে বলা হয়ে থাকে নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা খুব নির্যাতিত ছিলো। তুর্কিরা বাংলা দখলের পর নির্যাতিত নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা দলে দলে রাতারাতি মুসলমান হয়ে যায়। এরাই বাংলার মুসলিম জনসমাজের বড় অংশ।
আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে ‘নিম্নশ্রেণির হিন্দুর মুসলমান হওয়ার তত্ত্বের’ অসারতা নিয়ে কোনো যৌক্তিক আলোচনা এ যাবত হয়নি। এ নিয়ে ফয়েজ আলমই প্রথম প্রচুর প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ভিন্নমত তুলে ধরেছেন। প্রথমত লেখক দেখিয়েছেন যে: “উচুঁ নাকি নিচু জাতের হিন্দু থাইকা জাত দিয়া বাংলাদেশের মুসলমানরা মুসলমান হইছে এইরকম কোন আলাপ হয় নাই বাংলার আদম শুমারির আগে। কথাটার শুরু ১৮৭২ সালের আদম শুমারির পর। এইটা আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের তোলা হিন্দুত্ববাদী আলাপ, যার গোড়াটা আদম শুমারিতে মুসলমান জনসংখ্যার হার বেশি হওয়ার মধ্যে। উনিশ শতকে হিন্দুত্ববাদ সংগঠিত হওয়ার সময় হিন্দুত্ববাদীরা মনে করতেন বাংলাদেশে হিন্দু বেশি, সেইখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগেও হিন্দু বেশি আছিল। তখন এই রকম একটা কথা চালু আছিল যে প্রাচীন বাংলাদেশ আছিল একটা হিন্দুদেশ।” (ঐ, পৃষ্ঠা:৫৪) অর্থাৎ নিম্নশ্রেণির হিন্দু নাকি উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা মুসলামন হয়েছে তা নিয়ে কোনো আলোচনা আগে ছিল না। ১৮৭২ সালের আদম শুমারিতে যখন ধরা পড়ে বাংলাদেশে হিন্দুর তুলনায় মুসলামন দ্বিগুণ প্রায় তখনই কলিকাতার হিন্দুত্ববাদীরা প্রতিবাদ শুরু করে। পরে তারাই নিম্নশ্রেণির হিন্দু হতে মুসলমান হওয়ার কাহিনীর অবতারণা করে।
অথচ এর পিছনে কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই, কোনো ঐতিহাসিক দলিলদস্তাবেজ নেই, কেবলই অনুমান মাত্র। ফলে আমরা বুঝতে পারি আদম শুমারিতে বাংলাদেশে ধারণাতীত মুসলিম সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হওয়ায় হিন্দুত্ববাদীদের প্রাচীন আর্য-বাংলার দাবীর মুখে চপেটাঘাতের মত লাগে। লেখক বলতে চেয়েছেন তখনই তারা এ তত্ত্বের প্রচারণা শুরু করে। লেখকের ভাষায় “তথ্য-প্রমাণবিহীন, বানোয়াট, মুসলিম জনমানসের মানসিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তৈরি”। লেখক বানোয়াট এ তত্ত্বকে ইতিহাস হিসাবে চালিয়ে দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন সেই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রমেশচন্দ্র মজুমদারকেও। পূর্ববঙ্গেও মুসলমানরা গরীব—কেবল এ কারণে তাদের মনে হয়েছে এরা সকলেই নিম্নশ্রেণির হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া বাঙালি। এর সূচনাও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়। ফয়েজ আলম তার অভিযোগের প্রমাণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক এই উদ্ধৃতিটিও তুলে দিয়েছেন যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন: “এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।” (বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯১: ৩৩৯-৪০, ঐ, পৃষ্ঠা: ২৪)।
ফয়েজ আলম কালানুক্রমিকভাবে দেখিয়েছেন পরবর্তী কালের ইতিহাসবিদরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপরোক্ত তত্ত্বই অনুকরণ করেছেন মাত্র। নিখিলনাথ রায়, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার সবার ক্ষেত্রেই তা সত্যি। রমেশচন্দ্র মজুমদারও লিখেছেন: “হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণির লোকেরা নানা অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিত। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা অনুসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বখতিয়ার খিলজীর একজন মেচজাতীয় অনুচর গৌড়ের সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া যে দলে দলে নিম্নশ্রেণির হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই।” (বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীনযুগ, প্রথমখণ্ড ১৩৮০: ২৩২, ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৪)। বুঝাই যাচ্ছে নিম্নশ্রেণির হিন্দু হতে মুসলমান জনসমাজের উৎপত্তির তত্ত্বেও গোড়ায় কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।
এই তত্ত্বেও অসারতার কথা তুলে ফয়েজ আলম বাংলায় মুসলমানা জনসমাজের উদ্ভবের আরেকটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলছেন বাংলায় মুসলিম জনসমাজের বড় অংশ গড়ে উঠে শান্তিপ্রিয় জ্ঞানসাধক বৌদ্ধ ও স্থানীয় প্রকৃতি ধর্মের অনুসারী অস্ট্রিকদের দ্বারা। সন্দেহ নেই ফয়েজ আলমের এই দাবী একেবারে নতুন এবং গুরুতর। তাই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।
বস্তুত বৌদ্ধ ও প্রকৃতি ধর্মের অনুসারী অস্ট্রিকদের দ্বারা বাঙালি মুসলাম জনসমাজ গড়ে উঠার দাবীর সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের ইতিহাসের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের মূল্যায়নের প্রশ্নটি। যেমন, রজনীকান্ত, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র প্রমুখ বাংলার ইতিহাসের আলোচনায় হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও আধুনিক যুগ—এমন ধরণের যুগ বিভাগ প্রস্তাব করেছেন। বাস্তবে, বাংলায় প্রাচীন কাল হতে ১১২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ শাসন চলেছে, মাঝখানে আশি বছরের মত ছিলো হিন্দু সেনদের শাসন। সেক্ষেত্রে প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত হওয়ার কথা বৌদ্ধযুগ, এরপর অন্তর্বর্তীকালীন হিন্দু শাসন, এরপর মুসলিম যুগ। ফয়েজ আলম খুব যৌক্তিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, আশি বছরের সেন শাসনের উপর নির্ভর করে কোন যুক্তিতে বাঙালির ইতিহাসের হাজার বছরের বৌদ্ধ শাসনামলের বৌদ্ধযুগকে চাপা দিয়ে দেয়া হলো। বরং আশি বছরের হিন্দু সেনদের শাসনসহ গোটা প্রাচীনকালটা বৌদ্ধযুগ হিসাবে চিহ্নিত হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। এখানেই ইতিহাসবিদদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব স্পষ্ট হয় ওঠে।
এ প্রসঙ্গে ফয়েজ বাংলার ইতিহাসের একটি উপেক্ষিত অধ্যায়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটি হলো প্রাচীন কাল থেকে বাংলা ছিল একটি বৌদ্ধ দেশ। এখানে বৌদ্ধরাই ছিলো সংখ্যাগুরু। এর সপক্ষে বেশ কিছু প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনি, ধর্মীয় রচনা থেকে সাক্ষ্য হাজির করেন তিনি। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের (৩২৭ খ্রি.পূ.) সময় হতে খিষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সমসাময়িক গ্রীক লেখক যেমন হেরোডোটাস, মেগাস্থিনিস, প্লিনী, পেরিপ্লাস অব দ্যা ইরিত্রিয়ান সী’র অজ্ঞাত লেখক, টলেমি প্রমুখের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে পাঁচশ বছর এই অঞ্চলে শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য ছিলো । রাজ্যের নাম ছিল গঙ্গারিডি। এরপর ফাহিয়েন (৩৯৯-৪১২) ভারত ভ্রমণে এসে পশ্চিবঙ্গের তমলুকে দু’বছর অবস্থান করে লিখেন যে, ওখানে ২৪টি সংঘারাম আছে এবং সে দেশের মানুষেরা বৌদ্ধধর্মই মানে।
আবার ছয় সাত শতক থেকে দেখা যাচ্ছে সমতটে বৌদ্ধ শাসন। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে হিউয়েন সাঙ বাংলা সফর করে কর্ণসুবর্ণ, পুন্ড্রবর্ধন, সমতট ও তমলুকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি দেখতে পান। এরপর জৈন ধর্ম। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে বুঝা যায় তার সময়ে বাংলায় বৌদ্ধই ছিলো প্রধান ধর্ম, তারপর জৈন। অন্য কোনো ধর্মের কথা তিনি আলাদাভাবে উল্লেখও করেননি। এরপর বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পালেরা বাংলায় ক্ষমতায় এসে মোটামুটি ১১২৫/২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। তখন বৌদ্ধ ধর্মের আরো বিস্তৃতি হওয়ার অনুমানই স্বাভাবিক। ফলে বলা যায় প্রাচীন কাল হতে বারো শতকের শুরু পর্যন্ত বাংলা ছিলো একটি বৌদ্ধ প্রধান দেশ।
পালদের পর ক্ষমতায় আসে কর্নাটকের অবাঙালি সেনরা। সেনেরা সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। বাংলা ভাষার চর্চা বন্ধ হয়া যায়। ফয়েজ আলম লিখেছেন: “বলতে গেলে সেন আমলেই সংগঠিত ব্রাহ্মন্যবাদের চর্চা শুরু হয় বাংলাদেশে। অন্য ধর্মের মানুষদের উপর চলে নানা রকম নির্যাতন। … বল্লাল সেনের সময় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়া কিছু কিছু বৌদ্ধ হিন্দু হয়া যায়। নেপালে পালায়া যায় অনেক বৌদ্ধ ধর্মগুরু, শিক্ষক, লেখক। …তখনই নেপালে বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। এর বিবরণ পাওয়া যায় সমকালীন সাহিত্য এবং পরবর্তী কোনো কোনো রচনায়। এসব উল্লেখ করা হইছে লামা তারানাথের ‘ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বইয়েও’। তারানাথ বলছেন যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটা দল বখতিয়ার খিলজির কাছে আগায়া যায় এবং বাংলা আক্রমনে উস্কানি দেয়। এ পরিস্থিতিতে তুর্কি আক্রমনের সময় নির্যাতিত বৌদ্ধরা মুসলমানদের পক্ষ নেয়। … তুর্কিরা ক্ষমতায় আসলে এইসব নির্যাতিত বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম গ্রহন করে।” (ঐ, পৃষ্ঠা: ৬০-৬১)
উদ্ধৃতির এ অংশের বক্তব্যে আমাদের ইতিহাস চর্চায় নতুন এক তত্ত্বের প্রস্তাবনা লক্ষ্যণীয়। এ যাবত কলিকাতাকেন্দ্রিক ইতিহাসে পড়ে এসেছি নিম্নশ্রেণির হিন্দু থেকে বাঙালি মুসলিম জনসমাজের সৃষ্টি। আবার এর বিপরীতে বাংলাদেশের কোনো কোনো ঐতিহাসিক বাঙালির রক্তে বহিরাগত তুর্কি-ইরানি-আরব রক্তের প্রাধান্য দাবী করেছেন। আমরা ইতিহাসের সাধারণ পাঠকেরা এ দু’তত্ত্বের মধ্যেই অসঙ্গতি ও বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করেছি।
ফয়েজ আলম বৌদ্ধ ও স্থানীয় প্রকৃতি ধর্মানুসারী বিপুল বাঙালি জনগোষ্ঠীর দ্বারাই বাঙালি মুসলমান জনসমাজের গোড়াপত্তনের যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তা অনেক বেশি যৌক্তিক ভিত্তির উপর রচিত বলে মনে হয়। তার বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রাচীন ও সাম্প্রতিক গ্রন্থাদি থেকে সাক্ষ্যও হাজির করেছেন লেখক। তাছাড়া, প্রাচীন কাল হতে বারো শতকের শুরু পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল বৌদ্ধপ্রধান। বাংলাদেশে তুর্কি শাসন কায়েম হওয়ার পর এসব মানুষের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়েই নতুন মুসলিম জনসমাজ গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। লেখকও অনুরূপ যুক্তিও উপস্থাপন করেছেন: “মুসলমানদের আক্রমনের সময় সেখানে বৌদ্ধরাই ছিল সংখ্যাগুরু, হিন্দু ধর্মীয় লোকের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কাজেই হিন্দুরা মুসলমান হওয়ার কারনে সেইখানে মুসলমান বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না। কেবল সংখ্যাগুরু বৌদ্ধরা দলে দলে মুসলমান হয়া থাকলেই মুসলিম জনসংখ্যা বেশি হইতে পারে। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তিও লেখছেন: ‘উৎপীড়িত হইয়া অনেক বৌদ্ধ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এই ঘটনা বিশেষরূপে ঘটিয়াছিল বোধ হয়’।” (ঐ, পৃষ্ঠা: ৬১-৬২)
এ বিষয়ে লেখক কেবল রজনীকান্ত নয় ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, লামা তারানাথ, নগেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখের বই থেকে প্রাসঙ্গিক অনুকূল মতামত উদ্ধৃত করেছেন। সবশেষে মত প্রকাশ করেছেন বাঙালি মুসলমান জনসমাজের উৎস নির্ধারণের হিসাব হওয়া উচিত এরকম: বৌদ্ধ ও প্রকৃতিবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠ অস্ট্রিক বাঙালি, আরব-ইরানী-তুর্কি-মধ্যএশীয় মুসলমান, সেই তুলনায় সংখ্যালঘু হিন্দু এবং মোঙ্গল রক্তের স্বল্পসংখ্যক উপজাতীয় মানুষ।
বস্তুত, বাংলাদেশে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রধান দেশ ছিলো এ সত্য কিভাবে যেন আমাদের ইতিহাসের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি করে সেটি সম্ভব হলো, যখন সারা বাংলাদেশেই প্রচুর বৌদ্ধ স্থাপনা আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত রয়ে গেছে? রাজশাহীর নওগাঁর সোমপুর বিহার ও জগদ্দল বিহার পৃথিবী বিখ্যাত, দিনাজুপরের পার্বতীপুর নবাবগঞ্জে পাওয়া গেছে প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ, রংপুরে লোহানীপাড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের আবিষ্কৃত হয়েছে বৌদ্ধবিহারের কাঠামো, সম্প্রতি পাবনায় পাওয়া গেছে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের চিহ্ন। বগুড়া আর কুমিল্লা বহুকাল পূর্ব হতে বড়সরো দুই বৌদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি। এতসব প্রমাণ থাকা সাপেক্ষেও আমাদের ইতিহাস প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ বাঙালি জনসমাজ সম্পর্কে নীরব কেন? ফয়েজ আলমই প্রথম বারের মত সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা করছেন। তিনি বৌদ্ধ বাংলার ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো তুলে ধরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন তুর্কি বিজয়ের আগে পর্যন্ত বাংলা ছিলো বাঙালি বৌদ্ধদের মাতৃভুমি।
তৃতীয় আরেকটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন ফয়েজ। সেটি হলো আমাদের ইতিহাসে পুরাণের ব্যবহার। তিনি দেখিয়েছেন সেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার থেকে আরম্ভ করে রমেশচন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত সকল খ্যাতনামা ইতিহাসবিদগণ পুরাণের বিবরণকে ইতিহাসের সত্য হিসাবে উপস্থিত করেছেন। পুরাণ ইতিহাস নয়। পুরাণ লোকমানসের সৃষ্টি। কোনো একটা মূল কাঠামো সৃষ্টি হওয়ার পর বহুশত বছর ধরে অনেক মানুষের হাতে তার রচনা চলেছে, পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংশোধন হয়েছে। কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন যুগের মানুষের কল্পনাশক্তি ও সাংস্কৃতিক রুচি-আকাঙ্খা-স্বপ্নের একটু একটু ফসল। এটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট কালের কোনো বিশেষ মানুষের কথা বলে না। অতএব, পুরাণকে কোনো এক বিশেষ সময়ের কোনো ব্যক্তি বা সমাজের বয়ান হিসাবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। পুরাণের না আছে নির্দিষ্ট কালিক স্বাক্ষর, না নির্দিষ্ট কোনো অতীত-বাস্তবের প্রতিফলন। পুরাণের কোনো বিশেষ তথ্যকে ইতিহাসে ব্যবহার করতে হলে তার সত্যাসত্য অন্য উৎস থেকে যাচাই করে নিতে হবে। কিন্তু বাঙালির ইতিহাসের লেখায় পুরাণের ঢালাউ ব্যবহার হয়েছে। পুরাণের বয়ানকে এমনভাবে হাজির করা হয়েছে যেন মনে হয় এটি খাঁটি সত্য বিবরণ।
ফয়েজ আলম দেখান সেই প্রথম মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পুরাণ কাহিনী নিয়ে লেখন “রাজাবলী”। অতপর রাজকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায়ও পুরানের উল্লেখ থেকে প্রমাণ করতে চান বাংলায় প্রাচীন কাল হতে আর্য অধিকার চলে আসছিলো। রজনীকান্ত-নগেন্দ্রনাথ-রাখাল দাস-রমেশচন্দ্র প্রত্যেকে পুরাণের বয়ানকে টেক্সট হিসাবে লিখে গেছেন। এর কারণটাও দেখিয়ে দিয়েছেন ফয়েজ।
উনিশ শতকের কলিকাতায় ইংরেজদের মোসাহেবী করে প্রচুর অর্থবিত্ত অর্জন করেছিলো একদল সংখ্যালঘূ ব্রাহ্মণবাদী মানুষ। কাঁচা অর্থ, সম্পদ ও ক্ষমতার ভাগপাওয়া এ শ্রেণিটি কলিকাতার বাঙালি সমাজের মাথা হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বশত এরা নিজেদের আর্য পরিচয় ও আর্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়ে দেখতে পায় প্রাচীন বাংলায় আর্যদের গৌরবের ইতিহাস নেই, কোনো তথ্যপ্রমাণও নেই। তখনই তারা পুরাণ লোকসাহিত্য ইত্যাদি অবলম্বনে বাংলায় আর্য গৌরবের বানোয়াট ইতিহাস উপস্থিত করে। একই কারণে এ দেশের বৌদ্ধ প্রাধান্যের ইতিহাসও নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন ছিল। তাই তাদের লেখা ইতিহাস থেকে বাংলার অতীত গৌরবের জনক বৌদ্ধ বাঙালিদের অস্তিত্বই যেন নেই হয়ে গেছে। সে স্থলে দেখা দিয়েছে কল্পিত আর্য জনসমাজ ও আর্যত্বের গৌরবের কাহিনী। ফয়েজ আলম বলছেন পুরাণের বয়ানকে ইতিহাসের সত্য হিসাবে চালিয়ে দেয়ার কারণে বাঙালির নিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি হয়েছে।
বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা একটি ছোট গ্রন্থ, মাত্র ৬৮ পৃষ্ঠার কলেবর। এই অল্পকিছু পৃষ্ঠায় যেন বিপুল ভাবনা-চিন্তা-বিতর্ক-আলোচনার পরিসর সৃষ্টি হয়ে আছে। বিশেষ করে ‘নিম্নশ্রেণির বাঙালি থেকে মুসলমান জনগোষ্ঠীর উৎপত্তির তথ্য-প্রমাণবিহীন প্রচারণা’র বিপরীতে ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত বৌদ্ধবাংলার বিবরণ এবং বৌদ্ধ ও প্রকৃতিধর্মী অস্ট্রিক বাঙালিদের থেকে মুসলমান সমাজের উৎপত্তি সংক্রান্ত ফয়েজ আলমের নতুন তত্ত্ব প্রতিটি সচেতন বাঙালির মনোযোগী বিবেচনার দাবী রাখে। ফয়েজ আলম যেভাবে প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসহ আধুনিক কালের বইপত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের সাক্ষ্য উপস্থিত করে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা সহজে খারিজ করে দেয়াও সম্ভব নয়।
আমাদের ইতিহাস চর্চা এখনো প্রতিষ্ঠান নির্ভর। আর প্রতিষ্ঠানে ইতিহাস চর্চাকারীরা যেন কোনো মতেই বাঙালির অতীত ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে রাজী নন। অথচ গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাম্রলিপিসহ নানা লিখিত নমুনা পাওয়া গেছে তবু অতীত বাংলার ইতিহাস নিস্তরঙ্গই। ফয়েজ আলমের বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা সেই নির্লিপ্ত, নিস্তরঙ্গ জ্ঞানভাষ্যে বিপুল আলোড়ন জাগাবে বলেই মনে হয়। আর তা হলে, প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চাকারীরা যতই নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করুন না কেন, বাঙালির ইতিহাসের পুনর্লিখন জরুরি হয়ে দাড়াবে নি:সন্দেহে।
বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা
লেখক: ফয়েজ আলম
বিষয়: গবেষণা
প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ২০২৪ সাল
প্রকাশক: ঘাসফুল
মূল্য: ২৩০ টাকা।