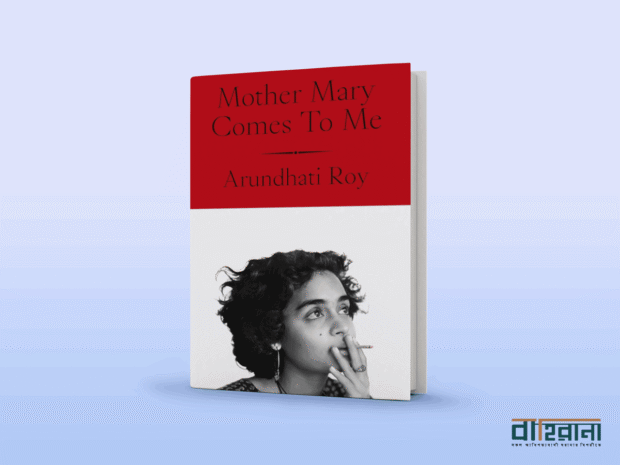অরুন্ধতী রায়ের মাদার মেরি কামস টু মি আত্মজীবনী শুরু হয়েছে তার গোত্রচ্যুত মা মেরি রায়ের শেষকৃত্যের বর্ণনা দিয়ে। ২০২২ সালে তিনি মারা যান, কেরালার এক খ্রীস্টান পরিবারের মেয়ে মেরি অরুন্ধতি রায়ের মা, তার ধর্ম ও স্বজাতি ছেড়ে এক বাঙালিকে বিয়ে করেছিলেন। স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি সেই কলকাতার বাঙালি যিনি বাংলাদেশের বরিশাল থেকে অভিবাসী হয়েছিলেন কলকাতায়, বন্ধুমহলে পরিচিতি ছিল তার মিকি রয় বা রায় নামে। চাকরি করতেন আসামের এক চা বাগানে, সেখানে তিনি মদপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। মিকি রয়কে মেরি ছেড়ে যান যখন মিকি এলকোহলিক হয়ে পড়েন। সঙ্গে নেন দুই সন্তান অরুদ্ধতি ও তার ভাই ললিতকে। স্মৃতিকথাটি মাকে দিয়ে শুরু হয়ে বেশিরভাগ অংশই তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। অরুন্ধতি বইটি উৎসর্গ করেছেন তার ভাই ও মাকে। মাকে উৎসর্গকৃত বাক্যটিও অসাধারণ, “Who never said let it be” “যে কখনও বলেনি হও” আমরা সহজেই বাইবেলের মেরির সঙ্গে তার যুগসূত্রতা আবিষ্কার করি। যিশুর মা মেরিও কখনও বলেননি, হও। এবং দুইজনকেই সমাজের বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল, তাদের মতো করে।
অরুন্ধতী রায়ের মাদার মেরি কামস টু মি স্মৃতিকথার শুরু ও শেষ সব জায়গাতেই তার মায়ের উপস্থিতি রয়েছে, তবে এই বর্তমান পৃথিবীতে তিনি হার মানবেন না সেই প্রতিশ্রুতিই দ্বিতীয় অংশের তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ায় ফুঁটে উঠেছে।
অরুন্ধতী আর্কিটেকচার নিয়ে পড়ার জন্য দিল্লি এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতের কোট্টায়াম থেকে ১৯৭৬ সালে, হিন্দি ভাষা জানা ছিল না তার। ১৮ বছর বয়স যখন তার, তখন থেকেই তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। “I left my mother not because I did’nt love her, but in order to be able to continue to love her” (মাদার মেরি কামস টু মি)। তার মা এ নিয়ে কিছু বলেননি, বিষয়টি নিয়ে মাদার মেরি কামস টু মি বইয়ে তিনি লিখেছেন তার প্রথম উপন্যাস গড অব স্মল থিংস-এ মায়ের সঙ্গে দূরত্বের প্রসঙ্গটি রয়েছে একটি বাক্যে, মায়ের উল্লেখে, “She loved me enough to let me go”। অরুন্ধতী রায়ের যাবতীয়ে লেখালেখি ও পৃথিজোড়া খ্যাতি এনে দেওয়া গড অব স্মল থিংস এই সময়গুলোতেই লেখা। কিন্তু আর্কিটেকচারের ডিগ্রি, রোজগার শুরু করা ও একজন সফল লেখক হয়ে উঠার পর মায়ের সঙ্গে আবার পুনর্মিলন হয়েছিল তার। তখন থেকে তাদের প্রতিনিয়তই দেখা হতো। বইয়ের প্রথম দিকের এই অধ্যায়গুলোকে মায়ের সঙ্গে, ভাইয়ের সঙ্গে ও পরিবার, যাপিত জীবনের ছোট-বড় শহরগুলোর বর্ণনায় অরুন্ধতী নিজের লেখক সত্তা ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠার আখ্যান শুনিয়েছেন। যা তার লেখালেখিকে অনুধাবনের জন্য অত্যাবশ্যক উপাদান।
১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস বিপদজনক বিধায় তার মা আসাম থেকে কলকাতায় তিন বছরের অরুন্ধতি রায় ও সাড়ে চার বছর বয়সী তার ভাই ললিত কুমার রায়কে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু ফেরার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন তামিলনাড়ুতে ফিরে যাবেন। তাই করেন, পুরো দেশ ঘুরে দুই সন্তান নিয়ে দক্ষিণভারতে চলে যান। এরপর অরুন্ধতী ও তার ভাই আর বাবাকে দেখতে পাননি, তবে তাদের দুজনেরই বিশের কোঠায় যখন বয়স তখন আবার বাবা মিকি রয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।
ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রতিক কালপর্বে অনেকেই ইংরেজিতে লিখে খ্যাতি পেয়েছেন যেমন পুলিৎজারজয়ী ঝুম্পা লাহিড়ী অন্যতম। ঝুম্পা লাহিড়ী এখন ইতালিয়ান ভাষাতেও লিখছেন। তবে অরুন্ধতী রায়ের সঙ্গে অভিবাসী সাহিত্যিকদের পার্থক্য শুধু আঙ্গিকগত নয়, ইংরেজিতে লিখলেও অরুন্ধতী রায় ভারতেই বসবাস করেন। এই পার্থক্যের কথা বলার কারণ হলো, ভারতে অবস্থানের কারণে বহুবছর ধরেই অরুন্ধতী রায় সেদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নিপীড়নমূলক শাসনের বিরুদ্ধে তার কলমযুদ্ধ ও মাঠপর্যায়ে সরাসরি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ জারি রেখেছেন। তবে তার গদ্য নিয়ে বলা যায়, তা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের গদ্যের ঝরে ঝরে পরিষ্কার ও পরিচ্ছতার প্রসাদগুণসম্পন্ন আবার তার জনমানুষের পক্ষে থাকার সাহসও হেমিংওয়েরই মতো। মাদার মেরি কামস টু মি বইয়ের দ্বিতীয় অংশ এই ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে তার অবস্থান নিয়ে। ভারতের পরমাণু কর্মসূচির বিরুদ্ধে তার অবস্থানসহ আরো বিভিন্ন সামাজিক প্রতিরোধ বিষয়ে তার পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে এই অংশে। এই বিবেচনায় ভারতীয় জাতীয় প্রদেশগুলোর ভাষায় রচিত সাহিত্যিকদের প্রতিবাদের সঙ্গে অরুন্ধতীর প্রতিবাদ—সবই ভারত রাষ্ট্রের নিপীড়নের মধ্যে বসে মুখোমুখি। তবে অরুন্ধতীর ভাষা ইংরেজি হওয়ায় ভারত যে ধর্মবাদী ও নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে তা বিশ্বদরবারে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে।
এই স্মৃতিকথায় বিভিন্ন বিষয় এসেছে, তার ব্যক্তিত্বের গভীরতা ও কাজের ব্যাপ্তি বোঝা যেতে পারে এতে। যেমন, বুকার জয়ী অরুন্ধতী রায় একজন নারীবাদীও, নারীবাদের মধ্যে কীভাবে পুরুষতন্ত্র ঢুকে পড়ে তার একটা চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়েছেন বইটিতে ডাকাত রাণী ফুলন দেবীর উপর নির্মিত চলচ্চিত্র ব্যান্ডিট কুইন (১৯৯৪) হলে বসে দেখার স্মৃতিচারণায়। তিনি যে হলে সিনেমাটি দেখছিলেন, তার থেকে মাত্র কয়েকমিনিট দূরত্বে থাকতেন জেল থেকে সাজা শেষ করে বেরুনো ফুলন দেবী। কিন্তু পরিচালক তাকে হলে আমন্ত্রণ জানাননি। ফুলন দেবীকে উচ্চজাত ২২ জন পুরুষ সংঘবন্ধ ধর্ষণ করেছিল, এরপর তিনি ডাকাত দল গঠন করে ২২ জনকেই মেরেছিলেন। কিন্তু সিনেমাটিতে ফুলন দেবীর ঘর্ষণকাণ্ডকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে মূল ধর্ষণের বাইরে মূল নারীটিকেই আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। বইয়ে আছে, “Over two hours it lingered vicariously on scenes of Phoolan Devi being explicitly and serially raped in various ways by various men until we almost forget who Phoolan Devi really was.” দুই ঘন্টার এই টানা ধর্ষণঘটনাকে অরুন্ধতী রায় বলেন, এটি, “ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ডাকাতকে ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ষণ উপদ্রুততে পরিণত করেছে।” এখানেই সমাপ্তি ঘটেনি, সিনেমা শেষ করেই তিনি ফুলন দেবীর সঙ্গে দেখা করতে যান, এবং এ নিয়ে তিনি পত্রিকায় লেখেন। ফলে, চ্যানের ৪ এর সঙ্গে তার একটি চুক্তি বাতিলসহ অনেক শত্রুও তৈরি হয়। কিন্তু আশার কথা এই, ফুলন দেবী এই সিনেমার বিরুদ্ধে কোর্টে উঠেন, এবং সিনেমার দুইবছর পর রাজনৈতিক দলে যোগ দেন ও সংসদ সদস্য হন।
এখানে অরুন্ধতীর সঙ্গে বাংলাদেশের নারীবাদের বৈপরীত্য দেখতে পাই আমরা। তিনি স্পষ্ট জানেন পুরুষতন্ত্র ও ক্ষমতা আসলে একই, এবং এতে জড়িত পক্ষগুলোকে যদি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা না যায় তাহলে তা আপোষে রূপ নেয়। ফুলদেবীর ঘটনায় তিনি যে পুরুষতন্ত্র ও পুঁজির যে গ্রাউন্ড ন্যারেটিভ খুঁজে পেয়েছিলেন, তা-ই তিনি প্রকাশ করেছিলেন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে। এই ফুলনদেবীর ছায়াপাত ঘটেছেন তার গড অব স্মল থিংস উপন্যাসের এক চরিত্রে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের ধর্ষণবর্ণনা নিয়ে বহু বই রয়েছে, সেগুলোতে বীরাঙ্গনারা কতটুকু থেকেছেন আর কতটুকু রগরগে ধর্ষণকাণ্ড মূখ্য ভূমিকায় পুঁজির তাবেদারী করেছে সেটা অরুন্ধতীর এই ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।
অরুন্ধতী রায়ের মাদার মেরি কামস টু মি স্মৃতিকথার শুরু ও শেষ সব জায়গাতেই তার মায়ের উপস্থিতি রয়েছে, তবে এই বর্তমান পৃথিবীতে তিনি হার মানবেন না সেই প্রতিশ্রুতিই দ্বিতীয় অংশের তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ায় ফুঁটে উঠেছে। সেই অনুপ্রেরণাও তিনি তার মায়ের জীবন যুদ্ধ থেকে পেয়েছেন। বাংলাদেশের বরিশালের মেয়ে অরুন্ধতী রায়, যেমন বাংলাদেশের বরিশালের কবি জীবনানন্দ দাশ ও আবুল হাসান। দুই কবির মতো অরুন্ধতীকেও কেন বাংলাদেশ নিজের বলে মনে করে না সেই আক্ষেপ রয়ে গেল। যখন মিকি রয় অতিরিক্ত মদ্যপানের আসক্তিতে স্ত্রী ও সন্তানদের হারিয়েছিলেন, তখন তার যে পরিচয় দাঁড়িয়েছিল সেই নাম দিয়ে বড় ভালোবাসায় অরুন্ধতী রায় বইয়ের শেষে বাবাকে স্মরণ করেছেন, “নাথিং ম্যান” বলে। অরুন্ধতী রায় এই দেশের, আমাদেরই একজন, এ কোনো জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত বক্তব্য নয়, তার বাবার নাড়ী পোতা বাংলাদেশে। অরুন্ধতী কয়েকবছর আগে বাংলাদেশে সত্য ও লেখকের দায় নিয়ে যা বলেছিলেন, তার সারসংক্ষেপ হলো, “সত্যই লেখকের পাশে দাঁড়ায় ক্ষমতার বিরুদ্ধে, তাই সত্য প্রকাশ করতে হবে।” আমাদেরও সত্যকে গ্রহণ ও প্রকাশ করতে হবে, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যলোপকারী পৃথিবীতে। সত্যেই মুক্তি।
মাদার মেরি কামস টু মি
অরুন্ধতী রায়
প্রকাশক: পেঙ্গুইন বুকস
প্রকাশকাল: ২০২৫ সাল।