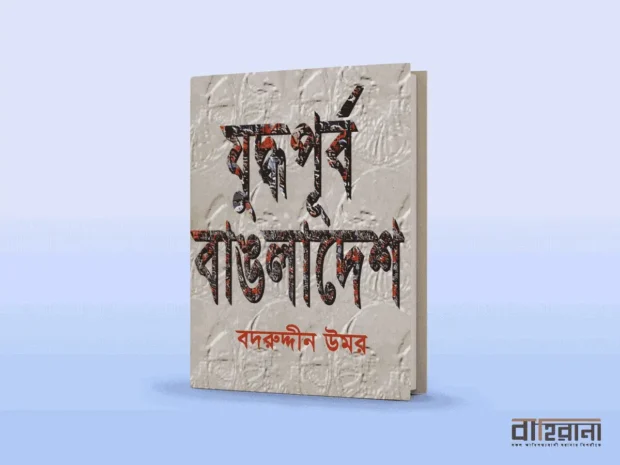বামপন্থী তাত্ত্বিক বদরুদ্দীন উমরের যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ (প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬) বাংলাদেশের ১৯৭১ পূর্ববর্তী রাজনীতিকে বোঝার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই। কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে শোষণ করছিল এবং এদেশীয় কোন কোন পক্ষ তাদের সহযোগী ছিল। এবং কেন ও কীভাবে জনগণ শোষক রাষ্ট্রকাঠামেরা বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল তার সবচেয়ে সুন্দর ভাষ্য হচ্ছে বইটি। এই মহাগুরুত্বপূর্ণ বইটিকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয় বা বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই বই ছাড়া পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক বইটিতেও এই বিষয়গুলো পেয়েছি আমরা বিস্তৃত পরিসরে। তবে শুধু বাংলাদেশের রাজীনীতি নয় বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ক বইয়ের তালিকাতেও নিঃসন্দেহে যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ অত্যাবশ্যকভাবে উপরের দিকে থাকবে। উমরের বইটির সাথে আরেকটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বই আবুল মনসুর আহমদের আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর বইটিও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমাদের দৃষ্টি পরিষ্কার করতে ও আগাপাছতলা বুঝতে বিরাটভাবে সাহায্য করে। এখানেও ১৯৭১ সালের আগের-পরের ইতিহাস পাই আমরা।
বইয়ের ভূমিকায় বদরুদ্দীন উমর আমাদের জানাচ্ছেন, ১৯৭০-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৭১ এর মার্চ পর্যন্ত গণশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ বইটি। এখানে সময়টির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যেতে পারে কেন বইটি গুরুত্বপূর্ণ। ৭০ এর উত্তাল সময় থেকে ১৯৭১ সালের ২১শে মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক অঙ্গনে যত ঘটনা ঘটেছে এবং ধর্মঘটসহ গণআন্দোলন, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, কৃষক-শ্রমিক বিদ্রোহ—তার সব নিয়েই টানা লিখে গেছেন বদরুদ্দীন উমর। ঘটনাগুলোর উল্লেখেই তিনি থেমে থাকেননি সেগুলো বিশ্লেষণপূর্বক নিজস্ব মত যুক্ত করেছেন। মতগুলো সবই সাধারণ জনগণের পক্ষ নিয়ে। ১৯৭০ সালে বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড) শিরোনামে আরেকটি বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানেও ভাষা আন্দোলন ও রাজনীতির সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ভাষা ও রাজনীতি নিয়ে জানতে বইটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ বইটি সহজে বুঝতেও সহায়ক হবে সেটি আগে পড়লে। আর পশ্চিমা রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের কথাকে আলাদা করে দেখলে উমর একাই বাংলাদেশে বসে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করেননি। বুকারজয়ী আফ্রিকান কবি ও কথাসাহিত্যিক বেন ওকরির আফ্রিকার শোকগাথা শিরোনামে কবিতার বইটির মধ্যেও এই বিষয়গুলো আমরা পাই। তৃতীয় বিশ্বের সেই কবি যখন কবিতায় নিজের দেশের কথা বলেন তখন সেখানে যেন উমরের কথাগুলোও ধ্বনিত হয়।
একপক্ষে দেশের সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, জনতা, শিক্ষক, খেঁটে খাওয়া মানুষ অন্য দিকে তারা যারা এই মানুষদের বিরোধী, পক্ষগুলো হলো পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব বাংলার মিল মালিক পক্ষ, এই মালিক পক্ষের স্বার্থ রক্ষাকারী রাজনৈতিক দল। যে দলগুলোর মধ্যে উমর আওয়ামী লীগ ও জামাতে ইসলামকেও ফেলেছিলেন। জামাত চাইত ইসলামী শাসনতন্ত্র। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের ন্যায্য সমস্যার সমাধান নির্বাচনের মাধ্যমে চাইছিল কিন্তু অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে হটিয়ে নয়। ফলে উমরের কাছে এই দুই পক্ষই শত্রুপক্ষ। তাই উপরে বলা স্বাধীনতার সময় এই দলগুলোর ভূমিকা কীরকম হবে তার উত্তর পাঠকদের বোধবুদ্ধিতে সহজেই চলে আসে।
একটা বিষয় মনে রাখা জরুরি, বদরুদ্দীন উমরের যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ বইটির সময়কাল ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ এর ২১শে মার্চ পর্যন্ত। আর এখানেই বইটি বিশেষ—কারণ তখন আওয়ামী লীগের সব নেতা কর্মীরা দেশে ছিলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ছিলেন (উমর শেখ মুজিবের নামের আগে বঙ্গবন্ধু ব্যবহার করেন না, নিতান্ত করতেই হলে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করেন), জামাতে ইসলাম সদর্পে ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েমের জন্য সভা সমাবেশ করেছে। জামাতের পূর্ব বাংলার প্রধান গোলাম আজম ৫২ এর ভাষা আন্দোলন ভুল ছিল বলে আক্ষেপ করেছেন এবং তিনি নিজেও তাতে জড়িত ছিলেন বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। (তবে উমর তার ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কথায় ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।) আওয়ামী লীগসহ জামাত ও অন্য দলগুলো নিজেরা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে তাদের মিল মালিক পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে ও তাদের পত্র পত্রিকায় গণআন্দোলন ও ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে। বদরুদ্দীন উমর বামপন্থার দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ হাজির করেছেন পাঠকদের কাছে।
বদরুদ্দীন উমরের যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ-এ তিনি পুঁজিপতিদের ও বড় রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত পত্রিকাগুলোর গণআন্দোলন ও ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচারণা বিশেষ করে ইত্তেফাকের ভূমিকা ও জামাতের মুখপাত্র পত্রিকা ‘সংগ্রাম’ -এর ভূমিকা সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। তার আরেকটি বই “যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ”-এ যুদ্ধের পরে এখানে বর্ণিত পক্ষগুলো নিয়ে তার বিশ্লেষণ তিনি হাজির করেছেন কিন্তু যুদ্ধের পূর্বেই পরিস্থিতির মধ্যে থাকা দ্বন্দ্বগুলোকে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন, কারণ আগামীর বাংলাদেশের রূপ কেমন হবে তা এই জায়গাটিতেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আরেকটি বইয়েও তার বিশ্লেষণগুলো মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। বইটি হলো মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা নিয়ে হাসান ফেরদৌসের ভুট্টোর তওবা ও মুক্তিযুদ্ধের নানা দিক । এই বইয়ে বাংলাদেশেরে মুক্তিযুদ্ধের অনেক জানা ও অজানা দিক তুলে ধরেছেন হাসান ফেরদৌস। বইটির বদৌলতে আমরা জানতে পারি মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার জন্য ভুট্টো একবার ঢাকায় ক্ষমা চেয়েছিলেন। এবং আন্তার্জাতিক পক্ষগুলো মুক্তিযুদ্ধে কী ভূমিকা রেখেছিল তা জানতেও হাসান ফেরদৌসের বইটির সঙ্গে উমরের যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।
গণআন্দোলন ও ধর্মঘটে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়ে বইটি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক, “একদিকে যখন এইভাবে গণ আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন অন্যদিকে নির্বাচনের নামে আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যেও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতির মুখোশধারী মহল থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।” (নির্বাচন, ধর্মঘট ও গণআন্দোলন)। এরপর আরো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে, “এই দলগুলির মধ্যে আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছে যে, তারা ক্ষমতায় প্রায় এসে গেছে, শুধু নির্বাচনের অপেক্ষা। কাজেই তারা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সরকারী দলের মতোই কাণ্ডকারখানা শুরু করেছে। তারা মনে করছে মাধ্যমিক শিক্ষক, বাস-ট্রাক শ্রমিক, বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক যারাই ধর্মঘট অথবা আন্দোলন করছে তারাই আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টিকারী। তারা যেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করছে অথবা ধর্ম ঘটের ডাক দিচ্ছে;” (ঐ)।
বইটিতে তার প্রবন্ধগুলো (এ নামেই তিনি লেখাগুলোকে আখ্যায়িত করেছেন) পড়লে বোঝা যায় এ সাধারণ ধারাবিবরণী নয় বরং উল্টো, যে, তিনি সুস্পষ্টভাবে শ্রেণী নির্ধারণ করেছিলেন। এই ধর্মঘট ও গণআন্দোলনগুলো আদতে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে অকার্যকর করে জনগণের হাতে ক্ষমতা নেওয়ারই অংশ। জনগণ তখন এসবের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছিল। তাই শাসক শ্রেণী যেকোনো মূ্ল্যে সেগুলো বন্ধ করতে চাইছিল।
একপক্ষে দেশের সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, জনতা, শিক্ষক, খেঁটে খাওয়া মানুষ অন্য দিকে তারা যারা এই মানুষদের বিরোধী, পক্ষগুলো হলো পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব বাংলার মিল মালিক পক্ষ, এই মালিক পক্ষের স্বার্থ রক্ষাকারী রাজনৈতিক দল। যে দলগুলোর মধ্যে উমর আওয়ামী লীগ ও জামাতে ইসলামকেও ফেলেছিলেন। জামাত চাইত ইসলামী শাসনতন্ত্র। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের ন্যায্য সমস্যার সমাধান নির্বাচনের মাধ্যমে চাইছিল কিন্তু অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে হটিয়ে নয়। ফলে উমরের কাছে এই দুই পক্ষই শত্রুপক্ষ। তাই উপরে বলা স্বাধীনতার সময় এই দলগুলোর ভূমিকা কীরকম হবে তার উত্তর পাঠকদের বোধবুদ্ধিতে সহজেই চলে আসে।
বদরুদ্দীন উমরের যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ বইটি আমাদের জানাচ্ছে বাংলার সর্বস্তরের সাধারণ জনগণই ছিল আদতে মুক্তিযুদ্ধের মূল ধারক ও বাহক। কারণ বিষয়টি স্পষ্ট, তাদের উপর অন্যায়ের প্রতিকার চেয়েছে তারা। রাজনৈতিক দলগুলো নয়। “জনগণের সংগ্রামী চেতনা এবং উদ্যম আজ যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সেখানে সংসদীয় রাজনীতির আর কোনো স্থান নেই। জনগণ এখন সরাসরিভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে হামলার মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এগিয়ে চলেছেন এবং সেই কাফেলায় এসে শরীক হয়েছেন পূর্ব বাঙলার জনগণের সর্বস্তরের মানুষ—শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী এমনকি অবাঙালী গরীব জনগণ।” (জনগণের সংগ্রামী কাফেলা এগিয়ে যাবে, ৭ই মার্চ ১৯৭১, ঐ)। এর কারণ শনাক্তের জন্য বাংলাদেশের জনগণের সতর্কতা বিষয়ে একটু উপরেই রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ছলচাতুরি নিয়ে, “জনগণের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদকে শাসকশ্রেণীর নিজেদের হাতের মুঠোয় এনে তাকে দিয়ে ইচ্ছেমতো ভাবে কাজ করিয়ে নেওয়ার যে সংকল্প করেছিলো আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সে পথ রুদ্ধ করেছে। তাদের পক্ষেও আজ আর তাদের ঘোষিত কর্মসূচির ক্ষেত্রে আপোষের সুযোগ নেই। জনগণের সতর্কতাই তাদেরকে সেই আপোষ প্রচেষ্টা থেকে আজ বিরত রাখছে। এবং এর ফলেই পাকিস্তানের শাসক-শ্রেণীর এবং পূর্ব বাঙলার জনগণের মধ্যে বিরোধ আজ শাসকশ্রেণীকে নিক্ষেপ করেছে এক নিদারুণ সংকটের মধ্যে।”(ঐ)।
ভোট নিয়ে এক জায়গায় তিনি বলেছেন “জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে ছিল গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিকে যাচাই করার উদ্দেশ্যে।” এবং তারা এর মাধ্যমে সংকট ঘণীভূত করে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ফলাফল মুক্তিযুদ্ধ। বদরুদ্দীন উমরের যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ-এ ইতিহাস এভাবেই এগিয়েছে, জনগণই একতাবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবকিছুর। ফলে মুক্তিযুদ্ধকে দলমত নির্বিশেষে দেখার পথ পাওয়া যায় বইটিতে।
বইটিতে মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (Nap) ও তার ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথাও এসেছে। ভাসানী ন্যাপ ও কৃষক সমিতির প্রধান থাকাকালে সমাজতন্ত্রের কথাই বলেছেন কিন্তু বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের মুখে পড়ে তিনি তাতে ইসলাম যোগ করেন। বইয়ের এক জায়গায় উমর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এই বলে যে, সমাজতন্ত্রের আগে ইসলাম শব্দটি থাকলে তাতে অমুসলিম কতজন যোগ দিতে পারবে।
যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ ছিল উত্তাল এক সময়। বিভিন্ন শ্রেণী তাতে জড়িত ছিল, ফলে বহুস্তরীয় ও জটির দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল তাতে। কারণ সব শ্রেণীই নিজেদের স্বার্থ দেখবে, এটাই স্বাভাবিক। কার্ল মার্ক্সের ডাস ক্যাপিটাল আমাদের সেই কথাই বলে। এদের কেউ কেউ যুদ্ধের সময় স্বজাতি নিধনযজ্ঞে মেতেছে, আর মালিকপক্ষ যুদ্ধের পর সাধারণ জনগণের ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। বিভিন্ন দল মুক্তিযুদ্ধের মালিকানা নিজেদের দাবী করেছে। যুদ্ধের পূর্বেই বদরুদ্দীন উমরের যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ-এ তাদের অবস্থান দেখা গেছে, তাই এরকমই যে হবে বা হওয়ার কথা এতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু এই বইয়ে আমরা নিরপেক্ষভাবে দেখতে পাই যদি আত্মত্যাগ ও সেই মোতাবেক পরিকল্পনা ও যুদ্ধ জয়ের প্রকৃত হকদার যদি কোনো পক্ষ থাকে তাহলে সেই শ্রেণী বাংলার সাধারণ কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা-শিক্ষক। ইতিহাসকে এভাবেই পাঠ করেন বদরুদ্দীন উমর। তিনি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে পাঠ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের আগে তেমনি ২০২৪ সালে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকেও পাঠ করেছিলেন সবার আগে, তিনিই প্রথম বলেছিলেন জুলাই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়। তার বিশ্লেষণ শতভাগ সত্য হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। প্রকৃত চিন্তক ও বুদ্ধিজীবীরা এরকমই হন।
লেখক: বদরুদ্দীন উমর
প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬,
আফসার ব্রাদার্স সংস্করণ ২০১৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)
প্রকাশক: আফসার ব্রাদার্স
মূল্য: ২১৩ টাকা।