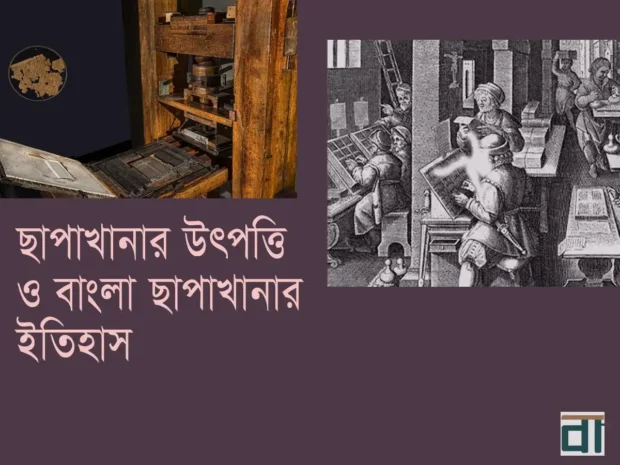মুদ্রণযন্ত্র বা বৃহৎ অর্থে ছাপাখানা ছাড়া আধুনিক সভ্যতার কল্পনা অসম্ভব ছিল। জ্ঞানের বিস্তার সম্ভব হয়েছিল ছাপাখানার মাধ্যমে। তাই জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে ছাপাখানার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা এর আগে হাতে লেখা বইয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তবে, সেই বইগুলো রাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে থাকত। বাকিসব বর্তমানের মতোই ছিল, বইগুলো রাখা হতো তাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় এবং লাইব্রেরিতে। আলেক্সান্দ্রিয়ার সেই বিখ্যাত লাইব্রেরি যেটি আগুনে পুড়ে যাওয়ায় এমন অনেক জ্ঞানই হারিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয় যা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেখানে প্রায় সব বই এবং দুর্মূল্য নথিপত্রই ছিল এক কপি করে এবং ছিল অসংখ্য ব্যাকরণের বই। তাই আলেক্সান্দ্রিয়ার ধ্বংস মানে তার ভেতরে থাকা অমূল্য সম্পদেরও চিরতরে বিনাশ হওয়া। যদি তখন মুদ্রণযন্ত্র সহজলভ্য হতো তাহলে পরিস্থিতি কিন্তু ভিন্নতর হতো। ছাপাখানার প্রকৃত ইতিহাস নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি, অনেকেরই ধারণা গুটেনবার্গের মাধ্যমেই ছাপাখানা এসেছিল। কিন্তু কথাটি সত্যি নয় মুদ্রণযন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল চীনে। এবং প্রথম কোন বইটি ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছিল? সেসব তথ্য খুবই চমকপ্রদ। আর বাংলায় ছাপাখানা কীভাবে এসেছিল? তারও ইতিহাস বিষয়ে ধোয়াশা কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন। ছাপাখানার উৎপত্তি ও বাংলা ছাপাখানার ইতিহাস নিয়ে লেখায় ছাপাখানা ও এর বাংলায় আগমন নিয়ে একটি তথ্যপূর্ণ রূপরেখা দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখায়।
ছাপাখানার আবিষ্কার ও বৈশ্বিক ইতিহাস
উৎপত্তি:
ছাপাখানার উৎপত্তি হয়েছিল পূর্ব এশিয়ায় অষ্টম শতাব্দীতে চিন দেশে। এই উৎপত্তির পেছনে ভূমিকা রেখেছে সম্ভ্রান্ত চাইনিজ, কুরিয়ার বুদ্ধ অনুসারী এবং চেঙ্গিস খানের বংশধরেরা।
প্রথম মুদ্রিত বই ও ত্রিপিটক:
চিনের টাং রাজবংশের সময়ে ৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বুদ্ধবই “হিরক সূত্র” প্রথম মুদ্রিত বই। তবে, ৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে উডব্লক পদ্ধতিতে চিনের জেইজিয়াংয়ের কারিগরদের দ্বারা মুদ্রিত বুদ্ধগ্রন্থ “ত্রিপিটক” ছাপাখানার ইতিহাসে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। এতে ১৩০,০০০ টি কাঠের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছিল।
আক্রমণ ও সংরক্ষণ:
এরপর চিন থেকে মুদ্রণযন্ত্রের জ্ঞান স্থানান্তরিত হয় কুরিয়ায় গরইয় রাজাদের হাতে। ১০৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আক্রমণকারীদের হাত থেকে বুদ্ধ ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তারা নিজেদের জন্য আবার উডব্লক পদ্ধতিতে “ত্রিপিটক” ছাপে। তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতিটি পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত হয়েছিল।
মোঙ্গল সেনাদের আক্রমণ ও বুদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা ত্রিপিটকের তৃতীয় মুদ্রণ:
১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র ওগেদাই খান সিংহাসনে বসেন। এর অব্যবহিত পরই ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কুরিয়ায় আক্রমণের নির্দেশ দেন। ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোল সেনাদের দ্বারা আবার ত্রিপিটক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু গরইয় রাজবংশ পুনরায় এটি ছাপার কার্যক্রম শুরু করে। বুদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা যে মুদ্রণের কাজ শেষ হয় ১২৫১ খ্রিষ্টাব্দে।
গুটেনবার্গের পূর্বে দ্রুতগতির ছাপাখানার আবির্ভাব:
এই সময়পর্বের মাঝেই গরইয় রাজবংশ ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে অন্য বই ছাপার দিকেও নিজেদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে। তারা বেসামরিক মন্ত্রী চুয়ে ইয়ুন-উই-এর কাছে একটি দীর্ঘ আয়তনের বই ছাপার প্রস্তাব নিয়ে যায়। কিন্তু এটি ছাপার জন্য অসম্ভব রকম বেশি কাঠের টুকরো আর সময়ের প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধানকল্পেই তার হাত ধরে চিনের ছাপাখানার একটি প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থানান্তরযোগ্য হরফের (মুভেবল টাইপ) দ্রুতগতির ছাপাখানার আবির্ভাব ঘটে। যে পদ্ধতি দুইশ বছর পর গুটেনবার্গ ব্যবহার করেন। গুটেনবার্গের জন্মের ১৫০ বছর আগে চুয়ে ইয়ুন-উই “স্থানান্তরযোগ্য হরফ”-এর আবিষ্কার করেন।
কোরিয়ায় স্থানান্তরযোগ্য হরফে প্রথম বই মুদ্রণ:
স্থানান্তরযোগ্য হরফে ছাপা প্রথম বই গুটেনবার্গের ছাপাখানার নয় বইটি কুরিয়ার, “দ্য এন্থলজি অব গ্রেট বুদ্ধিস্ট প্রিস্টস’ জেন টিচিংস”। ১৩৭৭ সালে ছাপা হয় এটি।
মোঙ্গলদের হাত ধরে ছাপাখানার জ্ঞান প্রথমে ইউরোপে প্রবেশ:
ধারণা করা হয় ওগেদাই খানের পুত্র কুবলাই খান চিন ও কুরিয়া থেকে ছাপাখানার জ্ঞান পেয়েছিলেন। পরে তার কাছ থেকে চেঙ্গিস খানের আরেক নাতি হুলেগু খান এই বিশেষ জ্ঞান পান। তিনি তখন মঙ্গোল সাম্রাজ্যের পারশিয়ার (ইরান) অংশে রাজত্ব করতেন। তার রাজত্বের সময়েই ছাপাখানার ধারণা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।
ইউরোপে মুদ্রণযন্ত্রের জ্ঞান পৌঁছাতে ইউঘুরের তুর্কিদের অবদান:
সিয়েন-সুয়েন-সিয়েন তার বই “সাইন্স এন্ড সিভিলাইজেশন ইন চায়না” (১৯৮৫)-তে বলেছেন, মঙ্গোলরা সিল্ক রোড হয়ে পারশিয়া গিয়েছিলেন, এই রাস্তার মধ্যবর্তী অংশে উইঘুররা বাস করতো, তারা তুর্কী আদিবাসী গোষ্ঠী। যারা মঙ্গোল সেনাবাহিনীতে যুক্ত হয়েছিল, আর কালক্রমে ছাপাখানার জ্ঞান সংগ্রহ করেছিল তারা। ছাপাখানায় ব্যবহৃত “উডব্লক” এবং “স্থানান্তরযোগ্য হরফ” দুই পদ্ধতিতেই তারা সিদ্ধহস্ত ছিল। তাদের মাধ্যমেই পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপে এই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে।
গুটেনবার্গের হাত ধরে ইউরোপে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন ও প্রথম বাইবেল:
জার্মানিতে জোহানেস গুটেনবার্গ ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে চুয়ে ইয়ন-উই-এর স্থানান্তরযোগ্য হরফের ছাপাখানা নতুন সময়ের প্রয়োজনে প্রবর্তন করেন। তাকে ইউরোপের ছাপাখানার জনক বলা হয়। এই ছাপাখানা থেকেই ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে গুটেনবার্গ বাইবেল ছাপা হয়, যেটি ছাপা বইয়ের যুগ শুরু করে ইউরোপে। বর্তমানে জার্মানিতে এর ৪৯টি কপি সংরক্ষিত আছে। গুটেনবার্গের ছাপাখানায় প্রতিদিন ৩৬০০ পাতা ছাপা যেত।
পশ্চিম ইউরোপে ছাপাখানার জনপ্রিয়তা:
পশ্চিম ইউরোপজুড়ে তার এই মুদ্রণশিল্প এতই জনপ্রিয় হয়েছিল, শুধুমাত্র ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দেই এগুলোর মাধ্যমে বই ছাপা হয়েছিল ২০ মিলিয়ন ভলিউম।
ভারত উপমহাদেশে ছাপাখানার প্রবেশ
ভারতে ছাপাখানা:
পর্তুগিজদের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা আসে। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে গোয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি।
অবিভক্ত বাংলায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্র ও প্রথম বই:
হুগলিতে মি. এন্ড্রুস প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্টিত করেন ১৭৭৮ সালে। একই সালে এখান থেকেই বাংলায় প্রথম মুদ্রিত বই প্রকাশিত হয় নাথানিয়াল ব্রাসে হ্যালহেড-এর “আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ”। বইটিতে বাংলা এবং ইংরেজি দুই ধরণের অক্ষরই ছিল।
কলকাতায় প্রথম মুদ্রিত পত্রিকা:
১৭৮০ সালে “বেঙ্গল গেজেট প্রেস” জেমস অগাস্টাস হিকি’র দ্বারা প্রতিষ্টিত হয়। এখান থেকেই তার সম্পাদনায় ভারত উপমহাদেশের প্রথম মুদ্রিত পত্রিকা “বেঙ্গল গেজেট” প্রকাশিত হয়।
পূর্ববাংলায় ও পরবর্তী বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা
পূর্ববাংলায় ছাপাখানা: পূর্ববঙ্গে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৪৭ সালে রংপুরে। প্রেসটির নাম “বার্ত্তাবহ যন্ত্র”। এরপর পর ঢাকায় ১৮৫৯ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, “বাঙ্গালা যন্ত্র” নামে প্রেস। এভাবে বহু বাক পেরিয়ে যশোরে ১৮৬৮ সালে “শিশির কুমার ঘোষের অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্র”। ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কাঙাল হরিনাথের “এমএন প্রেস”। এসব ছাপাখানার ধারাবাহিকতাতেই বাংলাদেশের বর্তমানের মুদ্রণযন্ত্রগুলো। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে এগুলো অবয়ব ও কাজের গতিতে পার্থক্য রয়ে বিস্তর, কিন্তু কাজ একই সে হচ্ছে ছাপা ও জ্ঞানের বিস্তার।
মুদ্রণযন্ত্রের ইতিহাস একটি বৈশ্বিক অগ্রগতি সূচনার কথা বলে আমাদের। নানাজাতি নানা বর্ণের মানুষ মিলে সেই ইতিহাস তৈরি করেছিল, তাই সেখানে যেমন চৈনিক, কোরিয়ার মানুষ ও মোঙ্গলদের অবদান যেমন আছে তেমনি তাকে দ্রুতগতিতে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে ইউরোপীয়দের অবদান রয়েছে। তাই সেই ইতিহাসে বাংলাদেশেরও ইতিহাসও জড়িত, আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার যে পথপ্রস্তুত করছি বহুকাল যাবত, আমাদের অসংখ্য সংগ্রাম, অসংখ্য আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ—সবখানেই মুদ্রণযন্ত্র জড়িত। দৈনিক পত্রিকা ও বই তো তার প্রাথমিক উপাদান, কিন্তু অজস্র লিফলেট যা বাংলাদেশের জনগণের মর্মের ক্ষোভকে ভাষা দিয়েছিল তার ইতিহাস অস্বীকার করতে পারব না আমরা, আর সেসব্ মুদ্রণযন্ত্রের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। আজকে ছাপা বই ও পত্রিকার দুরবস্থা চলছে বলে অনেকের ধারণা কিন্তু সেসব সাময়িক, মানুষ ছাপা লেখা পড়ারা বাসনা কখনও ছাড়তে পারবে না। মুদ্রণযন্ত্র থাকবে জ্ঞানের সহযোগী হয়ে, এ আশাবাদ নয় বাস্তবতা, ইতিহাস তাই বলে আমাদের।