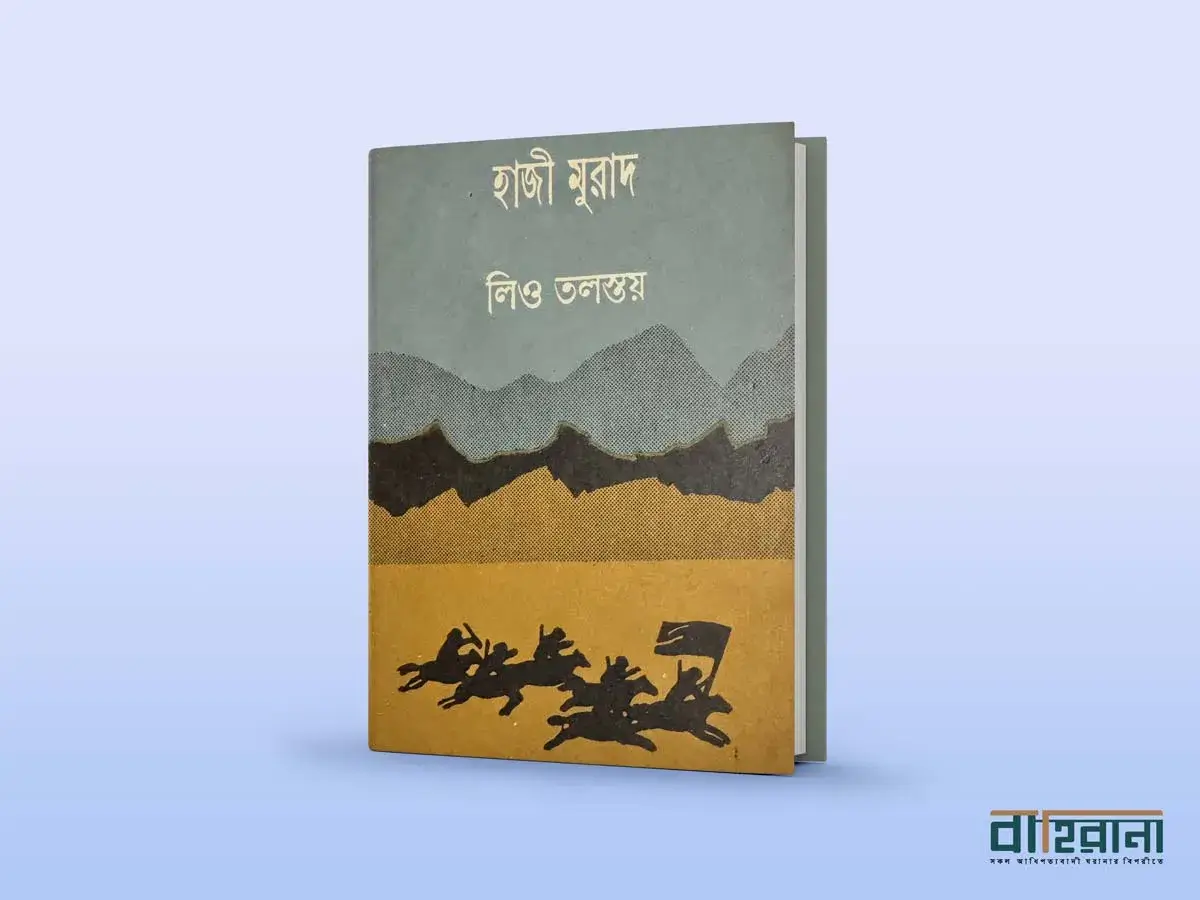লেভ লতস্তয়ের জীবনের বিচিত্র অধ্যায়গুলো তাকে দিয়ে বিচিত্র সব লেখা লিখিয়ে নিয়েছে। একদিকে তার হাত থেকে যেমন আমরা পেয়েছি ওয়ার এন্ড পিস, আনা কারেনিনা, অন্যদিকে ইভান ইলিচের মৃত্যু, কসাক-এর মতো উপন্যাসিকাও লিখেছেন তিনি। নৈতিক গল্প তো লিখেছেনই সেইসঙ্গে শিশু-কিশোরদের জন্যও দুহাত ভরে লিখেছেন। তবে কসাক-এর মতোই তলস্তয়ের হাজি মুরাদ নামে আরেকটি উপন্যাসিকা আছে। আকবর উদ্দিনের লিও তলস্তয়ের হাজী মুরাদ উপন্যাসিকাটির বাংলা অনুবাদ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। আমরা রাশিয়ার সাহিত্য প্রগতির অনুবাদে পড়েই অভ্যস্ত। কিন্তু আকবর উদ্দিনের অনুবাদ মানের দিক দিয়ে প্রগতির চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। বইটিতেও রুশ ও কসাকদের (তাতার, চেচেন, আভার) বৈরীতা উঠে এসেছে। তবে ভিন্নভাবে। কসাক ও হাজী মুরাদ দুইটি উপন্যাসিকাই তলস্তয়ের সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার উপর লেখা। তলতস্তয়ের মৃত্যুর (১৯১০ সাল) পর ১৯১২ সালে খণ্ডভাবে প্রকাশিত হয়েছিল নভেলাটি, সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। হাজী মুরাদ তলস্তয়ের শেষ বড় আকারের সমাপ্ত কাজ।
এই আখ্যানে একজন নির্মোহ সাধকের মতো তলস্তয় সত্যকথনে পিছপা হননি। প্রতিটি চরিত্রকেই অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন তিনি, তাদের গুণ ও দোষ—সবই বিচক্ষণতার সাথে বিচার করেছেন, ফলে সেই সময়টির সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পাঠকদের দেখা হয়ে যায়। উপনিবেশ স্থাপনের কর্মপ্রক্রিয়াকে এত অনুপমভাবে তিনি তুলে এনেছেন যে, যা ঔপনিবেশিক ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে গেছে।
তাতার, চেচেন ও পাহাড়ীরা যাদের অঞ্চল হলো ককেশাস, এই ককেশীয়দের সাথে রুশীয়দের বৈরিতা শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে। আধুনিক সময়ের অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা তারকোভস্কির আন্দ্রেই রুবলেভ (১৯৬৬) চলচ্চিত্রেও তাতারদের আক্রমণের বিষয়টি এসেছে। চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্র চিত্রশিল্পী রুবলেভ এক তাতার বর্বরতার সাক্ষী হয়ে ছবি আঁকাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আন্দ্রেই রুবলেভ ১৫শ শতাব্দীর রাশিয়ার একজন গুরুত্বপূ্র্ণ চিত্রশিল্পী। কিন্তু তলস্তয়ের সঙ্গে তারভোস্কিসহ অন্যদের তফাত আছে, তফাতটা এই যে, প্রথমত, তলস্তয়ের উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দাগেস্তানের বা ককেশাসের একজন মুসলিম ককেশীয়, যে আভার গোত্রের পাহাড়ী। হাজী মুরাদ দাগেস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় একজন। ককেশাসের বেশিরভাগ মানুষ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধর্ম পরিচয়সহ গুরুত্বসহকারে সাহিত্যে উল্লেখ করা হয় না, তলস্তয় তা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাতার ও চেচেনদের বাস্তব জীবন ও সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে তো যানইনি বরং ককেশাস বা বিশেষ করে এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে দাগেস্তানের অধিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম, নৈতিকতা, পারিবারিক জীবন—সবকিছুই নির্মোহভাবে বর্ণনা করেছেন। সেইসঙ্গে, তখনকার রুশ অভিজাত সমাজের দুর্নীতি, জার আমলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সম্রাটের মুখাপেক্ষিতা এবং অভিজাতদের মিথ্যাচার ও লাম্পট্যের বিবরণ দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি। যে লাম্পট্যে অগ্রগণ্য স্বয়ং সম্রাট জার নিকোলাস। মাথা পঁচে গেলে শরীরও একই পথে চলে। সম্রাট যে মাথা আর অভিজাতরা হলো শরীর তা দেখাতে কার্পণ্য করেননি। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের পার্থক্য (সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক) এবং দ্বন্দ্ব হাজী মুরাদ উপন্যাসিকায় সফলভাবে উঠে এসেছে।
আবার, রাশিয়া তার সীমান্তের দাগেস্তানসহ পুরো ককেশাস অঞ্চল দখলে নিয়ে তার বিভিন্ন গোত্রের অধিবাসীদের—যেমন তাতার ও আভার—বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য আদতে এই অঞ্চলের অনন্যতাকেও যে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল তা ককেশাসের দুর্ধর্ষ পাহাড়ী আভার গোত্রের বীর হাজী মুরাদকে অবলম্বন করে উপন্যাসিকাটিতে তুলে ধরেছেন তলস্তয়। তাও তিনি তা করেছেন চেচেন ও দাগেস্থানের ভূমি যে প্রাচ্য এবং তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির পাশ্চাত্যের সঙ্গে যে ভিন্নতা রয়েছে—সম্মান ও সততার সঙ্গে তা স্বীকার করেই। মহৎ সাহিত্য এরকমই পক্ষপাতহীন হয়। শুধু রাশিয়ার কথাসাহিত্যে কেন পৃথিবীজুড়েই হাজী মুরাদের মতো প্রাচ্যদেশীয় মুসলিম চরিত্র এভাবে তলস্তয়ের মতো সফলভাবে চিত্রিতকরণ খুব কমই হয়েছে।
প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের সঙ্গে তলস্তয় আরেকটি বৈশ্বিক সত্যেরও মুখোমুখি করেছেন আমাদের। সে হলো ক্ষমতা কীভাবে বিরোধীদের ছেটে ফেলে, তা। বাস্তবতাকে আমরা যেভাবে দেখি, তা অত সরল নয়, কারণ হাজী মুরাদ-এ জার নিকোলাস পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি ও শামিল প্রাচ্যের প্রতিনিধি হয়ে আসায় তা মাঝখানের ভারসাম্য তৈরি করা মানুষদের সততাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে। হাজী মুরাদ এই দ্বন্দ্বেরই বিয়োগান্তক নায়ক। কেননা, ক্ষমতা ক্ষমাহীন এক ঘূর্ণন তৈরি করে এরমধ্যে থাকা মানুষদের ঘিরে, তখন নীতি-নৈতিকতার বালাই থাকে না। তবে যারাই, যেমন হাজী মুরাদ এই নীতি, সততা ও পারিবারিক বন্ধনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে তাদেরকে ক্ষমতা কখনও ক্ষমা করে না। যেমন প্রাচ্যের দাগেস্তানে তেমনি পাশ্চাত্যের রাশিয়ান পক্ষের ক্ষমতাবলয়ে হাজী মুরাদের মতো একটিও শক্তিশালী চরিত্র ছিল না, ফলে তিনি দুই পক্ষেই অনুপযুক্ত। ঠিক এই কারণেই হাজী মুরাদের মতো এক নায়ককে তুলে ধরতে লেভ তলস্তয় তার শেষ জীবনে এত ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন, বইটি লেখার আগে তিনি প্রচুর গবেষণা করেছেন। হাজী মুরাদসহ বইয়ে থাকা প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডিটেইলস সংগ্রহ করেছেন। তলস্তয়ের সেনা জীবনের অভিজ্ঞতাও উঠে এসেছে। যেমন বাটলার চরিত্রে তা আমরা খানিকটা দেখতে পাই, তার জুয়া খেলা নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিবাহিত মারিয়া ডাইম্স্ট্রিয়েভ্নার প্রতি প্রেমের দুটানায়। অন্যদিকে শুধু তলস্তয়ের শেষ মাস্টারপিস বলেই নয়, হাজী মুরাদ-এর চিরকালীন প্রাসঙ্গিকতার আরেকটি কারণ হলো, ভিন্নজাতি, ভিন্নধর্মের দমনের বিষয়টি এতই বৈশ্বিক যে, তুলনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশেও পাহাড়ি আদিবাসীদের সঙ্গেও তাতার, আভার ও চেচেনদের মতোই আচরণ করা হয়।
আকবর উদ্দিন তার শেষ বয়সে লিও তলস্তয়ের হাজী মুরাদ উপন্যাসিকাটি অনুবাদ করেছিলেন। নভেলার আখ্যানভাগ খুবই সরল, হাজী মুরাদের জীবনের মাত্র শেষ কয়েকদিনের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন তলস্তয়। তার মধ্যেই রুশ ও কসাকদের যাবতীয় বিষয়-আশয় উঠে এসেছে। হাজী মুরাদ রুশদের প্রধানতম শত্রু ধূর্ত শামিলের নায়েব মানে সবচেয়ে বড় সহযোগী। ফলে, তিনিও একইরকম বিপদজনক রাশিয়ার জন্য। শামিল ও হাজী মুরাদ দুজনই দাগেস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্মুখসারির যোদ্ধা, যদিও হাজী মুরাদের কাছ থেকে শামিলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার পর তার সততা নিয়ে সন্দেহ জাগে। হাজী মুরাদের হাতে অনেক রুশ সৈনিক ও সেনা কর্মকর্তা মৃত্যু বরণ করেছে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই হাজী মুরাদ চেচেন নামে এক গ্রামে তার এক মুরিদ (কসাকদের মধ্যে সুফীদের মতো মুরিদ প্রথার চল ছিল তখন, এই প্রথা বহু বছরের বঞ্চনার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নিয়েছিল) সাদোর বাড়িতে রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন।
এরপর জানতে পারি শামিল গ্রামবাসীকে বলে রেখেছে হাজী মুরাদ এখানে আশ্রয় নিতে এলে তাকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। আশ্রয় দিলে আশ্রয়দাতার মৃত্যু অনিবার্য। এই নিষেধ সত্ত্বেও সাদো হাজীকে আশ্রয় দেয়। তো, এক পর্যায়ে গ্রামবাসী আশ্রয়ের খবরটি জেনে যায়। হাজী বাধার মুখে পড়ে, গ্রামে থেকে রাতেই বেরিয়ে যান। যাওয়ার আগে রুশ সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তার কাছে দূত পাঠান। এরপর তিনি কুরিন রেজিমেন্টের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রিন্স সাইমন মিখাইলভিচ ভরন্স্টভের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, মুরাদ তাকে বলেন শামিলকে পরাজিত করতে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে থাকবেন কিন্তু তার মা, স্ত্রী ও সন্তান শামীলের কাছে বন্দী। ভরন্স্টভ যেন বন্দি বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। তাহলেই তিনি শামিলের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়তে পারবেন, এর আগে তার হাত পা বাঁধা। হাজী মুরাদের আত্মসমর্পণ কসাক ও রুশ দুইপক্ষেই চাঞ্চল্য তৈরি করে, কারণ তিনি যে দলে থাকবেন সেই দলেরই বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর ভরন্স্টভেরর বাবা তখন রাশিয়ার সেনা প্রধান। ছেলের কাছে আত্মসমর্পণ করা মানে বাবা ও ছেলে দুজনেরই গৌরবে বৃদ্ধি হওয়া। ফলে কৌশলী এই আত্মসমপর্ণে মুরাদের একটি গোপন প্রত্যাশাও ছিল, তিনি ককেশাসের শাসনভার নিজের হাতে পাবেন এবং পরিবারকেও মুক্ত করবেন।
অন্যদিকে শামিল বিষয়টির বিপদ আঁচ করতে পারে, সে হাজী মুরাদের ছেলের চোখ তুলে নেওয়াসহ তার মা ও দুই স্ত্রীকে দাসী করে বিভিন্ন গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। তো যা ঘটে, পরিস্থিতি ক্রমেই হাজীর বিপক্ষে যেতে শুরু করে, কারণ রুশপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত স্থির করতে দেরি করতে থাকে। হাজী মুরাদের জন্য এটা জীবন-মরণ সমস্যা কারণ তার মা ও পরিবার শামিলের কাছে বন্দী। একপর্যায়ে তিনি নিজেই তাদের উদ্ধারের অভিযানে যাবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন বন্দী, তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য কসাক সৈন্যদের রাখা হযেছিল।
এক রাতে তিনি পালানোর জন্য স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন তার শিষ্যদেরসহ। পরদিন ভোরে যখন তারা পালাতে যান তখন রুশদলের কয়েকজন সৈন্য মারা যায় তাদের হাতে। কিন্ত তা সত্ত্বের ভাগ্য তার অনুকূলে নয়, তারা যখন রুশসীমানা পেরুনোর একদম দ্বারপ্রান্তে তখন বিপত্তি ঘটায় রাশিয়ার বিখ্যাত কাদা মাটি। সম্প্রতি ওই অঞ্চলে বন্যা হওয়ায় তাদের ঘোড়া দ্রুত গতিতে জমি পেরুতে পারছিল না। কাদায় ঘোড়ার পা দেবে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে তারা জমির পাশেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ভোরের কিছু আগে রুশ সেনারা হাজী মুরাদ ও তার দলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সেই দলে তার একসময়ের ধর্মবন্ধু হাজী আগা ও পুরনো শত্রুর ছেলে আহমদ খাঁসহ ২০০ জন তাতার মুসলিমও রয়েছে। সৈন্যাধ্যক্ষ কাগানফ ও হাজী আগা তাকে আত্মসমপর্ণের আহ্ববান জানায়, কিন্তু হাজী মুরাদ মুখোমুখি লড়াইয়ে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আত্মসমর্পণ করেন না। তিনি বীরের মতো লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। অনেক সৈন্য মারা যায় ও সেইসঙ্গে তার শিষ্যরাও মারা যেতে থাকে। একপর্যায়ে হাজী মুরাদও মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়েন। মারা যাওয়ার সময় তার তখনও চেতনা ছিল এইসময় হাজী আগা হাজী মুরাদের পিঠে চড়ে তার শিরচ্ছেদ করে।
এভাবেই রাশিয়ার সবচেয়ে বড় শত্রুদের একজন মারা যান যিনি কীনা তাদের বন্ধু হয়েছিলেন, সর্বস্ব বাজি রেখে তাদের হয়ে লড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিনিময়ে চাওয়া ছিল একটাই, তার পরিবারকে যেন শামিলের কাছ থেকে মুক্ত করা হয়। রুশ পক্ষের দোষ এখানে, যে, তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। কারণ যারা সিদ্ধান্ত দেবে ও যারা তা বাস্তবায়ন করবে তাদের দূরত্ব এবং কসাকদের সঙ্গে তাদের দুশমনি ও ঘৃণার সম্পর্ক থাকায় হাজী মুরাদের ব্যক্তিগত সমস্যা সে যত বড়ই হোক তাদের কাছে তার মূল্য খুবই অল্প ছিল। তবে এই নভেলাটির মাধ্যমে তৎকালীন রাশিয়ার প্রশাসনিক কাজকর্মের একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তখন জারের খেয়াল ও মর্জিমতো সব সিদ্ধান্তই সবার শিরোধার্য ছিল—যা সমগ্র রাশিয়াকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। আর অভিজাতরা ছিল জারেরই লোক, এমনকি তাদের চুলও সম্রাটের মতো করে আচড়ায় তারা, কারণ তাদের বর্তমান অবস্থান সবই জারের সুনজরের উপর নির্ভর করছে। হাজী মুরাদ উপন্যাসিকায় জার নিকোলাসের যে প্রতিকৃতি আমরা তলস্তয়ের কাছ থেকে পাই তাতে এটাই প্রতীয়মান হয়, এই অবস্থার অবসান আবশ্যক। কেন রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লব হয়েছিল বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। কারণ সাধারণ জনগণের জীবনের কোনো মূল্যই তখন রাশিয়ায় ছিল না। এরমধ্যে আবার বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তিতে যেতে হতো যুবকদের। নিকোলাস এতই খেয়ালখুশি মতো চলা সম্রাট ছিলেন যে আমরা বইটিতে দেখতে পাই তিনি এক বৈঠকেই তখনকার একমাত্র স্বাধীন কৃষকশ্রেণীকে নিজের সম্পতির অংশ করে দাস বানিয়ে দিয়েছিলেন। জার আমলে রাশিয়ায় দুইধরণের কৃষক ছিল একদল বেশি অংশ তারা পরাধীন ও আরেকদল খুবই ক্ষুদ্র অংশ তারা স্বাধীন।
এই আখ্যানে একজন নির্মোহ সাধকের মতো তলস্তয় সত্যকথনে পিছপা হননি। প্রতিটি চরিত্রকেই অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন তিনি, তাদের গুণ ও দোষ—সবই বিচক্ষণতার সাথে বিচার করেছেন, ফলে সেই সময়টির সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পাঠকদের দেখা হয়ে যায়। উপনিবেশ স্থাপনের কর্মপ্রক্রিয়াকে এত অনুপমভাবে তিনি তুলে এনেছেন যে, যা ঔপনিবেশিক ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সময় কী এই সময়ও নয়? জাতিগত বৈরিতা, আধিপত্য, দখলদারিত্ব, অবিশ্বাস কী পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গেছে? হয়নি। আর এই মানুষে মানুষে বৈরিতা, অবিশ্বাস, আধিপত্য ও উপনিবেশ স্থাপনের এক ক্লাসিক উপদাহরণ লিও তলস্তয়ের হাজী মুরাদ নভেলাটি। হাজী মুরাদ শুধু ঐতিহাসিক চরিত্র তাই নয়, তাকে তলস্তয় নিজে দেখেছিলেনও ককেশাসে। ১৯৯৪ সালের তার রোজনামচায় লিখেছিলেন, “খোলা মাঠে বেড়াবার সময় লাঙল-পিস্ট কাঁটা গাছের একটি ভাঙা ডালে টক্টকে লাল ফুল দেখে ‘হাজী মুরাদের’ কথা আমার মনে হয়েছিল।” (হাজী মুরাদ, অনুবাদ আকবর উদ্দীন) কিন্তু ঠিক কী তার মনে মনে হয়েছিল, তার কথা আছে উপন্যাসিকার শেষ বাক্যে, “চষা মাঠে চূর্ণ কাঁটা গাছটা দেখে এই মৃত্যুর কথাই আমার মনে হয়েছিল।” (ঐ)
হাজী মুরাদ
লেখক: লিও তলস্তয়
অনুবাদ: আকবর উদ্দিন
প্রকাশক: বাংলা একাডেমি
প্রকাশকাল: ১৯৮৪ সাল।
বিশ্ব সাহিত্যের মহৎ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম লেভ তলস্তয়। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক হামীম কামরুল হক বাহিরানা Talk-এ নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ধ্রুপদি প্রেরণা প্রসঙ্গে লেভ তলস্তয়ের নাম উল্লেখ করেছেন।