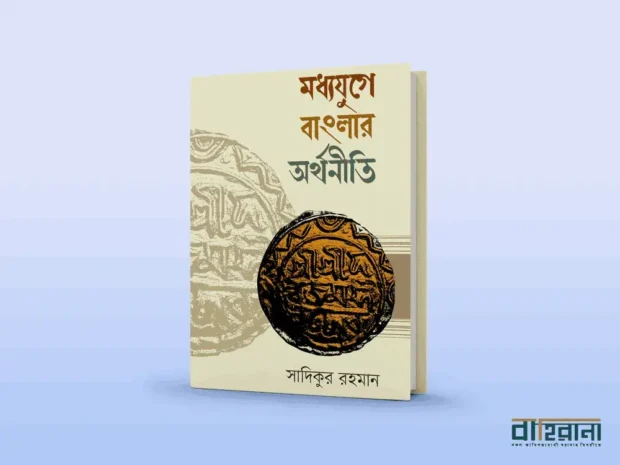মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য বিষয়ে আমরা যতদূর জানি বা গবেষণা রয়েছে তার খুবই অল্প পরিমাণই রয়েছে অর্থনীতি নিয়ে। এর কারণ তথ্য-উপাত্তের অভাব নাকি মনোযোগ—সেটা বের করা শক্ত। তবে এটা নিশ্চিত অর্থনীতি ও সাহিত্য ছাড়া মধ্যুযুগ কেন ইতিহাসের কোনো সময় পর্বের সমাজেরই প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে চর্যাগীতিকার কথা বলা যায়, গীতিকাগুলোতে সেইসময়ের সমাজের গঠন জানার পাশাপাশি তার অর্থনীতিও আমরা জানতে পারি। যেমন, তখন নীম্নজাতের মানুষদের সমাজের বাইরে বাস করতে হতো। তাদের জীবিকা ও জীবন কেমন ছিল তার একটা ধারণা পাই আমরা গীতিকাগুলোতে।
তবে খাঁটি অর্থনীতি নিয়ে স্বল্পসংখ্যক বইয়ের মধ্যে সাদিকুর রহমানের মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি (১২০৪-১৭৫৭) বইটি বাংলার মধ্যযুগের অর্থনীতি জানতে ও বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর সাথে অন্য গবেষকদেরও আকৃষ্ট করতে পারে।
লেখক বৃহৎ পরিসরে সময়টিকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, জীবন যাপনের মূল রসদ কোথা থেকে আসে, জীবিকা কীভাবে অর্জিত হয়, এগুলো তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আর বিষয়গুলোকে বাধা প্রদান করে বা সম্মৃদ্ধ করে যে রাজনীতি সেটিকে এড়িয়ে তো কোনো অর্থবহ আলোচনাই হতে পারে না, তাই তিনি একে বইয়ের একদম শুরুতেই রেখেছেন।
সাদিকুর রহমানের মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি (১২০৪-১৭৫৭) গবেষণা বইটিতে তিনি একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, সেটি হলো, মধ্যযুগে বৈশ্বিক পরিসরে বাংলা বিশেষ পরিচিত পেয়েছিল তার পণ্য ও ব্যবসায়ের কারণে, কিন্তু প্রচলিত ইতিহাস গবেষণায় সেটিকে অগ্রাহ্য করে সেইসময়ের রাজাদের নিয়েই আলোচনা হয় বেশি। লেখক বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে। ভিন্নসূত্রে উল্লেখ করা যায়, আধুনিক যুগে যেমন আকবর আলি খান তার আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি বইয়ে বলেছেন আমাদের এখানে মূলধারার অর্থনীতি নিয়ে প্রকাশিত বই অপ্রতুল, মানে হলো ইতিহাসজুড়েই বাঙালি সব সময় প্রয়োজনীয় বিষয়কে ফেলে অন্য জিনিসে মন দিয়েছে।
বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই মনোযোগ দাবী করে। তবে এও বলা যায় রাজাদের ইতিহাসও অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাদ দিয়ে নয়। আর ইতিহাস বলে, ভারতীয় গ্রাম ব্যবস্থা ও তার অর্থনীতির চেয়ে বাংলার গ্রাম ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ছিল ভিন্ন। সাদিকুর রহমানের অর্থনীতির আলোচনায় এটাও বিবেচনায় রাখা উচিত ছিল। কারণ এই ভিন্নতাই ভারতের চেয়ে বাংলার সমাজের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য অর্জনের কারণ। তবে পার্থক্যটি বইয়ে সম্যকভাবে না এলেও মধ্যযুগের বাঙালির জীবিকার সামগ্রিক আলোচনায় এটি এমনিতেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।
বইয়ে অধ্যায় আছে পাঁচটি, “মধ্যযুগে বাংলার রাজনীতি” “মধ্যযুগে বাংলার কৃষি” “মধ্যযুগে বাংলার শিল্প” “মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য” “মধ্যযুগে বাংলার জীবনযাত্রার মান”। শেষে পরিশিষ্ট অংশে রয়েছে সাহিত্য পর্যালোচনা।
দেখা যাচ্ছে লেখক বৃহৎ পরিসরে সময়টিকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, জীবন যাপনের মূল রসদ কোথা থেকে আসে, জীবিকা কীভাবে অর্জিত হয়, এগুলো তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। বইটি পড়তে পড়তে আরেকটি বিষয়ও মনের মধ্যে উঁকি দেয়, বাংলার বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থাকে কোন অর্থনীতির তত্ত্ব ধারণ করতে পারে? কিংবা কোন পরিস্থিতিতে অর্থনীতির তত্ত্ব জন্ম নেয়? এসব চিন্তাই আসে সনৎকুমার সাহার অর্থনীতির ন্যায়-অন্যায় বইটি পড়তে পড়তে। কারণ বইটির অর্থনীতির তত্ত্বতালাশ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন শুধু সমাজে মানুষের আদান-প্রদানেই অর্থনৈতিক তত্ত্ব দাঁড়ায় না, বরং কোনো একটি স্থানে স্থায়ী বসতি থাকলেই সেখান কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্ব দাঁড়াতে পারে। সাদিকুর রহমানের বইয়ে এই প্রতীতি জন্মায় বাংলায়ও কোনো অর্থনীতির তত্ত্ব জন্ম নিতে পারত, কারণ স্থায়ী বসতির পাশাপাশি এখানকার মানবসমাজের বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল। কিন্তু একই প্রবন্ধে সনৎকুমার সাহা ভাবনার শৃঙ্খলার বিষয়েও বলেছেন, যা তখনকার বাংলায় ছিল না। ফলস্বরূপ কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্ব তৈরি হয়নি।
মধ্যযুগে না হোক আধুনিক যুগে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দ্বারা সেই কাজ হয়েছে। তার দারিদ্র বিমোচনের তত্ত্ব যা তিনি তার তিন শূন্যের পৃথিবী বইয়ে বিস্তারিত বলেছেন, বিশ্ব অর্থনীতিকেই আশার আলো দেখাচ্ছে। অনেক দেশেই তা বাস্তবায়নের কার্যক্রমও চলছে।
সাদিকুর রহমানের মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি (১২০৪-১৭৫৭) বইয়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক আরেকটি বই সেলিম জাহানের বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বইয়ের তুলনা চলে আসে। তুলনাটি হলো মধ্যযুগের বাংলার অর্থনীতির সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতির, কেমন আছে বাংলাদেশের অর্থনীতি? অতীত কী আসলেই সম্মৃদ্ধির ছিল আর যদি তা হয় তাহলে এখন কেমন? আর অতীত সম্মৃদ্ধির না হলে বর্তমানে কতটা অগ্রগতি হয়েছে? একারণেই বোধহয় কোনো বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে জানতে, তার বিচিত্র উপাদানে চক্রাকারে ঘুরতে হয়, না হলে ফল মেলে না।
আরেকটি বিষয় হলো, অর্থনীতিসহ রাষ্ট্রের সব বিষয়কে বাধা প্রদান করে বা সম্মৃদ্ধ করে যে “রাজনীতি” সেটিকে এড়িয়ে তো কোনো অর্থবহ আলোচনাই হতে পারে না। রাজনীতির আওতা কত ব্যাপক তার প্রমাণ পাই আকবর আলি খানের পরার্থপরতার অর্থনীতি বইয়ে। বইটিতে একটি অধ্যায়ের নামই আছে “সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি” নামে, এমনকি সংস্কার নিয়েও রাজনীতি হয়। তাই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই রাজনীতিকে মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি বইটিতে সাদিকুর রহমান একদম শুরুতেই রেখেছেন। আর অগ্রসর পাঠকদেরকে বইয়ে থাকা গ্রন্থপঞ্জিও বিশেষ সহায়তা করতে পারে। সব ধরণের পাঠকদেরই বইটি পাঠের আনন্দ ও জ্ঞানের রসদ জোগাবে।
মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি (১২০৪-১৭৫৭)
লেখক : সাদিকুর রহমান
বিষয়: অর্থনীতি, গবেষণা
প্রকাশকাল : ২০২৫
প্রকাশক : কথাপ্রকাশ
মূল্য: ৮০০ টাকা।
মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি (১২০৪-১৭৫৭) বইটি কিনতে চাইলে